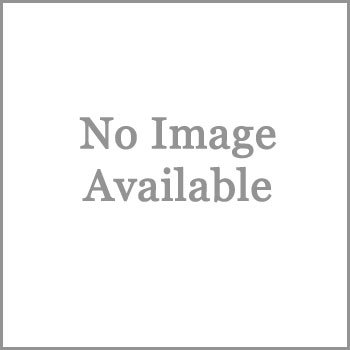একনায়কবাদী দলের বৈশিষ্ট্য ঃ দল গঠনের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম এ দ’টো উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের দলের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
(ক) ক্ষমতাসীন একনায়ক যাদেরকে নিয়ে দল গঠন করে, তারা কোন রাজনৈতিক দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বা দেশের সমস্যার সমাধানের তাকিদে ঐ দলে যোগ দয়ে না। বরং একনায়কের অনুগ্রহ নিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল করাই তাদের উদ্দেশ্য। এটাই তাদের আদর্শ।
(খ) রাজনৈতিক দল আগে গঠিত হয় এবং দলের মাধ্যমে ক্ষমতা হাসিল হয়। আর একনায়ক আগে ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে সুবিধাবাদীদের সমন্বয়ে দল গঠন করে।
(গ) একনায়কের তৈরী দল হল তার সেবক। একনায়ক দলের নির্বাচিত নেতা নয়, এ নেতাকে বদলাবার ক্ষমতাও দলের নেই। দলের আর সব ‘নেতা’ একনায়কের ব্যক্তিগত কর্মচারী। এ জাতীয় দলে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেতা হয় না। একনায়কই দলের স্বঘোষিত নেতা। তার ইচ্ছাই দলের ইচ্ছা। তার মর্জি পূরণ করাই দলের একমাত্র কর্মসূচী।
(ঘ) এ ধরনের দলের যেহেতু ক্ষমতা ভোগ করা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দর্শন থাকে না, সেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদীরা একনায়ককে ঘিরে সংঘবদ্ধ হয়। বিভিন্ন চিন্তাধারার লোক একনায়কের নেতৃত্বে মেনে এক সংগঠনভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে সত্যিকারের সাংগঠনিক ঐক্য সম্ভব হয় না। সুবিধাবাদ এবং ক্ষমতা ভোগই ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি।
গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতা দলের নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত। দলের রীতি ও আদর্শের বিপরীত চললে তার নেতৃত্ব বিপন্ন হয়। নেতারা দলের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য। দলের প্রাধান্য নেতাদেরকেও মানতে হয়। রাজনৈতিক দল দলীয় নেতৃত্ব একনায়কত্ব মানতে রাজী হয় না। একনায়কবাদী দলের নেতৃত্ব একনায়কেরই কুক্ষিগত, এমন কি দলের অস্তিত্বও তারই মরজীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
বর্তমান দলগুলোর অবস্থা ঃ বর্তমান দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নির্ণয় করা দস্তুরমত মুশকিলের ব্যাপার। এক নামেও একাধিক দল আছে। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান সরকারী দলকে কোন রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা তা অগণতান্ত্রিক একনায়কবাদী দল গঠনের যে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে সে আলোকে বিচার করার দায়িত্ব পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম।
অন্যান্য দলগুলোকে শ্রেণী বিন্যাস করলে নিুরূপ চিত্র ফুটে উঠেঃ
১। সমাজতন্ত্রী দল ঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ
(ক) রুশ পন্থী
(খ) চীনপন্থী
(গ) ভারতপন্থী (এরা অবশ্য রুশ পন্থীদের সহযোগী)
২। বাংলাদেশপন্থী দল ঃ যাদের রাজনীতি বাংলাদেশ ভিত্তিক, যারা অন্য কোন দেশপন্থী নয়, যারা বাঙালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয় বরং বাংলাদেশী জাতীয়তায় বিশ্বাসী। তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ
(ক) ইসলাম পন্থী ঃ যারা ইসলামকে দলের নামে এবং দলীয় আদর্শে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে।
(খ) দেশীয় সমাজতন্ত্রী ঃ এদের মধ্যে কোন কোন দল দেশীয় সমাজতান্ত্রিক বলেও দাবী করে এবং কোন দেশের লেজুড় বলে স্বীকার করে না।
(গ) ভারত রুশ বিরোধী ঃ যারা ভারতের আধিপত্য বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী হওয়ার কারণেই স্বাভাবিকভাবে মুসলিমপন্থী- তারা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হয়েও মুসলিম জনতার সমর্থনের প্রয়োজনে মুসলিমপন্থী হতে বাধ্য হয় এবং ইসলামের কথাও মাঝে মাঝে বলে।
৩। আমেরিকাপন্থী দল ঃ যারা সমাজতন্ত্রী নয় তাদেরকেই সমাজতন্ত্রীরা মার্কিনপন্থী বলে গালি দেয়। যেহেতু সমাজতন্ত্রীরা কোন না কোন বিদেশপন্থী তাই বাকী সবাইকে মার্কিনপন্থী মনে করে। আমেরিকার কোন আন্তর্জাতিক আদর্শ নেই। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধা দেয়াই তাদের নীতি। তাই যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হয়নি, সেখানে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বা দলকে ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় আসার জন্য আমেরিকা পৃষ্টপোষকতা করে থাকে। অবশ্য কোন নিষ্ঠাবান ইসলামী আদর্শবাদী দলকে কোন অবস্থায়ই আমেরিকা পছন্দ করতে পারে না। কারণ প্রকৃত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হলে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কবর রচিত হয় এবং বস্তুুবাদ খতম হয়ে যায়।
সমাজতান্ত্রিক হওয়ার দাবীদারদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান নয়, তাদেরকে যেমন আমেরিকা পৃষ্টপোষকতা করে থাকে তেমনি নামসর্বস্ব ইসলাম পন্থীদেরকেও আমেরিকা ব্যবহার করতে পারে।
উপরোক্ত কয়েক প্রকারের অগণিত দলের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক মজবুতি ও কর্মী বাহিনীর বিচারে মাত্র কয়েকটি দলকে জাতীয় মানের বলা চলে।
দেশে রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত বেশী হওয়াটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে অথবা নেতা হওয়ার খায়েশের কারণেই দলের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদের অনেকেই মনে করেন, যে সরকরী উদ্যোগেই সকল দলকে বিভক্ত করে প্রভাবহীন করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে দলের সংখ্যা ক্রমে সহজেই কমে যাবে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে তা কিভাবে কমে যাবে। তার উত্তরে বলা যায়- যারা পার্লামেন্টে সিট পাবে তারা ছাড়া বাকী দলগুলোর কোন প্রভাবই জনগণের
মধ্যে থাকবে না। ১৯৭৯ সালে প্রায় ৩০টি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি দু’টি সিট পেয়েছে এমন দলসহ মোট মাত্র দশটি দলই সংসদে আসন পেয়েছে। ১৯৮৬ সারের সংসদ নির্বাচনে অনেক দলই অংশগ্রহণ করেনি। সরকারী দল ও ৮ দলীয় জোট ছাড়া ছোট বড় ১৫টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ ১৫টি দলের মধ্যে মাত্র ২টি দল সংসদে আসনে পেয়েছে। নিয়মিত নির্বাচন চলতে থাকলে দলের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কমতে থাকবে।
কিন্তু দল কমানোর জন্য যদি কোন কৃত্রিম পদক্ষেপ নেয়া হয় তবে এর সংখ্যা না কমে বরং আরো বেড়ে যাওয়ারই ভয় আছে। দলের সংখ্যা কমাবার আরো একটা কারণ ঘটতে পারে। এদেশের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আদর্শ হিসেবে ইসলামী রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করলে ভিন্ন আদর্শের দলের সংখ্যা কমে যাবে। কোন আদর্শবাদী দল জনগণের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়ে গেলে নাম সর্বস্ব ইসলামী দলের সংখ্যাও আপনিই কমে আসবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবার প্রধান কারণই হলো গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। একনায়কের শাসনামলে সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিকদের চাহিদা বেড়ে যায়। এক নায়ক নিজের দল গঠনের জন্য চালু রাজনৈতিক দলগুলোতে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নেতৃত্বের কোন্দল বাঁধিয়ে এক একটি দলকে নেতৃত্বের ভিত্তিতে একাধিক দলে পরিণত করে। তাছাড়া একনায়কের নিকট ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির আশায় অনেক পাতি নেতাও ভিন্ন ভিন্ন নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহাল হলে এ জাতীয় দল আপনিই মরে যায়। (বাংলাদেশের রাজনীতি)
গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ্ও সরকার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে যত মতপার্থক্যই থাকুক গণতন্ত্রের দোহাই সবাই দিচ্ছে। জনগণকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস বলে স্বাকার করতে কেউ কার্পণ্য করে না। সামরিক অভ্যুত্থানের নায়করাও “গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য” নিয়েই সশস্ত্র বিপ্লব করে থাকেন। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গন্ধ না থাকলেও সমাজতন্ত্রী ভাইরা কি গণতন্ত্রের দোহাই কারো চেয়ে কম দেন ?
গণতন্ত্রের যত প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যাই দেয়া হোক এর একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা আছে। প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই গণতান্ত্রিক বলা চলে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঃ
১। জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারী ক্ষমতা হালিল করতে হয়।
২। প্রতিষ্ঠিত সরকারের দোষক্রটি প্রকাশ করার অবাধ সুযোগ জনগণের হাতে অবশ্যই থাকে।
৩। সরকার পরিবর্তনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে চেষ্টা করার সুযোগ ও অযাদী থাকে।
গণতন্ত্রের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার বহাল থাকতে পারে না। কিন্তু এ কাংখিত ব্যবস্থাটির প্রশংসা সবাই করলেও এর প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা সবচেয়ে কঠিন বলে দুনিয়ার প্রমাণিত হয়েছে। “সত্য কথা বলাই কর্তব্য” একথা কোন মিথ্যাবাদীও অস্বীকার করে না। কিন্তু সত্য বলা কি সবচেয়ে সুঃসাধ্য নয় ?
“বিপ্লব বনাম গণতন্ত্র” শিরোনাম থেকেই নিশ্চয়ই এটাই প্রতিপাদ্য বলে মনে হবে যে, বিপ্লব গণতন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতি। আসলে বিপ্লব শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যাপক পরিবর্তন বা মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) চরিত্রহীন সমাজে উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক তৈরি করে তাদের জীবনে সত্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। তিনি মদীনায় বিনা রক্তপাতে সরকারী ক্শতা গণ-সমর্থনের মাধ্যমে লাভ করে প্রচলিত গোটা সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায়। অবশ্য ‘দার্শনিক বিপ্লব’ই এ জাতীয় পরিবর্তনের সঠিক সংজ্ঞা।
বিপ্লব শব্দের ব্যবহার ঃ সাধারণভাবে “বিপ্লব” বললে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান, শক্তি বলে সরকারকে উৎখাত ইত্যাদি বুঝায়। এভাবে ক্শতা দখলকারী সরকারকে গৌরবের সাথে “বিপ্লবী সরকার” নামে পরিচয় দেয়। এই কারণেই যখন কেউ বিপ্লবের আওয়াজ তোলে তখনই মানুষ শক্তির ব্যবহার হবে বলে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করে।
অবশ্য আজকাল “বিপ্লব” শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকেই করছেন। আন্দোলন করার অর্থেই তারা বিপ্লব শব্দ ব্যবহার করছেন। নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে আন্দোলন বা অভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। এ কাজটি এত শ্রমসাধ্য ও সাধনা সাপেক্ষে যে, কয়েক বছরেও যদি কোন দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে সক্ষম হয় তাহলে জাতীয় জাতয়ি জীবনে এটা অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এ পরিবর্তন গায়ের জোরে হবে না। স্বাক্ষরতা আন্দোলন সফল হলেই তা সম্ভব। সেচ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে এবং বন্যার পানিকে ধারণ করার প্রয়োজনে খালখননের গণ আন্দোলনকে “বিপ্লব” নাম দেয়া হচ্ছে। এক একটি শব্দের বিশেষ একটা ওজন আছে। যেখানে সেখানে কোন শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যরস বা হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
“বিপ্লব” শব্দটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত বা অনুচিত এ বিষয়ে মতবেধ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আওয়াজ এমনকি কাবুল ষ্টাইলের বিপ্লবের শ্লোগান পর্যন্ত জনগণ শুনতে পাচ্ছে সেখানে বিপ্লবের সস্তা ব্যবহার চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিপ্লবের প্রতিরোধ স্পৃহা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতেও বিপ্লবের আওয়াজকে “খাল কাটা বিপ্লবের” মতই জনগণ নিরাপদ মনে করে অবহেলা করতে পারে। তাই “বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনেই হালকাভাবে এর ব্যবহার অনুচিত।
যা হোক বিপ্লব শব্দের ব্যবহার আলোচ্য বিষয় নয়। ভাববার বিষয় হলো যে আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, না গণতান্ত্রিক সরকার কামনা করি। দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন চাই, না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাই। জনগণকেও এ বিষয়ে সজাগ হতে হবে যে, কাদেরকে সমর্থন করা উচিত। যাঁরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর মনে করেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি এক ধরনের হবে। আর যারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী তাদের কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।
গণতান্ত্রিক মনোভাব ঃ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের আচরণ গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনকে অশালীন ভাষায় গালি দেয়া চলে না। গণতন্ত্রমনা লোকের ভাষাই জানিয়ে দেয় যে, তিনি অধৈর্য নন। সরকারী ক্ষমতা থেকে কোন বিরোধী দলকে অন্য দেশের দালাল বলে গালি দেয়া অর্থহীন। দালাল হয়ে থাকলে আইনের মাধ্যমে বিচার করুন। সরকারের হাতেই আইন রয়েছে। সে আইনের প্রয়োগ না করে অসহায়ের মত গালি দেয়া দুর্বলতারই পরিচায়ক। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এদেশে যে হারে একে অপরকে বিদেশী দালাল বলছে, তাতে দুনিয়ার মানুষ আমাদের সবাইকে শুধু দালালই মনে করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে রাজনীতিবিদদের পরম ধৈর্যশীল হতে হবে। দু॥খের বিষয়, এ ধৈর্যেরই অভাব সবচেয়ে বেশী। সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমালোচনার ভাষা যে নিুমানের লক্ষণ প্রকাশ করে তা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এ বিষয়ে সরকারী দলের দায়িত্বই বেশী। তাঁরা ক্ষমতায় থেকে যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা না করেন, তাহলে বিরোধীরা শিখবে কি করে ? যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের অধৈর্য হবার কোন প্রয়োজনই নেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় যাবার জন্য যদি অধৈর্য হয় তাহলে কিছুটা এলাউন্স তাদেরকে দিলে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন হতে পারে।
বিরোধী দলের অবশ্যই ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু কিভাবে তারা ক্ষমতায় যেতে চান ? একটা নির্বাচন হয়ে গেল। তাঁরা নির্বাচনে অংশও নিলেন। আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁদেরকে কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ক্রটিপূর্ণ। সরকার পরিচালকের হাতে এত ক্ষমতা থাকা অবস্থায় নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নীতি চালু থাকতে পারে না। এসব সথধা যেমন সত্য তেমনি অগণতান্ত্রিক পন্থায় যে গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না সে কথাও সত্য। তাই যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের নিজেদের কার্যাবলী প্রতমে গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে।
যারা বিরোধী দলে আছে তারাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পেতে চাইলে তাদের কার্যক্রম এক ধরনের হবে। কিন্তু যদি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কর্মধারাই তারা অনুসরণ করবে। তাদের কর্মনীতি ও কর্মপন্থা থেকে নিজেদের প্রকৃত চেহারা সবার সামনে স্পষ্ট হতে বাধ্য।
গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠ ও ধৈর্যের সাথে জনগণকে তাদের কার্যাবলী দ্বারা এতটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তথাকথিত বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সবার জন্যই নিরাপদ এ বিষয়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে সজাগ করে তুলতে হবে।
বিপ্লবের অনিশ্চিত পথ ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে যারা বিপ্লবের পথে গদিতে যেতে চান তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত ? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপ্লব যেখানেই এসেছে সেখানে গণতন্ত্র কোথাও দানা বাঁধতে পারেনি। বিপ্লবের পর বিপ্লব লাইন ধরে এসেছে। এটা কি নিরাপদ পথ ? শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় গেলে শক্তির উপর নির্ভর করেই শাসন চলে। এ ধরনের সরকার জনগণের সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না বলে যখন জনসমর্থন হারায় কথন সুযোগ বুঝে পাল্টা বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে তাই এ পথ একেবারেই অনিশ্চিত।
বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যারা বিপ্লব করে তাদের অবস্থা আরও করুণ। আফগানিস্তানে নূর মুহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন ও কারমাল এ বিপ্লব দ্বারা কি পেলেন ? যারা কাবুল স্টাইলে স্বপ্ন দেখেন তারা এটাকে নিরাপদ পথ মনে করেন কোন যুক্তিতে ? তথাকথিত বিপ্লবের পথে দেশকে একবার ঠেলে দিলে ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। এ বিপ্লব জনগণের পারস্পরিক আস্থা খতম করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে ছারখার হতে থাকে।
তাই বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরই সবার আস্থা স্থাপন করা উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করা প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীনদের। তারা যদি নিজেদের গদী ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে তাদের রেশন করা মাপে গণতন্ত্র দেন তাহলে ময়দান বিপ্লবীদেরই পক্ষে যাবে। যদি আন্তরিকতার সাথে গণতন্ত্রকে বিকাশ লাভের সুযোগ দেন তাহলে গণতান্ত্রিক শক্তিই ময়দানে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে বিপ্লবীদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। ক্ষমতাসীনরা ১৯৪৭ সাল থেকে একই ধারায় গণতন্ত্রকে কোন ঠাসা করে বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে সুযোগ করে দিয়েছে। এর কুফল ক্ষমতাসীনরাই বেশী ভোগ করেছে। কারণ ক্ষমতায় চিরদিন থাকা যায় না। গদী থেকে নামার পরও আবার উঠার সিঁড়িটা বহাল থাকে। একবার কোন প্রকারে কেউ ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ যাতে সেখানে যাবার পথ না পায় সে উদ্দেশ্যে সিঁড়িটাই নষ্ট করে দেয়। ফরে নিরাপদে তারা নামার পথও পায় না। গদীতে উঠা-নামার পথটা পরিস্কার রাখাই গণতন্ত্রের পরিচায়ক।
পাক-ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদেরকে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে কমই শিক্ষা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক পথে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা থেকে বেদায় হলেন। অনেকে মনে করেছিল যে, তিনি চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু ঐ গণতান্ত্রিক পথেই আবার ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারানো বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শেখ মুজিব ও ভুট্টো জনমসর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেও গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারালেন। ফলে এমন পথে তাদেরকে যেতে হলো, যে পথে গিয়ে আর ফিরে আসবার উপায় থাকল না। ক্ষমতাসীনরা যদি এটা বুঝতে পারতো তাহলে ইতিহাসের অনেক করুণ ঘটনাই হয়তো ঘটতো না।
সরকারী ও বিরোধী সব দলকে অত্যন্ত স্থির মস্তিকে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে, দেশের জন্য, তাদের দলের জন্য, এমন কি নেতাদের জন্যও কোন পথটা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ। নির্ভেজাল গণতন্ত্র দিলে সরকারী দলের গদীচ্যুত হবার আশংকা থাকলেও আবার জনসমর্থন নিযে গদী ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে। বিরোধী দল এক নির্বাচনে ক্ষমতা না পেলেও আবার সে সুযোগ আসতে পারে। তাই গণতন্ত্রের এমন নিরাপদ পথই সবার কাম্য হওয়া উচিত।
গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই। মনুষ্যত্বের উন্নয়নে বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ক্রটি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃতরূপে কল্যাণকর ব্যবস্থা রূপে দেখতে চাইরে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলে আমাদের যুব শক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগানের মোহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এ জন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠছে। বিপ্লবই যদি চাও তাহলে আস ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয় করলেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়, চরিত্রের বলে। এরই নাম গণতন্ত্র।
ইরানের বিপ্লব ঃ এ প্রসংগে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইরানে ইসলামের নামে যে বিপ্লব হলো তা গণতন্ত্রিক মাপকাঠিতে কতটা সমর্থনযোগ্য। ইরানে ডঃ মুসাদ্দেকের স্বল্পকালীন শাসনের সময় দেশকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে দেবার প্রচেষ্ট চলে। আমেরিকার সাহাযে শাহ পুনরায় ক্ষমতা পেয়ে দীর্ঘকাল ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে যেরূপ নৃশংসভাবে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় গোটা ইরানবাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। জনাব খোমেনী রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি। শাহর রক্তপাতের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ব্যর্থ হবার ফলে খোমেনীর দীর্ঘ আন্দোলন বিজয় লাভ করে।
ইরানের দীর্ঘ ইতিহাসে গণতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জনাব খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করারই চেষ্টা চলছে। শাপুর বখতিয়ার যদি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা খোমেনীর হাতে তুলে দিত তাহলে পরিস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য আরও উপযোগী হতো। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর দীর্ঘ সাধনা ও আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শক্তির ফলেই বামপন্থীদের ব্যাপক অস্ত্র লুট সত্ত্বেও ইসলামী শক্তি শেষ পর্যন্ত ময়দান দখল রাখতে সক্ষম হলো। সুতরাং ইরানে ১৯৭৯ এর বিপ্লব হঠাৎ কতক লোকের সশস্ত্র ক্ষমতা দখল জাতীয় কোন ব্যাপার নয়। বরং ব্যাপক জনসমর্থনের মাধ্যমেই ইরানী বিপ্লব সফল হয়েছে।
(বাংলাদেশের রাজনীতি)
সামরিক বিপ্লব
বিপ্লবের নামে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের যত ধরন হতে পারে তার মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সামরিক বিপ্লব হলো সবচেয়ে বেশী জঘন্য। অন্যান্য ধরনের বিপ্লবে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় এবং তাদের একাংশের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সামরিক বিপ্লবে জনগণকে জড়িত করার কোন দরকার হয় না। এমনকি জনসমর্থন ছাড়াই অস্ত্রবলে সামরিক শাসন চালু করা যায়।
সশসত্র বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানগণ দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হিসেইে গণ্য। তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় ব্যারাকে রেখে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়। দেশের স্বাধীনতার হেফাযতের জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত বলে বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ তাদেরকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বেশী পরিমাণে দেয়া হয় যাতে তারা নিশ্চিন্তে দেশরক্ষার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।
আইনগতভাবে যাদের হাতে বেসামরিক সরকারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তারাই সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এটা দুনিয়ার সব দেশে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত বৈধ নীতি। দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত বেসামরিক সরকারের নির্দেশ পালন করাই সশস্ত্র বাহিনীর আইনগত কর্তব্য। এমন কি কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার বৈধ দায়িত্বও বেসামরিক সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকে। সামরিক, বিমান ও নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। বেসামরিক কর্মচারীগণ যেমন সরকারের আনুগত্য করতে বাধ্য তেমনি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্যও তাই।
সামরিক সরকার সরকার অবৈধ ঃ প্রত্যেক দেশেই সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। কোন দেশেই সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার কোন আইনগত বিধান থাকে না। অথচ বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র বাহিনীকে সরকারী ক্ষমতা দখল করতে দেখা যায়। এ জাতীয় ক্ষমতা দখল কোথাও বৈধ বলে স্বীকৃত নয়। সরকারী কর্মচারী হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর এভাবে ক্ষমতা দখল কোন অধকারই নেই। “জোর যার মুলুক তার” যদি বৈধ নীতি বলে আইনে গণ্য হতো তাহলেও সামরিক বিপ্লবকে কোন রকমে জায়েজ বলা যেতো। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সামরিক আইন বৈধ কোন বিধানই নয়। সুতরাং সামরিক বিপ্লব নিঃসন্দেহে চরম দুর্নীতি ও জাতীয় পার্যায়ের ডাকাতি।
বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা শক্তিবলে কোন সরকারকে বেদখল করে সরকারী ক্ষমতা জবরদখল করতে পারে না। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র নেই এব্ং তারা প্রথকভাবে সুসংগঠিত কোন শক্তিও নয়। সশস্ত্র বাহিনী জনগণ থেকে আলাদাভাবে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল শক্তি হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তারা উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অন্ধভাবে পালনে অভ্যস্ত। তাই যখন এসব বাহিনীর দায়িত্বশীলগণ তাদের অধীনস্থ সবাই বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করেন। সশস্ত্র বাহিনীর এ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেই উচ্চাভিলাসী অফিসাররা সামরিক আইন জারি করার সুযোগ গ্রহণ করেন।
কিন্তু যে অস্ত্র বলে তারা বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন তা জনগণের টাকায় যোগাড় করা হয় এবং তা একমাত্র বেসামরিক সরকারের মরজী মতোই ব্যবহার করা কর্তব্য। এ অস্ত্র দ্বারা সরকারী ক্ষমতা দখল করা শুধু অবৈধই নয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে জনগণকে পরাধীনতার অফিশাপ থেকে হেফাযত করার উদ্দেশ্যেই তাদের হাতে এ অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। অথচ সে অস্ত্র দিয়েই জনগণকে গোলাম বানানো হয়-এর চেয়ে বড় বেঈমানী আর কী হতে পারে ? জনগণের কর্মচারী (চঁনষরপ ঝবৎাধহঃ) হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিপরীত আচরণই হলো সশস্ত্র বিপ্লব। অস্ত্রবলে জনগণকে গোলাম বানিয়ে দেশ শাসনের অপর নামই হলো সামরিক আইন প্রশাসন।
সামরিক শাসনের অভিশাপ ঃ যে দেশে একবার সামরিক অভিশাপ নেমে আসে সে দেশে গণতন্ত্র ্ও আইনের শাসন চালু করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। বিদেশে শক্তির অধীনতা থেকে মুক্তি প্ওায়ার চেয়ে দেশী সামরিক শাসন থেকে উদ্ধার প্ওায়া কম কঠিন নয়।
সামরিক শাসকরা গণতন্ত্রের দোহাই কম দেন না। তারা সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েমের মহান উদ্দেশ্যেই নাকি সামরিক আইন জারি করে থাকেন। সামরিক শাসন যে অবৈধ সে কথা অন্তরে তারা উপলদ্ধি করেন বলেই গণতন্ত্রের জপমালা হাতে নিতে তারা বাধ্য হন। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে তারা এমন ধরনের বেসামরিক সরকার গঠন করেন যা সামরিক সরকারেরই বেসামরিক চেহারা মাত্র। তাদের হাতেই মূল ক্ষমতা থাকে- শুধু সামরিক উর্দি গায়ে থাকে না।
১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন চালু করার পর বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সত্ত্বেও জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সামরিক শাসনের কুপ্রথা একবার চালু হলে তা থেকে নিস্তার পাওয়া স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
১৯৮২ সালের সামরিক শাসন ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার পর ১৯৮১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জনগণ বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে কারচুপির তেমন অভিযোগ শুনা যায়নি। বিপুল ভোটাধিক্যে বিচারপতি আবদুস সত্তার নির্বাচিত হন। চার মাস পর সেনাপতি এরশাদ কোন যুক্তিতে সামরিক শাসন চাপিয়ে দিলেন তা জনগণের নিকট অস্পষ্ট। বৃদ্ধ বিচারপতি যে বাধ্য হয়েই বন্দুকের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন সে কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি।
সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা ১৯৫৮ সাল থেকেই দেশবাসীর যথেষ্ট হয়েছে। কোন সামরিক শাসনই সঠিকভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনষ্ঠান করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু জেনারেল এরশাদ যে যোগ্যতার সাথে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন এর কোন তুলনা নেই।
এ সামরিক শাসন রাজনীতিকে যে পরিমাণ কলুষিত করেছে, জনগণকে যেভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, গদী রক্ষার প্রয়োজনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে যে পরিমাণ বাড়ার সুযোগ দিয়েছে এবং সুবিধাবাদী, নীতিহীন দলছুট ব্যক্তিদের দ্বারা যে ধরনে দুর্নীতিপরায়ন শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে এর কুফল থেকে এদেশ কতদিনে উদ্ধার পাবে তা আল্লাহই জানেন।
(বাংলাদেশের রাজনীতি)
সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতি
সশস্ত্র বাহিনীর সঠিক মর্যাদা বহাল রাখার প্রধান দায়িত্ব তাদেরই। সামরিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই তারা উপলদ্ধি করছেন যে যারা তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করেন তারা কোন কল্যাণ করেননি। সশস্ত্র বাহিনী রাজনীতিতে জড়িত থাকলে তারা কিছুতেই জনগণের আস্থাভাজন থাকতে পারবেন না। রাজনীতির ময়দানে দলাদলী ও মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। সশস্ত্র বাহিনী কোন এক দলের পক্ষে কাজ করলে অন্যসব দল কেমন করে তাদের প্রতি আস্থা রাখবে? সকল দলই যাতে সমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে আপন মনে করে সে পরিবেশ অবশ্যই বহাল রাখতে হবে।
জনগণের পক্ষ থেকে এ আস্থা বহাল করার যত আগ্রহই থাকুক সশস্ত্র বাহিনীর আচরণ এর প্রমাণ না দিলে এ আশা অন্য কোন পন্থায় পূরণ হতে পারে না। সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে সচেতন থাকলে পূর্বের ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস; জনগণকে একথা বুঝানো সম্ভব যে সরকারের নির্দেশেই সশস্ত্র বাহিনী কাজ করে থাকে। তাই সরকার যদি অন্যায় নির্দেশ না দেয় তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে জনগণের অধিকার হরণ করার মতো কোন অন্যায় কাজ কখনো করে না। সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করার ভ্রান্ত মতবাদ দেশের জন্য যে কত মারাত্মক সে কথা সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেককে অন্তর দিয়ে উপলদ্ধি করতে হবে।
ক্ষমতা দখলের পূর্বে জেনারেল এরশাদ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের সম্মেলন ডেকে ঐ ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মতো একটি সুশৃংখল শক্তিকে দেশ শাসনে যোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।
এ দাবীর ধুয়া তুলে হয়তো তিনি তার ক্ষমতা দখলের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ চিন্তাধারা চালু থাকলে সশস্ত্র বাহিনী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক স্বার্থের বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হতে বাধ্য। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করতে হলে এ কুচিন্তা ‘থেকে সংশ্লিষ্ট সবার মন মগজকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে হবে। এ অন্যায় দাবীর পক্ষে সামান্য যুক্তিও তালাশ করে পাওয়া যায় না। দেশ শাসন ও পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীকে কেন বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে? দেশের যারা মেধা ও প্রতিভার অধিকারী তারা সবাই কি সশস্ত্র বাহিনীতেই যোগদান করে? প্রথম বিভাগে পাশ করাও সেখানে ভর্তি হবার জন্য কোন শর্ত নয়। অথচ প্রথম বিভাগে পাশ না হলে মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সুযোগই পাওয়া যায় না।
আজ পর্যন্ত দেশেরই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ, কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগন, ব্যারিষ্টার ও ুকিলগন, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ শ্রেণীগতভাবে এ উদ্ভট দাবী পেশ করেননি যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদার করতে হবে। অথচ মেধা ও প্রতিভার বিচারে তাদের মান কি সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের থেকে নিু?
সুতরাং একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, অস্ত্র বলই ক্ষমতার দাবীর পেছনে আসল কারণ। কিন্তু এ অস্ত্র কি তাদের নিজস্ব? জনগণের রক্ত পানি করা শ্রমের প্রধান অংশই কি তাদেরকে সুসংগঠিত ও সশস্ত্র হবার যোগ্য বানায় নি? কী উদ্দেশ্যে এ গরীব দেশের বিরাট বাজেট তাদের জন্য বরাদ্ধ করা হচ্ছে ? দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই জাতি এতবড় ত্যাগ করছে। এ কুরবানী করতে হচ্ছে বলে জনগণ মোটেই অসন্তুষ্ট নয়। বরং হাসিমুখে আরও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। কারণ সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের দেশের আযাদী রক্ষার জন্য জীবন দিতে হবে। যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের জন্য জাতি সম্পদ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে কেন?
সশন্ত্র বাহিনীর সবার বিবেক ও সদিচ্ছার নিকট আকুল আবেদন জানাই যে, ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের যে ভ্রান্ত মতবাদ তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আশংকা রযেছে সে কুচিন্তা ত্যাগ করে জনগণের প্রাণপ্রিয় হতে হবে।
রাজনীতি ও অস্ত্র ঃ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, দেশের রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। পেশী ও অস্ত্রকেই যদি রাজনৈতিক ময়দান ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে দেশের আযাদী অবশ্যই খোয়াতে হবে। বিদেশের বলিষ্ঠতর পেশী ও শক্তিশালী অস্ত্র দেশী সশস্ত্র রাজনীতি সহজেই দখল করে নেবে।
রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করাতে হলে সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই রাজনীতি মুক্ত করতে হবে। একথা যতি সশস্ত্র বাহিনী অন্তর দিয়ে উপলদ্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে দেশকে-গৃহযুদ্ধ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কারণ ১৯৮৬ সালে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে এর তিক্ত অভিজ্ঞতা
জনগণকে তাদের ভোটাধিকার হেফাযত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। যেমন পুলিশ ডাকাত দমনে অবহেলা করলে জনগণ আইন তাদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং নিজেরাই ডাকাতকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়।
এরশাদ সাহেব দেশে যে রাজনীতি চালু করেছেন অবিলম্ েএর অবসান প্রয়োজন। তা না হলে এ রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়েই অস্ত্রের চর্চা সীমাবদ্ধ রাখবে না।
অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ না হলে আইন শৃংখলায় আরও অবনতি অবশ্যই হবে। যে লোকদের হাতে ব্যালট ডাকাতির জন্য অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে তাদেরকে দমন করার ক্ষমতা পুলিশ কোথায় পাবে? এরশাদ সাহেবের রাজনীতি চালু করার জন্য যে ছাত্র ও যুবকদেরকে অস্ত্র দেয়া হয়েছে তারা তো আইনশৃংখলা ভংগ করার সরকারী লাইসেন্সই পেয়ে গেছে।
এ দুরবস্থা থেকে নিস্তার পেতে হলে সর্বপ্রথম সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতির ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার বক্তব্য দেশ দরদী সকল মহলের প্রাণের কথা। এমন কি সশস্ত্র বাহিনীর ভায়েরাও এসব কথা যুক্তি বিবেক-সম্মত বলে মনে করবেন।
সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ
বাংলাদেশ আকারে ক্ষুদ্র একটি দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিরাট দেশ হিসেবেই গণ্য হবার যোগ্র। দশকোটি মানুষের একটি দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশ মোটেই নগণ্য নয়। এ দেশের মানুষ ১৯৪৭ সালে ইংরেজ থেকে আযাদ হয়ে পাকিস্তানে যেটুকু অধিকার ভোগ করছিল তাতে তারা সন্তুুষ্ট ছিল না বলেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের আশায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে একটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। স্বাধীনতার এ চেতনাবোধই দেশের আসল পুঁজি। এ পুঁজিই দেশের আসল রক্ষাকবচ।
একটি বিরাট দেশ বাংলাদেশকে প্রায় চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে আছে। ঐ দেশের জনগণের সাথে সবসময়ই এদেশের পক্ষ থেকে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ দেশের কোন সরকারের আচরণেই বাংলাদেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি।
বাংলাদেশের মতো আর কোন দেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে এমন বেকায়দায় নেই। এদেশের চার পাশে যদি কয়েকটি দেশ থাকতো তাহলে দেশ রক্ষা সমস্যা এত কঠিন হতো না। চারপাশে একটি মাত্র দেশ থাকায় এবং সে দেশটি বিরাট হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অবশ্য দুঃসাধ্য। প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সাথে ঐ দেশের আচরণের গত ৪০ বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই দেশ রক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থার গুরুত্ববোধ জনগণের মনে অত্যন্ত প্রবল।
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থারই দাবী রাখে। কোন কোন মহল এদেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে যা দেশরক্ষার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। তারা বলে যে, “একমাত্র ভারতই এদেশ আক্রমণ করতে পারে। ভারতের বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিহত করার মত শক্তিশালী দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা বাংলাদেশের সাধ্যের বাইরে। তাই এ গরীব দেশে এত বড় বাহিনী পোষার প্রয়োজনই নেই। আধুনিক বিশ্বের এক দেশের পক্ষে প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্র দখল করে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্ব জনমত এ জাতীয় অন্যায় দখল মেনে নেবে না। জাতিসংঘ ও দেশের জনগণই দেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট।
প্যালেষ্টাইন, লেবানন, আফগানিস্তান ও বিশ্বের আরও অনেক উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও যারা এমন উদ্ভট ধারণা পোষণ করেন তাদেরকে ভারতীয় লবীর অন্তর্ভুক্ত মনের করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ লবীর প্রভাবেই হয়তো মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবত ভারতের পক্ষ থেকে আক্রমণের তেমন কোন আশংকা তিনি করেননি। তাই দেশ রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে হয়তো তাঁর সরকারের প্রতিরক্ষার জন্যই রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা তিনি বেশী দরকার মনে করেছিলেন।
সশস্ত্র বাহিনী এ পলিসি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। প্রধানত এরই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় শেখ সাহেবকে জীবন দিতে হলো। রাষ্ট্র প্রধানকে এমন নির্মমভাবে স্বপরিবারে হত্যা করার মত করুণ ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও দেশের আপামর জনসাধারণের ঐ সময়কার আচরণ একথাই প্রমাণ করে যে, জনগণ শেখ সাহেবের নীতি সমর্থন করতে পারেনি।
যদিও দেশরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীই যথেষ্ট নয় এবং স্বাধীনচেতা জনগণের আবেগপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া প্রতিরক্ষা কিছুতেই সম্ভব নয়, তবুও সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া দেশরক্ষার চিন্তাও করা যায় না। জনগণের মনোবলের প্রধান ভিত্তিই সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল দেশরক্ষা বাহিনী। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের এলাকায় জনগণের মহব্বত, আবেগ ও সহযোগিতা সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে যেভাবে উদ্ধুদ্ধ করেছে তা আমি নিজের চোখে না দেখলে এ বিষয়ে এতটা দৃঢ় অভিমত পোষণ করতে পারতাম কি না সন্দেহ। বাংলাদেশকে বিদেশী হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সেনা, নৌ ও বিমাট বাহিনীকে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসজ্জিত করতে হবে। এরই পাশাপাশি জনগণকে বিশেষ করে যুবকদেরকে এতটিা সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে যাতে দেশবাসী যোগ্যতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে।
সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ সশস্ত্র বাহিনীর উপর দেশ রক্ষার যে মহান দায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করতে হলে তাদের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা থাকা প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা যদি অনুভব করে যে, জনগণ তাদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তবেই তারা দেশের জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দেবার প্রেরণা পাবে। জনগণ জানে যে, তাদের স্বাধীনতার হেফাজত করার পবিত্র দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর রয়েছে। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ব্যবস্থা না হলে বিদেশের গোলামে পরিণত হতে হবে। তাই সশস্ত্র বাহিনীকে যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতেই হবে। জনগণের মধ্যে এ অনুভূতি থাকলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দেশের সবাই সব রকম ত্যাগ ও কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবে।
সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি এ জাতীয় আস্থা ও ভালবাসা যাতে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে বিশেষ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও ঐ বাহিনীর দায়িত্বশীলদেরই। কারণ জনগণের আস্থা অর্জন করা ছাড়া তাদের পেশাগত সাফল্য কিছুতে সম্ভব নয়। এ আস্থা আপনা আপনিই সৃষ্টি হয় না। সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকলাপ ও আচরণ যে রকম হয় জনগণের মনে তাদের সম্পর্কে ধারণাও সে রকমই সৃষ্টি হয়।
সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাক এলাকায়ই থাকে। জনসাধারণের সাথে তাদের ঘনিষ্ট কোন যোগাযোগের সুযোগ হয় না। বেসামরিক ক্রিয়াকান্ডে তাদেরকে ব্যবহার করা হয় না। দেশ শাসনের কোন দায়িত্বও তাদের উপর থাকে না। তারা সেনানিবাস এলাকায় দেশের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পেশাগত ট্রেনিং নিয়েই নিয়মিত ব্যস্ত থাকেন। এটাই দুনিয়ার সব দেশে সাধারণ নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত।
এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জনগণের মনে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হবার কারণ ঘটে না। বরং মাঝে মাঝে জাতীয় কোন দুর্যোগে যখন বেসামরিক সরকারের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদেরকে জনগণের খেদমতের জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হয় তখন তাদের নিঃস্বার্থ সেবায় সর্ব সাধারণ মুগ্ধ হয় এবং তাদের প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে যায়।
এভাবেই সশস্ত্র বাহিনী জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পারষ্পরিক আস্থা গড়ে উঠে। যেসব দেশে সামরিক শাসন চালু নেই সেখানে এ আস্থা বিনষ্ট হবার কোন কারণ ঘটে না। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করলে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনগণের স্বার্থের কোন সংঘাতই সৃষ্টি হতে পারে না।
সামরিক শাসনের প্রধান কুফল ঃ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন দেশেই সামরিক শাসনের কোন সুফল দেখা যায়নি। একবার কোন দেশে সামরিক শাসন চালু হলে এ থেকে আর সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। বহু দেশেই এখনও সামরিক শাসন চালু আছে। প্রতিটি দেশেই দেখা যায় যে, যেসব সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে সামরিক শাসন জারী করা হয় সে সব সমস্যা তো সেখানে আরও বেড়েই চলে, তদুপরি অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।
এখানে সামরিক শাসনের যাবতীয় কুফল ও ঐ সব কুফল দেখা দেবার কারণ আলোচনা করার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বড় কুফলটি আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে পারষ্পরিক আস্থা ও ভালবাসার সম্পর্কের যে গুরুত্ব ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি সামরিক শাসনে সেটাই বিনষ্ট হয়ে থাকে।
১৯৮২ সালে জনগণের নির্বাচিত একটি সরকারই এ দেশ শাসন করছিল। ভাল হোক মন্দ হোক জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও এম, পিদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছিল। জনগণ তাদের কাছে পৌছতে পারত, তাদেরকেও জনগণের কাছে যেতে হতো। হঠাৎ করে ২৪শে মার্চ সকালে জনগণ জানতে পারল যে, সামরিক আইন জারী হয়েছে। তারা দেখল তাদের নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে সামরিক লোকেরা তাদের শাসক সেজে বসেছে। নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে সামরিক লোকেরা তাদের শাসক সেজে বসেছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও এম, পি এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত অগণিত লোকেরা ভালবাসা থেকে সশস্ত্র বাহিনী বঞ্চিত হলো। দেশ শাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সামরিক অফিসারগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বেসামরিক অভিজ্ঞ অফিসারদের কর্তা হয়ে বসল। এতে বেসামরিক সকল সরকারী কর্মচারীর মনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি মহব্বত
বৃদ্ধির কাম্য পরিবেশ আশা করা যায় না। এভাবেই সামরিক শাসন মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপর থেকে অস্ত্রবলে চাপিয়ে দেবার ফলে সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যতই দিন যায় ততই সামরিক লোকদেরকে বেসামরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনগণের নিকট অপ্রিয় হতে হয়। কারণ শাসনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাসিতদের নিকট জনপ্রিয় থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। এভাবেই সামরিক শাসনের পরিণামে সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে যে পারস্পারিক ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক তা বিনষ্ট হতে থাকে। আর দেশ রক্ষার জন্য এ অবস্থাটা অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
গণতন্ত্রের নামে সামরিক শাসকদের কর্তৃত্ব ঃ যদি কোন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন সাময়িকভাবে কায়েম করার পর গণতন্ত্রের নামে স্থায়ীভাবে সামরিক শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না চলে তাহলে সশস্ত্র বাহিনীর জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হয় না। যেমন কিছুদিন পূর্বে সুদানে জেনারেল সুয়ারুয্যাহাব জেনারেল নুমেরীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সামরিক আইন জারি করার এক বছরের মধ্যেই নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। নির্বাচনে তিনি কোন দলের পক্ষ অবলম্বন না করায় জনগণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পেরেছে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি জেনারেল আবদুর রহমান সুয়ারায্যাহার গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে প্রহসনমূলক নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতেন তাহলে সুদানে অশান্তি আরও বেড়ে যেতো এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতো।
জেনারেল এরশাদ যদি তেমনিভাবে দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে তাদের মর্জি মতো সরকার গঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বেড়ে যেতো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এরশাদ সাহেব সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিই অবলম্বন করেছেন।
১৯৮২ সালের মার্চ মাসে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে তিনি সামরিক শাসন দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন। দেশে এমন কোন পরিস্থিতিই ছিল না যাতে তখন সামরিক আইন জারি করার সামান্য কোন অজুহাতও দেখানো চলে। প্রেসিডেন্ট আবদুস সত্তার সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেই তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখল করাটাই ছিল চরম দুর্নীতির পরিচায়ক এ জন্যই গত চার বছরের শাসনে দুর্নীতি যে কত বেড়েছে তা কারোরই অজানা নয়।
গণতন্ত্র হত্যা করে ক্ষমতা দখলের পর জনগণের সরকার কায়েমের দোহাই দিয়ে তিনি চরম অগণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসী পন্থায় পার্লামেন্ট নির্বাচন করে তার দলকে ক্ষমতাসীন করলেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাই ১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন করে। ফলে এক প্রহসন মূলক নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোসিত হন। এ দ্বারা তিনি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কোন সুনাম বয়ে আনেননি। তবে সামরিক আইন উঠে যাওয়ার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (বাংলাদেশের রাজনীতি)
গণতন্ত্রের দুর্গতি কেন ?
দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। আশা করা গিয়েছিল যে, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসে দেশ শাসনের দায়িত্ব পেলেন তারা জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই চালু রাখবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও শাসকগণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে থাকলেন। ফলে ক্রমেই তারা জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা আমলাদেরকে এমনভাবে ব্যবহার করতে থাকলেন যে, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বুঝতে পারলেন শাসকদল জনগণের সমর্থনের চেয়ে তাদের সাহায্যেই গদীতে বহাল থাকতে চান। তখন তারা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
এমনি এক পরিস্থিতিতে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে যোগসাজশে সেনাপতি আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দেন। জনগণ নিজেদেরই বেতনভুক্ত কর্মচারীদের হাতে বন্দী হয়ে ইংরেজ আমলের চেয়েও কঠোর রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।
১৯৬০ সাল থেকে নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠিনতর সংগ্রামে পরিণত হলো। দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলনের পর ১৯৬৯ সালে যে গোলটেবিল বৈঠক হয় তা যদি সফল হতো তাহলে গণতন্ত্র হয়তো বহাল হতো। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে দলটি নিরংকুশ বিজয় লাভ করলো তাদের হাতে ১৯৭২ সালে ক্ষমতা আসার পরও গণতন্ত্র কেন টিকে থাকলো না সে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে বড় হয়েই দেখা দেবার কথা।
দু'টো বিষয়ের বিশ্লেষণ ঃ আজও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদেরকে ধীর মস্তিস্কে চিন্তা করতে হবে যে, দু-দু’বার স্বাধীনতা অর্জন করেও গণতন্ত্রের পথে আমরা সামান্য অগ্রগতিও কেন লাভ করতে পারলাম না। এ প্রসঙ্গে দু'টো বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। প্রথমত আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব যে, স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ কেন হলো না। দ্বিতীয়ত আমরা হিসেবে নিয়ে দেখব যে, গণতন্ত্রের পথে আমাদের দেশে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। রোগের কারণ না জানলে সঠিক চিকিৎসা হতেই পারে না। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে যদি কোন প্রকারে একটি নির্বাচিত সরকার কায়েম করতে সক্ষমও হই, তবু আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বহাল রাখতে পারব না যদি ঐসব দোষ-ক্রটি ও প্রতিবন্ধকতা রাজনৈতিক নেরতা ও দলগুলোর মধ্যে থেকে যায়। গণতন্ত্রের পরিপন্থী বিষয়গুলো যদি আমাদের থেকে দূর করা না যায় তাহলে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে আমার নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে হবে। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়েই উপরোক্ত দু'টো বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।
আমি আশা করি সকল রাজনৈতিক মহলই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমার বিশ্লেষণকে বিচার করবেন। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের নিষ্ঠা আছে তরা এ আলোচনার মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ পাবেন। আসুন আমরা সবাই গণতন্ত্রের স্বার্থে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি।
বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেন বহাল রইল না ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যে দলটি এককভাবে মহাবিজয় লাভ করে সে দলটিই বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত একটি দল বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন চালু রাখতে পারলো না তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।
উদার দৃষ্টিতে এবং সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ
(১) একটি সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এ নতুন রাষ্ট্রটি কায়েম হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে অস্ত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য অনেকদিন পর্যন্ত বহাল থেকে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুযোগ এমন বহু সুসংগঠিত গ্র“প ও উপদলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এসে যায় যারা “বন্দুকের বুলেট দ্বারা বিপ্লব সাধনের নীতিতে” আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। ৭২ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার কায়েম হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব উপদল অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করেনি। তাদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য সরকারকেও রক্ষীবাহিনী ব্যবহার করতে হয়েছে। এমন কি বেসামরিক পর্যায়েও সরকার সমর্থক এবং সরকার বিরোধীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বহু জায়গায় অস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যেভাবে রাজনৈতিক গোপন হত্যা চলেছে তাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।
(২) গণতন্ত্রের সঠিক পরিবেশের পূর্বশর্ত হলো জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বৃহত্তম ঐক্য থাকা। শাসনতন্ত্রের এমন সব মতবাদকে জাতীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছিল যা দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান আকিদার বিরোধী ছিল। ফলে গণমনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং সরকার বিরোধী যে কোন আওয়াজই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। সরকারী দলেরই একাংশ নতুন দল সৃষ্টি করে চরম সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হয়। তারা এমন আকত্রমণাত্মক ভাষায় সরকারের সমালোচনা করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে থাকে। কোন কোন সশস্ত্র উপদল এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক শাসন স্বাভাবিক গতিতে চলতে ব্যর্থ হয়।
(৩) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করে যে, স্বাধীনতা লাভ করার দু’বছরের মধ্যেই মানুষ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। এ অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ভারতই দায়ী বলে জনগণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে ভারতপন্থী বলে বিবেচনা করার কারণে সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বিলীন হয়ে যেতে থাকে। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা তখন ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে গণমনের এ তীব্র বিদ্বেষ সরকারকে চরম বেকায়দায় ফেলে দেয়।
(৪) এক শ্রেণীর অতি উৎসাহী ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রীর আচরণ ও কার্যকলাপ এবং সরকারের কতক সিদ্ধান্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে এমন আঘাত হানে যে, দেশের ছোট-বড় ওয়ায়েজগণ জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে সজাগ রাখার উদ্দেশ্যে যে আবেগময় বক্তব্য রাখেন তা-ও পরোক্ষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করতে থাকে।
(৫) উপরোক্ত কারণসমূহ সরকারের জন্য এমন কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় এর মোকাবিলা করা অসম্ভব বলে সরকার মনে করে। শেষ পর্যন্ত সরকারী দল তাদের নেতার জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে পূর্ণ একনায়কত্ব কায়েমের মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তারা এমন এক শাসন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় যা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে গণতন্ত্রের সকল পথই বন্ধ হবার আশংকা দেখা দেয়। এ ব্যবস্থা চালু হবার প্রাক্কালেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের দুর্ঘটনা ঘটে।
(৬) উপরে বর্ণিত কারণসমূহ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতা এবং তার ব্যাপক গণসমর্থন পুষ্ট দল জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেও দেশকে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নেবার বদলে একনায়কত্ত্বের ভ্রান্ত পথে কেন পা বাড়ালেন ? শেখ মুজিব আজীবন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি কেন জনগণের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কেন তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এগিয়ে নিতে পারলেন না ?
পরলোকগত শেখ মুজিব সাহেবের প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশের ইতিহাসে চিরদিনই উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকবেন। তাই এদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে তাঁর উল্লেখ না হয়েই পারে না। যারা আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ চান এবং যারা সাধ্যমতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করেন। তাদের নিকট আমার বিনীত অভিমত প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করছি। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ বিষয়ে আলোচনা করা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি।
(ক) ইংরেজ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে না দেবার ফলে রাজনৈতিক ময়দানে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদেরকে বাধ্য হয়ে অগণতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে বিরোধী দলীয় রাজনীতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের বদলে অমরঃধঃরড়হধষ চড়ষরঃরপং (বিক্ষোভের রাজনীতি)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা গঠনমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রায় অসম্বব। এরই ফলে শেখ মুজিব সরকার বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও দেশ শাসনের জন্য যে ধরনের সুস্থির নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে তুলবার প্রয়োজন ছিল তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাই দেশের নিরস্কুশ ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি জাতিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।
(খ) প্রায় আজীবন রাজনীতির ময়দানে সংগ্রামরত থাকার ফরে এবং বার বার কারাভোগ করার দরুন তাঁর মধ্যে আবেগ প্রবণতা এতটা প্রবল হয়ে পড়েছিল যে, জাতীয় পর্যায়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি আবেগ দ্বারাই বেশী পরিচালিত হয়েছেন বরে আমার ধারণা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে কাজ করা ও মত বিনিময় করার মাধ্যমে আমি তাঁকে যতটুকু বুঝেছি তাঁতে আমার যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের যতগুলো গুণ দিয়েছিলেন যদি প্রজ্ঞার সাথে তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে এদশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো।
আমার ধারণায় নেতার মধ্যে প্রজ্ঞার চাইতে আবেগ বেশী থাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কর্মীদের মধ্যে আবেগই প্রবল থাকা দরকার যাতে তারা নেতার নিদের্শে জীবন দিতে দ্বিধা না করে।কিন্তুু নেতার মধ্যে প্রজ্ঞা ্ও দূরদশিতার চেয়ে আবেগ প্রবল হ্ওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ আবেগচালিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভ্রান্তির আশংকা প্রবল।
(গ) তাঁর সংগ্রামী জীবনে রাজনৈতিক নেতিবাচক কর্মকান্ডের প্রাধান্য থাকার দরূন তাঁর সংগঠনে বিভিন্ন চিন্তাধারা ্ও মতবাদের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাই দেশ গড়ার লক্ষ্যে আদর্শ কর্মনীতি ্ও কর্মসূচীর যে ঐক্য তার সংগঠনে থাকা প্রয়োজন ছিলো তার অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত যেন অনেকটা অসহায় হয়েই একদলীয় শাসন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন।
(ঘ) তাঁর দলে যারা কট্রর সমাজতন্ত্র ছিলেন তারা বুঝতে পারলেন যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে তাদের কাঙ্খীত সমাজ ব্যবস্থা চালু করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই তারা বিভিন্নভাবে দল যেভাবে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল তাতে হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রীক পদ্ধতিতে এক দলীয় সরকার কায়েম করা হলে তাদের সমর্থন ্ও প্ওায়া যাবে।
গণতন্ত্র পথে প্রতিবন্ধকতা ঃ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের পথে নিম্নরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা দূর করা ছাড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারে না ঃ
১। আইয়ুব খানের আমল থেকেই এ কুপ্রথা চলে এসেছে যে, সামরিক একনায়কগণ ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠনের অপচেষ্টার মাধ্যমে রাজনীতিতে চরম দুর্নীতি চালু করে। তারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো থেকেই স্বার্থের বিনিময়ে নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে কিনে নেয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিপন্ন হয়।
২। সামরিক একনায়ক যেসব নেতাকে কিনতে সমর্থ হয় না, সেসব দলের নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে যাতে কোন দল তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার যোগ্যতাই না রাখে।
৩। রাজনৈতিক ময়দানে এভাবেই সুবিধাভোগী এবং ক্ষমতালিপ্সুদের ভিড় বারতে থাকে ও এ জাতীয় লকেরাই নেতা হওয়ার জন্য নতুন নতুন দল সৃষ্টি করে। এ জাতীয় লোকদের কারনেই রাজনীতি করাকে অনেকে সুধী, জ্ঞানী এবং চরিত্রবান লোক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না এবং তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে আস্তে চায় না। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে নৈতিক এবং আদর্শিক মান হ্রাস পেতে থাকে।
৪। আমাদের দেশে ১০০ টিরও বেশী রাজনৈতিক দল আছে বলে জানা যায়। এটা মোটেই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। গুটিকতক লোক নিয়ে দল গঠনের এ হিড়িকের পেছনে অগণতান্ত্রিক মনোভাবই প্রধানত দায়ী। যেসব মনোবৃত্তির জন্য কথায় কথায় দল সৃষ্টি হচ্ছে সে সবই গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক। অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ধরন কয়েক রকমের দেখা যায়। যেমন-----
ক। দলের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব যার হাতে থাকে তিনি দলীয় সংবিধান, আদর্শ এবং নীতি অগ্রাহ্য করে নিজ খেয়াল খুশি মত সিদ্ধান্ত নিলে সংগত কারনেই দল ভেংগে যায়।
খ। দলের সাংগঠনিক পদ্ধতিতে নেতৃবৃন্দের সমালোচনা এবং সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে উপদল সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমে দলে ভাংগন সৃষ্টি করে।
গ। দলীয় আদর্শ এবং নীতির চেয়ে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হবার কারনে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি হবার ফলেও একদল ভেংগে কয়েক দল তৈরি হয়।
ঘ। দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় অধিকাংশ সদস্যের রায়ের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করাই গনতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ যদি সংগঠনের সংবিধানের চেয়ে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকাংশের মত মেনে না নেয় তাহলেও দল ভেংগে যায়।
ঙ। এদেশে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দল থেকে বহিস্কার করা হলে সে ব্যক্তিই পাল্টা দল গঠনের ঘশনা দিতে একটুও লজ্জাবোধ করে না।
উপরোক্ত প্রতিটি মনোভাব সুস্পষ্টরূপে গনতান্ত্রিক চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জাতীয় মনোভাবের দরুনেই এদশে প্রায় একই নামে আধা ডজন দলের অস্তিত্ব দেখা যায়।
৫। কোন সময় আদর্শের ঐক্য সত্ত্বেও কর্মনীতি এবং কর্মসূচীতে মতের পার্থক্য হতে পারে ও এর ফলে এক সংগঠনে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। গনতান্ত্রিক নিয়মে এঅবস্থায় অধিকাংশ লোকের মতামতের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। যারা ভিন্ন মত পোষন করে তারা নিজেদের নিজস্ব কর্মসূচী ও কর্মনীতি নিয়ে ভিন্ন নামে দল গঠন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের মতকে অগ্রাহ্য করে তারা যদি মূল দলের নামটিকে ব্যবহার করে তাহলে নিঃসন্দেহে তা গণতন্ত্র বিরোধী।
৬। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভাষার পারস্পরিক আক্রমণ চলে, বিশেষভাবে সরকারী এবং বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনার যে নিম্নমান কখনো কখনো দেখা যায় তা- ও গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
৭। গণতন্ত্রের রুপায়নের পথে সব চাইতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হল – দৈহিক শক্তির প্রয়োগ করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধিতা করা। এ মারাত্মক রোগ যে দলে আছে সে দলে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হলেও তারা শক্তির দাপটেই মীমাংসা করার চেষ্টা করে।
এ জঘন্য মনোবৃত্তিটি যাদের মধ্যে আছে তারা চিন্তার ক্ষেত্রে আসলেই দুর্বল। তারা যুক্তির বলে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় অক্ষম বলেই শক্তির আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ময়দানে শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ কুপ্রথা এদেশে সরকারী দলেরই অবদান। পাকিস্তান আমল থেকেই তা চলে এসেছে। সরকারী দল বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য গুন্ডাদল পোষার এ জঘন্য প্রথা আজো পুরা দস্তুর চালু রেখেছে।
মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে, রাজনৈতিক ময়দানে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা একটি আধুনিক মতবাদের কর্মনীতি হিসেবে স্বীকৃত। তারা আফগানিস্তানে রাশিয়ার অমানবিক হামলায় লজ্জাবোধ করেনি। এদেশেও কাবুল স্টাইলের বিপ্লব করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে তাদের গণতন্ত্রে কোন দোষনীয় কাজ মনে হয় না।
আমরা যদি সত্যিই গণতন্ত্র চাই এবং গনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তি, উন্নতি এবং প্রগতি কামনা করি তাহলে রাজনৈতিক অংগন থেকে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।
ক্ষমতার রাজনীতি বনাম আদর্শিক রাজনীতিঃ
আমাদের দেশে রাজনৈতিক ময়দানে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকার আসল কারন হলো ক্ষমতার রাজনীতি। যে কোন উপায়ে সরকারী ক্ষমতা দখল করাই যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যা হওয়া স্বাভাবিক আমাদের দেশে তাই ঘটছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় বিরোধীদলের যোগ্য ভুমিকার মাধ্যমেই যে দেশের যথেষ্ট সেবা এবং কল্যাণ করা সম্ভব সে কথা যদি আমাদের বুঝে আসে তাহলে ক্ষমতা দখল করার জন্য গণতান্ত্রিক এবং অরাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করার কুপ্রথা এদেশে এতোটা চালু থাকতে পারবে না।
আইয়ুব খানের কর্মচারীর মর্যাদা নিয়ে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মন্ত্রী এবং গভর্নর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শ থাকতো তাহলে কিছুতেই এমন অরাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন না। যে ব্যক্তি জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্র বাতিল করে এবং জাতীয় নির্বাচন বন্ধ করে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব ফেলে রেখে দেশ শাসনের বোঝা অন্যায়ভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিলো তার এ জঘন্য কাজে যদি রাজনৈতিক নেতারা সহযোগী না হতেন তাহলে পরবর্তীকালে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না।
যারা নিজেকে কায়েম করার জন্য রাজনীতি করে তারা যে কোন ভাবেই ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তালাশ করে। আর যারা দেশ এবং জাতির কল্যাণ লাভের মহান উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতা লাভকে আসল লক্ষ্য মনে করেন না। দেশ সেবার আদর্শ যাদের আসল লক্ষ্য তারা কোন একনায়কের কাছে মন্ত্রিত্ব ভিক্ষা চাইতে পারে না। রাজনৈতিক ময়দানে এ জাতীয় ভিক্ষুকরাই সামরিক শাসনের জন্য আসল দায়ী। এ জাতীয় লোক বাজারে না পাওয়া গেলে সামরিক শাসন বার বার জাতির ঘাড়ে চেপে বসতে পারতো না।
ব্যক্তি ভিত্তিক রাজনীতিঃ
রাজনৈতিক দল আদর্শ, মত এবং চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত হওয়াই উচিত। কিন্তু কোন দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যখন দলীয় নেতাকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর নেতারা একনায়কের মর্যাদা দিয়ে বসে তখনই দলটি ব্যক্তি ভিত্তিক হয়ে পড়ে। “এক নেতা এক দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ” শ্লোগান দিয়ে যখন শেখ মুজিবকে অতি মানব বানিয়ে দেয়া হলো তখন সে ব্যক্তির নামটাই দলের আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়ে গেলো।
জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী তার সমর্থকদেরকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নামে আলাদা দল গঠন করার পরও তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নামই নিলেন। ফলে মূল আওয়ামী লীগের সাথে পাল্লা দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহন করলেন তখন চৌধুরী সাহেব দলের নামই ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।
তেমনি অবস্থা নিএনপির মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের আদর্শই যখন দলের আদর্শে পরিনত হয়ে গেলো তখন এ দলের নাম নিয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বের সাথে প্রতিযোগিতা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি ভিত্তিক দলের নেতৃত্ব ঐ বংশের হাতে থাকাই স্বাভাবিক। পাকিস্তানের মিঃ ভুট্টর দল পি, পি, পি- এর মধ্যে এ অবস্থাই বিরাজ করছে। এমনকি ভারতে গণতন্ত্র মোটামুটি চালু থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহেরুর বংশেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব এ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে আছে। এটা কোন অবস্থাতেই গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। রাজতন্ত্রেরই পরিচায়ক। এতে বুঝা যায় যে, সত্যিকার গনতন্ত্র এখনো ভারতে কায়েম হয়নি।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
আদর্শিক রাজনীতি
ডুগডুগি বনাম আদর্শের রাজনীতি
সম্মানিত পাঠকবর্গ মাফ করবেন। ডুগডুগির চেয়ে কোন শালীন উদাহরণ যোগাড় করতে পারলাম না। রাজনীতির ময়দানে এদেশে দলের সংখ্যার হিসেব নেই। অনেকেই আদর্শের নাম নেয়। তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আদর্শভিত্তিক রাজনীতি এদেশে অতি দুর্বল। এর আসল কারন বিশ্লেষণ করতে হলেই ডুগডুগির উদাহরণ দিতে হয়। বানর বা ভল্লুক নাচে এখনো ডুগডুগির ব্যবহার চালু আছে। আমি যে উদাহরণের জন্য “ডুগডুগি” শব্দ ব্যবহার করছি সে ময়দানে কিঞ্চিত উন্নতি হয়েছে। আজকাল সেখানে মেগাফোন বা মাইক ব্যবহার করা হয়। ময়দানটা হল হাতুড়ে চিকিৎসার।
দেশে জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। চিকিৎসার অভাব থাকায় রোগ বেড়েই চলেছে। যেটুকু চিকিৎসা আছে তাও পয়সার অভাবে অনেকেই পায় না। জনগনের মধ্যে শিক্ষার অভাব। তাই হাতুড়ে চিকিৎসার ময়দান এখনো যথেষ্ট প্রশস্ত। শহরে বন্দরে বাজারে আজকাল মেগাফোন, মাইক লাগিয়ে হাতুড়ে ডাক্তার বা তার এজেন্ট চিকিৎসা চালায়। আগে এক্ষেত্রেই ডুগডুগির ব্যবহার করা হতো।
ডুগডুগি এবং মাইক দিয়ে লোকজন জড়ো করার জন্য কোন খেলা বা যাদুর নামেও ডাকা হয়। লোক জড়ো হয়ে গেলে বেশ কায়দার সাথে কথা বলা হয়। মানব দেহে যত রোগ আছে যোগ্যতার সাথে তা এক নিঃশ্বাসে সব বলার পর একটি মাত্র তাবিজ, গাছের শিকড় বা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ দ্বারা রোগমুক্ত হওয়ার এমন আশার আলো দেখানো হয় যে, শ্রোতা নিজের কিংবা পরিবারস্থ রোগীর চিকিৎসা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে এ হাতুড়ে চিকিৎসাই সম্বল বলে মনে করে।
হাতুড়ে রাজনীতিঃ
যেসব কারনে মানুষ হাতুড়ে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হয় সে ধরনের পরিবেশেই জনগন হাতুড়ে রাজনৈতিকদের পাল্লায় পড়ে। রাজনৈতিক ডুগডুগি বাজিয়ে বিরাট হই চৈ সৃষ্টি করে জনসভায় লোক জমায়েত করা হয়। যোগ্য হাতুড়ে ডাক্তার মঞ্চে অতি নিপুনতার সাথে জনগনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে দেশে যত সমস্যা আছে সব একনাগাড়ে শুনিয়ে দিয়ে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দেয়। সমস্যা জর্জরিত মানুষ সে দরদী আওয়াজ কান লাগিয়ে শুনে। সমাধান তারা জানে না। কিন্তু সমাধান পেতে চায়। সমস্যার সুচিকিৎসক কারা তা চিনবার ক্ষমতাও তাদের নেই। যারা তার রোগ নিয়ে এতো দরদ দেখাচ্ছে তাদের কাছ থেকেই চিকিৎসা আশা করছে। হাতুড়ে রাজনীতিবিদ তখন তার দলকে ভোট দিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সে কথা জানিয়ে দিয়ে জনগনের প্রতি পবিত্র দায়িত্ব পালন করে।
হাতুড়ে ডাক্তারের তাবিজে বা ঔষধে যে রোগ সারে না বরং রোগ বাড়ায় এ অভিজ্ঞতা যদি কারো চোখ খুলে দেয় তাহলে সে পাশ করা আসল ডাক্তার তালাশ করে। তেমনি হাতুড়ে রাজনীতির কুফল ভোগ করার পর যদি জনগনের বুঝবার যোগ্যতা হয় কিংবা সুচিকিৎসকগণ যদি তাকে বুঝাতে সক্ষম হয় তাহলে হাতুড়ে রাজনীতিবিদদের হাত থেকে বাচার উপায় হতে পারে।
ডুগডুগি রাজনীতির আর বড় একটা লক্ষণ আছে। রাজনৈতিক ময়দানে সুস্থ পরিবেশ এবং মুক্তবুদ্ধি তাদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তারা মানুষের এমন এক ভাব প্রবণতার সৃষ্টি করে যাতে জনগন জোশের বশবর্তী হয়ে হুশ হারিয়ে তাদের ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। আবেগময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারই তাদের রাজনীতি।
গণতান্ত্রিক রাজনীতিঃ
সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে, দেশের সমস্যাবলীর সত্যিকারের সমাধান দিতে হলে এবং জনগনের সুখসমৃদ্ধি আন্তরিকভাবে চাইলে এ জাতীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজতন্ত্র নামক আদর্শের নাম নিয়েও ডুগডুগি রাজনীতি করতে দেখা যায়। সমাজতন্ত্র যদি কল্যাণের আদর্শই হয় তাহলে মানুষকে ধীরভাবে বুঝানো যাবে না কেন ? মানুষের মনে শ্রেনী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ময়দানে হিংসার আগুন জ্বালানোর কারন কি ? শোষকের সংখ্যা সামান্য- শোষিতই প্রায় সবাই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে তাদের স্বার্থের কথা বুঝাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা এ পথ পছন্দ করেন না। বন্দুকের নল ছাড়া মানুষকে নাকি বুঝানো যায় না। তাই তাদেরকেও ডুগডুগির আশ্রয় নিতে হয়।
এ বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করার জন্য আরো একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। মানুষ রাজনীতি করে কেন ? উদ্দেশ্যহীনভাবে কেউ কাজ করে না। রাজনৈতিক ময়দানে কে কোন উদ্দেশ্যে নেমেছেন তার ভিত্তিতেই একের রাজনীতি অন্যের থেকে পৃথক হয়। মুখে নীতি কথা যাই বলুক, একটি দলের কর্মনীতি এবং কর্মপদ্ধতি থেকেই তার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বুঝা যায়। জনগন যে পর্যন্ত এসব কথা বুঝবার যোগ্য না হবে ততদিন তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে না। এসব কথা বুঝবার জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা জরুরী নয়। ছাত্র সমাজের একাংশ কি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ডুগডুগি রাজনীতির হাতিয়ার নয় ? আসল হল রাজনৈতিক চেতনা এবং অভিজ্ঞতা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু থাকলে অশিক্ষিত জনগণও এ শিক্ষা পেতে পারে।
রাজনীতির উদ্দেশ্য
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকলে রাজনীতিও থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে রাজনীতির উদ্দেশ্য কি ? রাজনীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সরকারী ক্ষমতা অর্জন। এক্ষনে জিজ্ঞাসা সরকারী ক্ষমতা চাইবারই বা উদ্দেশ্য কি ? সরকারী ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যও একাধিক হতে পারেঃ
*১। ক্ষমতার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা
ক্ষমতার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা চাওয়া জঘন্যতম কাজ। এটাকে বলা যায় জাতীয় ডাকাতি এবং জনগনের বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র। জনগনের সেবার দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে শক্তির ব্যবহার দেখানো এবং জনগনের ক্ষমতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গোষ্ঠী বিশেষের মর্জি ও স্বার্থ মোতাবেক কাজ করাকে জাতীয় ডাকাতি না বলে আর কি-ই বা বলা যেতে পারে ? ক্ষমতা হাতে পেয়ে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা, স্বজনপ্রীতি এবং ভোগবিলাসের মাধ্যমে সরকারী সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, জনগনের স্বার্থের অপচয় এবং তাদের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা যারা করে তাদের এ সমস্ত কার্যাবলী নিঃসন্দেহে জনগনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা। প্রকৃতপক্ষে এটা ক্ষমতালোভীদের স্বভাব। এটাই হচ্ছে ক্ষমতার রাজনীতি।
*২। জনসেবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা
জনসেবার দায়িত্ব কঠিন এবং ত্যাগ সাপেক্ষ। বিনা স্বার্থে ব্যক্তিগত গরজে মানুষ এ দায়িত্বের বঝা কাঁধে নেয় না। কেননা এ দায়িত্বের কামনা করা নিঃস্বার্থ লোকদের জন্য অস্বাভাবিক।
শুধু জনসেবার দোহাই দিলেও এটাই ক্ষমতার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। জনসেবার নামে ক্ষমরা দখল করে পার্থিব যাবতীয় স্বার্থেই কাজ করা হয়। অবশ্য বুদ্ধিমানরা এক্ষেত্রে জনসেবা এতোটুকুই করে যেতোটুকু করলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে। এক কথায় এখানেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাই রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায়।
*৩। আদর্শের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা
আদর্শের দোহাই দিয়েও অনেকে ক্ষমতা লাভ করে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এটা প্রায়শই ঘটে থাকে। কিন্তু মুখে আদর্শের কথা আওড়ালেও তাদের কাজে কিংবা চরিত্রে সে আদর্শের প্রতিফলন না ঘটলে তাদের কুমতলব ধরা পড়ে যায়। এ ধরনের লোক আদর্শের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। সুতরাং কোন জনপ্রিয় আদর্শের দোহাই দিলেই কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।
পর্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার যে, যে আদর্শের দোহাই দেয়া হচ্ছে বাস্তব কার্যকলাপে তার নিদর্শন পাওয়া যায় কি- না।
গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দোহাই
ক। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে অনেকে ক্ষমতা পায়। কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই দিলেই কেউ গণতন্ত্রী হয়ে যায় না। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র আছে কি- না, দলের কর্মীদের সাথে গণতান্ত্রিক আচরণ করা হয় কি- না, দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা হয় কি-না তার উপরই নির্ভর করে ঐ দলের গণতন্ত্রের প্রকৃতি। যে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই সেই দল ক্ষমতায় গিয়ে গনতন্ত্রকে ক্ষতম করাই প্রধান কর্তব্য মনে করে।
গণতান্ত্রিক নেতার ভাষা এবং বক্তৃতার ভঙ্গী থেকেই তাকে এবং তার দলকে চেনা যায়। যুক্তির বদলে যারা শক্তির হুমকী দেয়, হৃদয়ের আবেদন বাদ দিয়ে যারা হাত ও পায়ের দাপট দেখিয়ে বক্তৃতা করে, প্রতিপক্ষকে যারা গায়ের জোরে দমাতে চেষ্টা করে, গ্রেনেড এবং হাতবোমা দিয়ে যারা “রাজনৈতিক শত্রুর মোকাবেলা করে” তাদের পরিচয় স্পষ্ট।
খ। সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী হয়ে যারা গণতন্ত্রের দোহাই দেয় তারা অশিক্ষিত লোকদেরকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানাতে সক্ষম হলেও রাজনীতি সচেতন লোকদেরকে ধোঁকা দিতে অক্ষম। কারন সচেতন লোকেরা জানে সমাজতন্ত্রীরা একবার কোথাও ক্ষমতায় আসতে পারলে সে দেশে চিরদিনের জন্য গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহীগন গণতন্ত্রের মাধ্যমে একবার কোনরকমে ক্ষমতায় যেতে পারলে গনতন্ত্রকে হত্যা করাকেই তারা নিজেদের পহেলা নম্বর কর্তব্য বলে মনে করে।
গ। ইসলামের নামে রাজনীতিঃ ইসলামের আদর্শবাদী না হয়েও কেউ কেউ ইসলামের নাম নিয়ে রাজনীতি করে থাকেন। তাই ইসলামের নাম নিয়ে ক্ষমতা পেলেই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসই এর সাক্ষী। ইসলামের নামে মুসলিম জনতাকে পাগল করে, অসংখ্য মুসলমানের রক্তের উপর ভিত্তি করে, হাজার হাজার মা- বোনের ইজ্জত আব্রু বিকিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের ধন সম্পদ বাড়ী ঘর ধংস করে তাদেরকে পথের ভিখারী বানিয়ে যারা ক্ষমতায় বসলেন তাদের হাতেই ইসলামের দুর্দশা ঘটলো।
যারা ইসলামের জ্ঞান রাখে না, ইসলামকে জানার চেষ্টা করেনা, যেটুকু জানে তাও বাস্তবে মেনে চলে না, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কেবল মুখে ইসলামের কথা বলে, তাদের দ্বারা সমাজে কিভাবে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে ? যারা নিজেদের সাড়ে তিন হাত দেহে, কয়েক ইঞ্চি জিহ্বায় এবং দেড় ইঞ্চি চোখে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, তাদের দ্বারা একটা দেশে কিভাবে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে ? কক্ষনো হতে পারে না। যারা নিজেদেরকে ইসলামী নীতিতে চালাতে পারে না। তারা গোটা জাতিকে কি করে ইসলামের আদর্শে পরিচালিত করতে পারে ? তাদের এ অধিকার বা যোগ্যতা কোনটাই নাই। এ জাতীয় লোকদের দ্বারা ইসলামের নামে ধোঁকাবাজি কিংবা প্রতারণা বৈ আর কিছুই হতে পারে না।
ইসলামের নামে যে দল ক্ষমতা চাইবে তাকে সমর্থন করার পূর্বে দেখা দরকার যে সে দলের নেতারা ইসলামের জ্ঞান রাখে কি- না ? তাদের সে ইলেম যদি বাস্তবিকই থেকে থাকে তবে সে জ্ঞান অনুযায়ী তারা আমল করছে কি-না ? তাদের কর্মী বাহিনীর মধ্যে ইসলামী জ্ঞান এবং চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে কিনা। ইসলামকে প্রচার এবং প্রসার করার যে মৌলিক দায়িত্ব তাদের উপরে রয়েছে তা তারা আমানতদারীতার সাথে পালন করছে কিনা। উল্লেখিত কার্যাবলী যদি তারা নিষ্ঠার সাথে করে থাকে কেবল তখনই সে দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় এমতাবস্থায় তাদেরকে সহযোগিতা করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়।
আদর্শের রাজনীতিঃ
দক্ষিন এশিয়ার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এদেশটি এমন একটা অবস্থানে আছে যার অস্তিত্ব নির্ভর করে সুস্থ রাজনীতির উপর। আর সুস্থ রাজনীতি আদর্শের উপরই নির্ভরশীল। কোন রাজনৈতিক দর্শন ব্যতীত রাজনীতি করা যেমন অসততা, তেমনি আসল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে কোন আদর্শের দোহাই দেয়া চরম ধোঁকাবাজি।
যিনি যে আদর্শই কায়েম করতে চান তা জনগনের নিকট পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। এখানে চোরাকারবারীর কোন অবকাশই থাকতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শ এবং দর্শনের প্রতি যাদের নিষ্ঠা আছে তাদের প্রতিপক্ষের অন্তরেও তাদের জন্য শ্রদ্ধাবোধ থাকে এবং আদর্শের লড়াই সত্ত্বেও দেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে। যদি প্রকৃতই আদর্শের রাজনীতি দেশে আন্তরিকতার সাথে চালু করা হয় তবেই জাতি এবং দেশ হিসেবে আমাদের টিকে থাকা সম্ভব।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
রাজনীতি এবং নৈতিকতাঃ
যারা রাজনীতি করে তারা যে দলেই থাকুন, অবশ্যই নিজেদের হাতে সরকারী ক্ষমতা চান। তারা দেশের সেবা যেভাবে করতে চান তা ক্ষমতা হাতে পেলেই সম্ভব হতে পারে। ক্ষমতা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী বাস্তবে রূপলাভ করতে পারে না। আবার নইতিকতা জাতির সেবার জন্য একটা অপরিহার্য গুন। নৈতিকতা ব্যতীত ক্ষমতার ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার সম্ভব নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার হলে জাতি সেবার পরিবর্তে জুলুমই ভোগ করে। পক্ষান্তরে ক্ষমতা না পেলেও নীতিবান রাজনীতিক দ্বারা দেশ এবং জাতির কিছু না কিছু খেদমত অবশ্যই হয়।
সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদের নৈতিক মানের উপরই দেশ এবং জাতির প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে। সমাজে নৈতিক অবনতি বাড়তে থাকলে নিঃসন্দেহে এজন্ন ক্ষমতাসীনদের দায়ী করা যায়। কারন ক্ষমতাসীনরা হচ্ছেন চলন্ত গাড়ির ড্রাইভারের মত—যার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং নৈতিকতার উপরে নির্ভর করে অসংখ্য যাত্রীর জীবন। দেশ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপরে থাকে তাদের নৈতিক মান, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পলিসি স্বাভাবিকভাবে সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জনগনের চিন্তা, ধ্যান-ধারনা, তাদের কর্মতৎপরতা এমনকি জাতির পোশাক- পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি- অবনতি, বহির্বিশ্বে তার সম্মান এবং মর্যাদা এসব কিছুই ক্ষমতাসীনদের নৈতিক মানের উপরে নির্ভর করে। এ কারনেই আরবীতে বলা হয়েছে—“আননাসু আলা দীনি মুলুকিহীম” অর্থাৎ জনগন শাসকদেরই জীবন ধারা অনুসরণ করে।
চরিত্রের গুরুত্বঃ
মানব জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব কোন কালেই অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। উন্নত চরিত্রের নেতৃত্ব ব্যতীত কোন দেশই সত্যিকার উন্নতি করতে পারে না। মানুষ বিবেকবান জীব হিসেবে ভালোমন্দের একটা সার্বজনীন ধারণা পোষণ করে। এরই নাম মনুষ্যত্ব। এটাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে। দেশ এবং সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী যারা তাদের চরিত্রের মান উন্নত না হলে জনগনের চারিত্রিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। কতক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করে তা স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে তারা চরিত্রবান না হলে রাষ্ট্রীয় উপায়- উপকরণের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ লোককে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পক্ষান্তরে উন্নত চরিত্রের লোকেরা ক্ষমতাসীন হলে সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে আদর্শ এবং চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।
তাই রাজনৈতিক ময়দানেই উন্নত চরিত্রের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। চরিত্রহীন লোক যদি রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে থাকে তবে জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। জাতীয় এ অবক্ষয়ের কারনেই দেশে খুন- খারাবী, হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি, ব্যাভিচার, ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ- বঞ্চনা নিত্য- নৈমিত্তিক হয়ে দাড়ায় এবং জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।
পলিটিক্স মানে ধোঁকাবাজিঃ
আমাদের দেশে এমন অনেক নীতিবিদ ও চরিত্রবান লোক রয়েছেন যারা রাজনীতি করাকে রুচিবিরুদ্ধ মনে করেন। কারন অধুনা রাজনৈতিক কার্যকলাপে চরিত্রের যে রূপ দেখা যাচ্ছে তা নীতিবান সম্পন্ন লোকের নিকট ঘৃণার বিষয় ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। রাজনীতিটা আমাদের দেশের চরিত্রবান লোকদের নিকট এতোটাই ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারনভাবে অনেক ভদ্রলোকই বলে থাকেন “আমি ভাই পলিটিক্স করি না”। আবার কেউ যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য গোপন করে কায়দা করে কথা ফাঁকি দিয়ে সরে যেতে চায় তাহলে বলা হয় “দেখুন আমার সাথে পলিটিক্স করবেন না”। এরদ্বারা পলিটিক্স করা মানে ধোঁকাবাজি করাকেই বুঝানো হয়।
নৈতিকতা বর্জিত রাজনীতির পরিনামঃ
১। যে নেতারা মুখে নীতি বাক্য আওড়ান আর বাস্তবে কর্মীদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ শেখান তারা পরবর্তী সময়ে কর্মীদের হাতেই অপদস্থ হন। কর্মীরা এধরণের দলে বিভেদ সৃষ্টি করে পাল্টা দল গঠন করে। এভাবেই এদেশে একটি দল স্বার্থের জন্য এবং নেতৃত্বের কোন্দলের জন্য বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একই নামে বহু দল এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।
২। নীতিহীন দল এবং নেতৃত্ব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এমন সব অবাস্তব ওয়াদা করে যা ক্ষমতায় গিয়ে তারা পূরণ করতে পারে না। ফলে জনগন হতাশ হয়। কর্মীরা নেতাদের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়। নেতাদের ছলে বলে কলে কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি দেখে জনগন ভাবতে শুরু করে যে, রাজনীতি করা মুনাফেকী এবং অসভ্য স্বভাবের কাজ। উন্নয়নশীল বিশ্বে এসব নীতিহীন দল এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে গনঅসন্তোষ গণবিক্ষোভে পরিনত হয়। দেশের অর্থনীতি পর্যন্ত রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়। ফলে সামরিক সাসন জারি হয় এবং দেশের সংকট জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে।
৩। অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ এবং স্বার্থপর লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা এলে তারা সরকারী কর্মচারীদের নির্লজ্জভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। সরকারী দলের পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগে কর্মচারীরা জনগণকে শোষণ করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। যে কোন অন্যায় করেও তারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে দুর্নীতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
৪। সরকারী দল নৈতিকতা বিবর্জিত হলে তারা ক্ষমতার প্রভাবে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায় করে। মোটা অংকের টাকা ছাড়া যেখানে মন্ত্রীরাও কাজ করতে চায় না সেখানে অফিসাররা আরো বেশী সুযোগ নেয়। এর ফলে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা যাবতীয় ঘুষের মোটা অংক কারখানা ও ব্যবসায়ের খরচে শামিল করে জিনিসের দাম বাড়ায়। তাই সরকার এ দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে কিছুই বলে না। নির্বাচনের সময় এজাতীয় রাজনীতিকরা যে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে তাও এপদ্ধতিতেই শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। আর ব্যবসায়ীরা শেষ পর্যন্ত তা দ্রব্যমূল্যের আকারে জনগনের ঘাড়ে চাপায়। এভাবেই জনজীবন হয়ে পড়ে কঠিন থেকে কঠিনতর।
৫। নীতিজ্ঞান বর্জিত রাজনীতির ফলে দুষ্ট লোকদের সকল প্রকার অপকর্ম বৃদ্ধি পায়। “দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন”- শাসকবর্গের কর্তব্য বলে চিরদিন স্বীকৃত হলেও চরিত্রহীন রাজনীতিকরা এর উল্টোটাই চালু করে থাকে। বিচারের বানী সেখানে নিরবে নিভৃতে কাঁদে। ফলে সমাজে “জোর যার মুল্লুক তার” নীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাজনৈতিক ডাকাতিঃ
যদি কেউ জাতির উন্নতির জন্য রাজনীতি করতে চান তাহলে তার হাতে অবশ্যই জাতীয় চরিত্রের মানোন্নয়নের কর্মসূচী থাকতে হবে। চরিত্রবান কর্মী বাহিনী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাড়া যারা রাজনীতি করেন, শুধু ডানপিটে কর্মীদল নিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখলের যারা চেষ্টা করেন, যুক্তির বদলে শক্তির ব্যবহারের দ্বারা যারা প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে চান তারা আর যাই হোক দেশ গঠনের জন্য কোন পরিকল্পনা হাতে রাখেন না। মনোবৃত্তির দিক দিয়ে তারা ডাকাত। সাধারন ডাকাত আইন এবং প্রশাসনের বাধা এবং জেল- গণপিটুনির ঝুঁকি নিয়ে ডাকাতি করে। কিন্তু যারা রাজনৈতিক ডাকাত তারা সরকারী ক্ষমতা হাতে নিয়ে গোটা দেশের উপর ডাকাতি করে। তাতে আইন এবং প্রশাসনকে ডাকাতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই এরা জাতীয় ডাকাত।
রাজনৈতিক ময়দানে নৈতিকতার প্রাধান্য না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসী সরকারের কাছ থেকে সত্যিকার খেদমত বা সেবা কিছুই পাবে না। জনগন যদি সত্যিই শান্তি পেতে চায় তাহলে চরিত্রহীন নেতা এবং রাজনৈতিক দলকে জাতীয় ডাকাত মনে করতে হবে। চরিত্রহীন লোকদের হাতে যারা নেতৃত্ব দিয়ে খেদমত পাওয়ার আশা করে তারা প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যাই করে। আল্লাহর কুরআন এবং রাসুলের হাদীসে এজন্যই সৎ, খোদাভীরু এবং চরিত্রবান লোকদের হাতে ক্ষমতা দেয়ার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
সুস্থ রাজনীতির ভিত্তি
একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার বিশ্বাস, রাজনীতিকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহন করেন, তাদের কোন স্থায়ী আসন জনগন এবং কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। যারা দেশ এবং জাতিকে খেদমত করাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন, এ ময়দান তাদেরই উপযোগী। পেশাদার রাজনীতিবিদরা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, তারা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম এবং ত্যাগের পথে এগিয়ে যেতে পারেন না। রাজনীতি যাদের নেশা তারাই সংগ্রামী হয়। তারা কোন মতবাদ বা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এর জন্য যে কোন কুরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এরাই দঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী এবং নেতা হয়।
তাই এ ময়দানে যারাই অবতীর্ণ হবেন তাদের পহেলা কর্তব্য হবে কোন আদর্শ ও মতবাদকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। নিজকে কায়েম করাই যাদের লক্ষ্য তাদের এ ময়দানে অবতীর্ণ না হওয়াই উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি দেশে কোন আদর্শ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যেখানে বিভিন্ন মতবাদ এবং আদর্শের লড়াই ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে এসেছে, সেখানে সুবিধাবাদী ধরণের কোন রাজনীতির স্থান নেই। কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পেশাদার রাজনীতিবিদের স্থায়ী আসন হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু এ দেশের পরিবেশে সাময়িকভাবে নেতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও কারো পক্ষে স্থায়ী নেতৃত্ব অর্জন করা অসম্ভব।
সুতরাং যারাই এদেশের সত্যিকার খেদমত করতে চান এবং যারা রাজনীতির কঠিন ও অনিশ্চিত ময়দানে মূল্যবান জীবন ও সময় নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল রাজনৈতিক মতাদর্শ।
সবদিক বিবেচনা করে যে আদর্শকেই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করুন, তার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। সুস্থ রাজনীতির এটাই প্রথম ভিত্তি।
আদর্শের বাছাই- প্রথম ভিত্তি
দেশে যারাই রাজনীতি করতে চান, তাদেরকে তিনটি বিকল্প আদর্শের মধ্যে একটিকে বাছাই করতে হবে। আদর্শ বাছাই করার মানদণ্ড নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু যে আদর্শই বাছাই করুন, ধীরভাবে বিবেচনা করে এবং দেশের সার্বিক কল্যাণকে সামনে রেখেই বাছাই করতে হবে। এ তিনটি আদর্শের মধ্যে প্রথমটি হলঃ
১। ইসলামঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পুরনের নিশ্চয়তা ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের নীতিসহ একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয়, যারা ইসলামের নৈতিক বিধানকে পালন করার মতো চারিত্রিক সবলতা অনুভব করেন না, তাদের পক্ষে ইসলামী আদর্শকে পছন্দ করা সত্ত্বেও এর জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।
এদেশের শতকরা আশি জন নাগরিকের ঐতিহ্য ও মানসিক প্রস্তুতি বিবেচনা করলে এবং সর্বোপরি মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে ইসলামী আদর্শকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।
২। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বা জনকল্যাণমুলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা
যে কোন কারনেই হোক যারা ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম কিন্তু জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞ তারা “গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক” রাষ্ট্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। জনগনের আস্থাভাজন সরকার কায়েম করে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে “বৃহত্তর সংখ্যক নাগরিক সর্বাধিক কল্যাণ সাধনকে” ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। দেশকে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে “গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র” একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্যই কোন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষে এটুকু আদর্শ মোটেই যথেষ্ট হতে পারে না। তবুও মন্দের ভালো হিসবে ইসলামের পর এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ।
৩। ইসলাম এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন হোক বা বর্তমান যুগের সমাজতন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের ফলেই হোক, যারা সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন তাদেরকেও এ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া প্রয়োজন। তারা যদি “ইসলামী সমাজতন্ত্র” বা “গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র” এর ন্যায় উদ্ভট নাম দিয়ে এদেশের মাটিতে দখলী সত্ত্ব কায়েম করতে চান, তাহলে মানুষের সামনে ধোঁকাবাজ হিসেবে পরিচিত হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। অবশ্য ধোঁকা দেয়া সমাজতন্ত্রী আদর্শে কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজ নয়। কিন্তু সমাজে ধোঁকাবাজ হিসেবে পরিচয় লাভ করাটা নিশ্চয়ই সে আদর্শের জন্যও লাভজনক নয়।
সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে যারা নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করবেন, তাদের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, এদেশে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সমাজতন্ত্রীরা চীনপন্থী কিংবা মস্কোপন্থী হতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী কিছু লোক থাকলেও বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে তাদের কোন সংগঠন এখনো দানা বাঁধতে পারেনি।
দ্বিতীয় ভিত্তিঃ
যারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে চান এবং আন্তরিকভাবে দেশের মঙ্গল কামনা করেন তাদের দ্বিতীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল- “রাজনৈতিক কর্মপন্থার ধরন”। জনগনের সমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারী ক্ষমতা দখল করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাহলে গণতন্ত্রের দোহাই না দিয়ে সরাসরি ফ্যাসিতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই রাজনীতি করা উচিত।
রাজনৈতিক কর্মপন্থার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা যদি যুক্তির বদলে শক্তি দিয়েই করার প্রচেস্তা চলে, তাহলে কোনদিনই জনগনের সরকার কায়েম হওয়ার কথা নয়। শক্তি প্রয়োগের নীতি চালু হলে যারা গুণ্ডামির প্রতিযোগিতায় যারা শ্রেষ্ঠ বলে প্রমানিত তারাই রাষ্ট্র পরিচালক হবে। এরপর রাজনৈতিক ময়দান গুণ্ডাদের আখড়ায় পরিনত হবে। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যেখানেই শক্তিবলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেখানেই যুক্তির অপমৃত্যু ঘটেছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এবং ক্ষমতাসীনদের দুষ্কৃতির সমালোচনার পথ বন্ধ হয়েছে। মানব সমাজের জন্য এর চেয়ে জঘন্যতম পরিস্থিতি কল্পনাও করা যায় না। তাই মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রয়োজনে শক্তিবলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রীতি অবশ্যই বর্জনীয়।
তাই এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে আন্তরিকতার সাথে আমাদের সবাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং যুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করার স্বাভাবিক রীতিই দেশে চালু করবো এবং একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থায়ই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবো। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি দেশে চালু থাকলে ক্ষমতাসীন না হয়েও সরকারকে বহু জনকল্যাণমূলক কাজে বাধ্য করা যায়। শক্তির পরিবর্তে যুক্তি প্রতিযোগিতা মানবতার দিক দিয়ে সমাজকে ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে দেয়। এ পরিবেশে সব দল এবং নেতাই জনগনের মনে উন্নতম আদর্শ ও কর্মসূচী পেশ করার প্রতিযোগিতায় লেগে যায়। একবার যারা ক্ষমতাসীন হয়, তাদেরকে কয়েকবছর আবার নির্বাচনে সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে জনকল্যাণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। বিরোধীদল তার চেয়েও অধিক কল্যাণব্রতী কর্মসূচী পেশ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সমাজ মঙ্গল এবং কল্যাণকর নীতির দিকে এগিয়ে চলে।
বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই এরূপ কল্যাণকর নীতি চালু করার চেষ্টা করেনি। বরং অধিকাংশই এর বিপরীত পন্থায়ই কাজ করেছেন। এর ফলে বিরোধী মহলেও শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চালু হয়েছে। এ জঘন্য পদ্ধতির প্রবর্তনের স্বাভাবিক পরিনাম এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এক নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দলগুলির মধ্যেই কোন কোন দল অপর গনতন্ত্রকামী দলের উপর বিভিন্নভাবে বল প্রয়োগ করে এবং যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে শক্তি দ্বারা ফায়সালা করার চেষ্টা করে। এমনকি কোন কোন নেতা অন্যান্য দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনতাকে শুধু এজন্য ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন যে, তারা উক্ত নেতার অযৌক্তিক মত গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরই ফলে কারো কারো উপরে দৈহিক আক্রমণও হয়েছে। যারা সরকারী ক্ষমতায় পৌছুবার পূর্বেই এমনি শক্তির দাপট দেখাবার চেষ্টা করেন তারা ক্ষমতাসীন হলে আরও যে কি কি করতে পারেন, তা ধারণা করা মোটেও কঠিন নয়।
এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্রী মহলের উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক। কারন বলপ্রয়োগ দ্বারা ক্ষমতা দখল করাই তাদের একমাত্র নীতি। এ কারনে “জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো” “সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম” “ধরো মারো দখল করো” ইত্যাদি মন্ত্র তাদের পক্ষেই শোভন। কাজেই যারা গণতন্ত্রের দোহাই দেয় তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমাজতন্ত্রের কর্মপন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। একমাত্র গণতান্ত্রিক কর্মনীতির মাধ্যমেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মনীতি বাছাই করার সাথে সাথে আমাদেরকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দেশের জন্য অকল্যাণকর মতবাদ ও অগণতান্ত্রিক কর্মপন্থার মোকাবেলা করার জন্য গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসীদেরকেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনার পক্ষে কারো সভা পণ্ড করতে চেষ্টা করা নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু আপনার সভায় যারা গুণ্ডামি করতে আসবে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। শক্তির বলে আপনার মতামত যেমনি অন্যের উপর চাপানো অন্যায়, আপনার উপর অপরের মতামতকে চাপাবার হীন প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেয়াও তেমনি দোষের। যে সত্য মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে না সে সত্য সত্যের মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সঠিক আদর্শ এবং কর্মনীতি গ্রহণ করার পর মযবুত সংগঠন অপরিহার্য। সৎপন্থীরা আজ সুসংগঠিত নয় বলেই অন্যায়ের দাপট এতো প্রবল। অভদ্রতাকে প্রশ্রয় দেয়া কোন দিকে দিয়েই ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। মযবুত সংগঠনের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যতীত সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি অসম্ভব।
ইসলামী দলের কর্মপন্থা
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করার ব্যাপারে ইসলামী দলের পক্ষে ইসলাম বিরোধীদের মত নীতিহীন এবং মানবতাবিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তারা যখন ইসলামী দলের সভা- সমাবেশ কিংবা মিছিলে হামলা করে তখন প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলাকারীদের সাথে প্রয়োজনীয় মেহমানদারী করতে বাধ্য হয়।
কিন্তু তারা যে সন্ত্রাসী কায়দায় চোরাগুপ্তা হামলা করে এবং রিক্সা বা বাস থেকে নামিয়ে, রেলস্টেশনে একা পেয়ে, অফিসে, বাড়িতে, হোস্টেলে ও হলের কামরায় নিরস্ত্র লোকদের উপর কাপুরুষের মত অতর্কিত হামলা চালায় এর প্রতিরোধ ইসলামী দলের জন্য বড়ই কঠিন। কারন এমন অমানবিক পন্থা কোন মুসলিমের পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তাদের এ জাতীয় পাষণ্ড সুলভ তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে সমাজে এদেরকে অপাংক্তেয় করে দিতে হবে এবং ইসলামী দলকে গনসংগঠনে পরিনত করতে হবে যাতে সন্ত্রাসীরা অপকর্ম করে পালাবার সুযোগ না পায়। ( বাংলাদেশের রাজনীতি )
রাজনীতি এবং সমাজ সেবা
রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই সমাজ সেবা। সমাজকে সেবা করার মহান ব্রত নিয়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ করা উচিৎ। প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রিক দেশে সর্বসাধারণের খেদমত ব্যতীত রাজনীতি চর্চার অপর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলন বাহ্যত ক্ষমতা দখলেরই প্রচেষ্টা, কিন্তু ক্ষমতা অর্জনই এর চরম লক্ষ্য নয়। দেশের জনগনের খেদমত করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। কিন্তু যে রাজনীতির পরম কাম্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করা, তা দ্বারা স্বার্থপর রাজনীতিকদের কিছু খেদমত হলেও জনসেবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই।
আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে রাজনীতিকের অভাব নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনের দাপটে সাধারন মানুষের জীবন অস্থির। ক্ষমতার রদবদলও কম হয়নি। অথচ জনসেবা যে কতটুকু হয়েছে তা আর বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের রাজনীতিকগন সাধারনত ব্যক্তি, স্বজন ও দলকেই জনগনের স্থলাভিষিক্ত মনে করে জনসেবার কর্তব্য পালন করে। ফলে সমাধানের পরিবর্তে দেশের সমস্যা আরও জতিলতর হয়েছে এবং এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যা কিছুদিন পূর্বে ধারনারও অতীত বলে মনে হতো।
রাজনৈতিক আন্দোলন যেভাবে জনসেবার পরিবর্তে পাইকারী জুলুম এবং সুপরিকল্পিত অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিনত হয়েছে তাতে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী ও চিন্তাশীল সমাজকর্মীদের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিছু সংখ্যক নিঃস্বার্থ কর্মীদল ব্যতীত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনই সফল হতে পারে না। সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করেও জনসেবার পরিবর্তে গন জুলুম করেছে সেসব দলও নিঃস্বার্থ কিছু কর্মী ব্যতীত ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এসব নিঃস্বার্থ কর্মীদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, তাদের অক্লান্ত শ্রম এবং ত্যাগের ফলে যারা জনসেবার ওয়াদা করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেছেন, তারা কেন এরূপ স্বার্থপরতা ও স্বজন প্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে চরম বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় প্রদান করেন। ত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ কর্মীদের মধ্যে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে।
একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এ লজ্জাকর পরিনাম এক স্বাভাবিক প্রতিফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে নিরাশ হবারও যেমন কোন কারন নেই, এ পরিনাম রোধ করার পন্থা আবিস্কার করাও তেমনি অসাধ্য নয়। আসল ব্যাপার হল এই যে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় থেকেই আমাদের রাজনীতি হুজুগ প্রধান হয়ে পড়ে। সকল দিক থেকেই কেবল ভাংগ ভাংগ রব উঠতে থাকে। কিন্তু ভেংগে গড়ার কোন সুস্থ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করায় আমরা এখনো অভ্যস্ত হইনি। বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতিবাচক কর্মপন্থাই এর জন্য প্রথমত দায়ী।
গদী দখল করলে সেবা করবো বলে যেসব রাজনৈতিক দল ওয়াদা করে, তারা নিঃস্বার্থ কর্মীদেরকেও ধোঁকা দেয়, জনগণকেও বেওয়াকুফ বানায়। জনগনের খেদমত করাই যে রাজনীতির উদ্দেশ্য তার কর্মসূচীতে জনসভা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করা উচিত। কারন অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন কাজই মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আর নিঃস্বার্থ জনসেবার ন্যায় কঠিন দায়িত্ব বিনা অভিজ্ঞতায় পালন করার চিন্তা করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। “সাতদিনের মধ্যেই ডাল- ভাতের ব্যবস্থা” করার ওয়াদা এবং “পনের দিনের মধ্যেই খাদ্য সমস্যার সমাধান” করার আশ্বাস যারা দেন তাদের ধূর্ততা, অসাধুতা এবং ভণ্ডামি যেমন ক্ষমার অযোগ্য তাদের কথায় যারা বিশ্বাস করেন তারাও তেমনি খেদমত পাওয়ার অনুপযুক্ত।
প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের কর্মসূচী থেকেই রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। যদি সত্যই কোন দল জাতির, দেশের এবং মানুষের খেদমত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ রাখে তাহলে কর্মী সংগ্রহ এবং নেতৃত্ব গঠনের পর্যায়েই এর সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। যে দল কর্মীদের দেশের খাদেম হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেনি সে দল ক্ষমতা দখল করলে নিজেদের সেবা ব্যতীত আর সকলের উপরই জুলুম করবে।
কর্মীদের জন্য জনসেবামূলক কর্মসূচী থাকলে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে যে অভিজ্ঞতা লাভ হবে, ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৃহৎ আকারে ঐ অভিজ্ঞতা বাস্তবে কাজে লাগবে। যে দল রাজনৈতিক কর্মী বাহিনীকে জনগনের সেবক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে সে দল ক্ষমতায় গেলে তাদের কাছে থেকে জনগন সত্যিকার সেবাই পাবে।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
চরিত্রবান লোকদের শাসন
দেশের শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা চরিত্রবান না হলে জনগনের চরিত্রের উন্নতি অসম্ভব। ক্ষমতাসীনরা যে মানের চরিত্রের অধিকারী হয় সে মানেই দেশ পরিচালিত হয়।
তাই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের আন্দোলন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংগঠনে যদি চরিত্র সৃষ্টির কর্মসূচী থাকে তবেই কেবল চরিত্রবান লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা আনবার সম্ভাবনা থাকে।
এদেশে অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিলেন এবং এখনো যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের চরিত্রের মান জনগনের নিকট উন্নত বলে কতটুকু স্বীকৃত তা যে কোন সাধারন লোকের মতামত নিলেই সহজে বুঝা যায়।
আমরা যদি দুনিয়ায় উন্নত জাতি হিসেবে দাড়াতে চাই তাহলে যেসব রাজনৈতিক দলে ব্যক্তি চরিত্র উন্নত করার কর্মসূচী রয়েছে তাদের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করতে হবে। যে কোন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে যারা রাজনৈতিক দল গঠন করেন তাদের হাতে চরিত্র বিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং চরিত্রের অভাব দূর করতে হলে চরিত্রবান নেতৃত্ব এবং কর্মী বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।
( আমার দেশ বাংলাদেশ )
গণতন্ত্র ও ইসলাম
বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি
রাসুলুল্লাহর ( সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ) জীবনে রাজনীতির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা আজ নানা কারনে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পরিনামে ধার্মিকদের মধ্যেও আজ এমন লোক সৃষ্টি হয়েছে যারা দ্বীনদার এবং পরহেজগার বলে সমাজে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও “রাজনীতি” করাকে নিন্দনীয় মনে করেন, অথবা অন্তত পক্ষে অপছন্দ করেন। তারা দেশের রাজনীতি থেকে পরহেজ করাকে ( নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাকে ) দ্বীনদারি এবং তাকওয়ার জন্য জরুরী মনে করেন। আবার আর এক শ্রেনীর লোক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, মতবাদ এবং জীবন দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে ইসলামকেও খ্রিস্ট ধর্মের ন্যায় এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব পুজা পার্বণ বিশিষ্ট ধর্মমত বলে মনে করেন। তাদের ঈমান মতে ধর্ম এবং রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকদের আড়াই শত বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ইউরোপের পদানত থাকা অবস্থায় প্রায় সকল মুসলিম দেশেই সে মতাদর্শ প্রতিস্থিত হয়।
ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা অবস্থায় যেসব মুসলিম পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং জীবন দর্শনের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন প্রধানত তারাই আজ স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর পরিচালক। ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে কয়টি ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এর প্রত্যেকটিই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসক গোষ্ঠীর গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামকে খ্রিস্ট ধর্মের মতই শুধু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে পালন যোগ্য একটি ধর্মে পরিনত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্রটিকে ধর্মের আওতা থেকে পৃথক করার পরিকল্পনা এঁটেছেন।
এভাবে কতক ধার্মিক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের দিকে লক্ষ্য না করে তাকে এমন ভাবে চিত্রিত করেন যেন আল্লাহর নবী কোন সংসারত্যাগী কোন বৈরাগী ছিলেন ( নাওউজুবিল্লাহ )। ওদিকে মুসলিম নামধারী শাসকেরাও রাসুলকে ( সাঃ ) শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবেই স্বীকার ( গ্রহণ নয় ) করতে প্রস্তুত। মহানবীর সামগ্রিক জীবনকে একক এবং পূর্ণাংগ সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ না করার মনোভাবটি উদ্দেশ্য মূলক হলেও কিছু সরল মুসলমান এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।
বিশেষ করে ধর্মীয় এবং সমাজসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠান রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ইসলামের নামে আন্তরিকতার সাথে খেদমত করেছেন বলে উপরোক্ত স্বার্থপর লোকেরা ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি না করার পক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নজীর পেশ করেন। তাদের মতে দুনিয়ার সব মত এবং পথ নিয়ে রাজনীতি করা যায়েয হলেও ইসলামী আদর্শকে নিয়ে রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অন্যায়। এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে “বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি” ছিল কি-না এবং ইসলামে রাজনীতি জরুরী কি- না তা আলোচনা করা প্রয়োজন।
রাজনৈতিক কার্যকলাপ
সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদেরকে সংশোধন করা, তাদের কার্যাবলীর সমালোচনা করা, সরকারী নীতির ভ্রান্তি প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করা এবং এ জাতীয় যাবতীয় কাজকেই রাজনৈতিক কার্যাবলী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই হল সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ, ভ্রান্ত নীতি এবং আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে দেখলে সরকারী কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করে সঠিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টাই প্রধান রাজনৈতিক কার্যকলাপ।
বিশ্ব নবীর দায়িত্ব
এখন দেখা যাক, আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বিরাট কাজ কররা দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তা পালন করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হয়েছিল কি- না। যদি তিনি নবী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়েছিলেন বলে জানা যায় তাহলে রাজনীতি করা ইসলামের তাগিদ বলেই মনে করতে হবে। নবী বলে ঘোষিত হবার পর থেকে যদি তার গোটা জীবনই আমাদের জীবনে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয় তা হলে তার রাজনৈতিক কাজগুলো অনুসরণ করতে কি বাধা থাকতে পারে ? হযরতের উপরে কি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি কিভাবে তা পালন করেছিলেন তা আলোচনা করলেই বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি কতটা ছিল সে কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে।
আল্লাহ পাক তার রাসুলকে কোন কর্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, কুরআন মাযীদের বহুস্থানে বিভিন্নভাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ
আয়াত***
“তিনিই ঐ সত্ত্বা যিনি তার রাসুলকে হেদায়াত এবং দ্বীনে হক সহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দ্বীনের উপর একে ( দ্বীনে হক ) বিজয়ী করে তুলতে পারেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।”
এ আয়াতের শেষাংশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তার রাসুলকে প্রধানত কোন কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশী কারো পক্ষে জানবার উপায় নেই। সুতরাং সে বিষয়ে অন্য কারো সাক্ষ্যই গ্রাহ্য নয় – আল্লাহর সাক্ষ্যই সেখানে যথেষ্ট।
রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) এর জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে কোন একটা দিক বা বিভাগকে নিজেদের রুচীমত প্রধান দিক বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। সাত অন্ধের হাতী দেখার ন্যায় কেউ তার বিশাল জীবনের একাংশ থেকে শুধু হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন দিকটিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ তার নামায- রোযা, তাসবীহ- তেলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদের দিকটাই প্রধান বলে গ্রহন করেছেন। কেউ তাকে একজন আরব জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবেই দেখেছেন। আর কেউবা শুধু সর্বহারাদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করে নিজ নিজ মত এবং পথের সমর্থনে রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) কে দলীল হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।
এ জাতীয় সবাই রাসুলের গোটা জীবনকে একসাথে বিবেচনা করে রাসুলের জীবনের মূল লক্ষ্যটুকু বুঝতে সক্ষম হননি। তারা অন্ধের মতই হাতিয়ে যেটুকু দেখতে পেয়েছেন সেটুকুই রাসুলের গোটা জীবন বলে ধারণা করেছেন। এদের অনেকেই হয়তো সাত অন্ধের ন্যায় আন্তরিকরার সাথেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন তার সাথে এদের ধারণার কোন মিল নেই।
হেরাগুহায় হযরতের ধ্যানমগ্ন থাকা, নামায- রোযায় মশগুল হওয়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হওয়া এবং সর্বহারাদের দুর্গতি দূর করার চেষ্টা চালান – এসবই তার জীবনে লক্ষ্য করা যায় সত্য। এগুলো তার কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনা হলেও এর কোনটিই বিচ্ছিন্ন নয়। এসবই হযরতের মূল দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার মূল লক্ষ্যে পৌছার উপযোগী। কিন্তু ঐ সব কাজের কোনটাই রাসুলকে পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য নয়।
রাসুলের প্রধান দায়িত্ব
পূর্বোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তার রাসুলকে পাঠাবার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটাই নবী জীবনের প্রধান দায়িত্ব। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসুলকে একমাত্র দীনে হক দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং মানব রচিত যাবতীয় দীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, রাসুলকে কেবলমাত্র একজন প্রচারক বা ধর্ম নেতার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। দীন ইসলাম রূপ পূর্ণাংগ জীবন বিধানটিকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হযরতের প্রধান দায়িত্ব ছিল। দীন ইসলামকে মানব সমাজে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই নবী জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন করেছেন একমাত্র সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যই করেছেন এবং সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যেই একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।
রাসুলের বিপ্লবী আন্দোলন
মানব সমাজে কোন না কোন ব্যবস্থা কায়েমে থাকেই। সামাজিক রীতি- নীতি, আইন, শাসন, বিচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত থাকে। যে সমাজ ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে তা যেমন আপনীই কায়েম থাকে না তেমনি তা আপনা আপনিই উৎখাত হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং ধর্মীয় নেতৃত্বই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখে। যখন কেউ এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আওয়াজ তুলে তখনই সর্ব শ্রেনীর নেতৃত্ব একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করে। কারন এসব নেতৃত্বের স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম থাকার মধ্যেই সম্ভব। এগুলোই প্রচলিত সমাজের কায়েমী স্বার্থ ( Vested Interest )। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যখনই কোন প্রচেষ্টা চলে তখনই কায়েমী নেতৃত্বের সাথে সংঘর্ষ বাধে। ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতি- নীতি, আইন ও শাসন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো মিলে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নতুন রূপে নতুন ধরনের নীতি এবং আদর্শে সমাজকে গঠন করার আওয়াজ উঠবার সংগে সংগেই কায়েমী নেতৃত্ব চঞ্চল হয়ে উঠে এবং এ আওয়াজকে বন্ধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। সমাজে এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করাকে বিপ্লব বলে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত উত্থান পতন বা দল বিশেষের নাটকীয় ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব নাম দিলেও তাকে প্রকৃত বিপ্লব বলা চলে না। গোটা সমাজে মৌলিক এবং ব্যাপক পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলে। এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যে আন্দোলনের প্রয়োজন তারই নাম বিপ্লবী আন্দোলন।
রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) আরব ভূমিতে যে ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা হঠাৎ সংঘটিত হয়নি। আরবের প্রচলিত সমাজকে সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেয়ার জন্য রাসুলকে কালেমা তাইয়েবার ভিত্তিতে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করতে হয় এবং দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম চেষ্টায় সে আন্দোলন সফল হয়।
দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ কোন নযীর পাওয়া যায় না যে, কায়েমী নেতৃত্ব কোন বিপ্লবী আওয়াজ শুনেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়বার জন্য খুশী হয়ে নেতৃত্বের আসন ত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে। বরং সব সমাজেই সর্বকালেই দেখা গেছে যে, কায়েমী নেতৃত্বের অধিকারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে তাদেরকে উৎখাত করেছে।
রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবার যে দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল, তা পালন করার প্রথম পদক্ষেপেই মক্কার নেতৃত্ব অস্থির হয়ে উঠলো। পহেলা পহেলা লোভ দেখিয়ে তাকে এ পথ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করলো। কালেমা তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াত থেকেই সমাজের কায়েমী স্বার্থের অধিকারীরা বুঝতে পারলো যে, এ আওয়াজ তাদের বিরুদ্ধেই স্পষ্ট বিদ্রোহ। নেতৃত্বের লোভ, অরথ- সম্পদ, নারীর লালসা ইত্যাদির ( যা তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ) বিনিময়ে তারা হযরতকে এ পথ থেকে ফিরাতে চেষ্টা করলো। হযরত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলে তাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেও মেনে নিতে বাধ্য হতেন।
কিন্তু আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যারা করেন তাদের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবে রাজী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই এ ধরনের আন্দোলনের সাথে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য। দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামের পর নবী করিম ( সাঃ ) বিজয়ী হন এবং ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন।
ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতি
অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী ( সাঃ ) যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাই হচ্ছে আদর্শ ইসলামী আন্দোলন। এ ধরনের আন্দোলন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যতীত কি করে সম্ভব হতে পারে ? সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং আধুনিক আদর্শবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যারা কিছুটা চর্চা করেন এবং মানব সমাজের সমস্যা নিয়ে যারা একটু চিন্তা- ভাবনা করেন তাদের পক্ষে একথা বুঝা অত্যন্ত সহজ। যারা স্থূল দৃষ্টিতে ইসলামকে দেখেন তারা এটাকে একটা ধর্ম মাত্র মনে করে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে আলাদা করতে চান। তারা হয় আন্দোলনের অর্থই বুঝেন না, আর না হয় আন্দোলনের সংগ্রামী পথে চলার সাহস রাখেন না। ইসলামকে একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে বুঝেও যারা রাজনীতি করা পছন্দ করেন না, তারা নিশ্চয়ই পার্থিব কোন স্বার্থের খাতিরে অথবা কায়েমী নেতৃত্বের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ নিষ্ক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন।
নবী করিম ( সাঃ ) যে আন্দোলন চালিয়েছেন তাতে প্রকৃতপক্ষে চরম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। দেশের নেতৃত্ব যদি অনৈসলামী লোকদের হাতে থাকে তাহলে ইসলাম কিছুতেই একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের চেষ্টাই চরম রাজনীতি। রাজনীতি করাকে যারা দীনদারীর খেলাফ মনে করেন তারা রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) এর চরম রাজনীতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ? যারা এ নীতি অবলম্বন করেন তারা কি নিজেদেরকে রাসুল ( সাঃ ) এর চেয়েও বেশী দীনদার বলে মনে করেন ? তা নিশ্চয়ই তারা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা রাজনীতির অর্থই বুঝেন না এবং দীনের দাবী সম্পর্কেও পূর্ণ চেতনা রাখেন না।
রাসুলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য
আজকাল রাজনীতি করাকে নেক লোকেরা যে কারনে ঘৃণা করেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অনুকূলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে রাজনীতির প্রচলন হয়েছে তা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই পছন্দ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের জঘন্য কোন্দলই এক শ্রেনীর লোকের নিকট রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ টাকার জোরে, কেউ ভোটের বলে, আর কেউ অস্ত্রের দাপটে ক্ষমতা দখল করতে সর্বপ্রকার অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করে থাকেন। এসব লোকেরা জঘন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গদী দখল করার পর তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকারটুকুও হরণ করেন। নীতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠনের প্রচেষ্টাকেও এরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে দমন করতে চান।
শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলনকেও এ মনোভাব দিয়ে দমন করার চেষ্টা চলেছিল। শুধু শেষ নবীই নয়, হযরত ইব্রাহীম ( আঃ ), হযরত মুসা ( আঃ ), এবং অন্যান্য নবীর আন্দোলনের সাথেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা নবীদের আন্দোলনের পরিনতি যে নেতৃত্বের পরিবর্তন সে কথা বুঝতে ক্ষমতাসীনদের আর বাকী ছিল না। কিন্তু নবীদের রাজনৈতিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- তাদের চারিত্রিক এবং নৈতিক শক্তি। বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পূর্বে নবীদের নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘ জীবন যে নিঃস্বার্থতার পরিচয় বহন করে তা ইসলাম ব্যতীত আর কোন আদর্শবাদী আন্দোলনে সমপরিমানে পাওয়া যায় না। সমাজে এ নৈতিক প্রতিষ্ঠাই তাদের আন্দোলনের প্রধান মূলধন। শেষ নবীর রাজনীতিতে এ নিঃস্বার্থতা এবং নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল ছিল। এ জন্যই তার বিরুদ্ধে কোন সস্তা স্লোগান কার্যকরী হয়নি। তার নিঃস্বার্থ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।
হযরতের রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল উপায় উপকরণের পবিত্রতা। তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেন নি। তার রাজনৈতিক দুশমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে রাযী হতো তা হলে তিনি পূর্বের সব দোষ মাফ করে দিতেন।
তার রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল- উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তার কাম্য ছিল। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা যদি তার উদ্দেশ্য হত তাহলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাদশাহ হতে পারতেন।
চারিত্রিক পবিত্রতা, উপায় এবং পন্থার পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যর পবিত্রতা --- এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রাসুলের রাজনীতিকে স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদি কেউ ইসলামী রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাকে মহানবীর এই তিনটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। যাদের চরিত্র, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য অপবিত্র বলে বুঝা যায় তারাও যদি ইসলামের নামে রাজনীতি করে তাহলে ইসলামের উপকারের চাইতে অপকারই বেশী হয়। এদের রাজনীতি অন্যান্য স্বার্থবাদী রাজনীতির চেয়েও জঘন্য।
কায়েমী নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাসুলের কর্মপন্থা
কোন নবীই প্রচলিত নেতা বা শাসকদের নিকট নেতৃত্বের গদী দাবী করেননি। হযরত ইব্রাহীম ( আঃ ) নমরুদের নিকট, হযরত মুসা ( আঃ ) ফিরাউনের নিকট এবং শেষ নবী মক্কায় অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকগণের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পেশ করেছেন, তাদেরকে গদী পরিত্যাগ করার আহবান জানাননি। তবুও প্রত্যেক রাসুলের সংগেই কায়েমী নেতৃবৃন্দের সংঘর্ষ বেধেছে। সমাজের সর্ব শ্রেনীর শোষকই রাসুলগনকে সকল দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামের আহবান জানানোর পর সকল কায়েমী স্বার্থই যুক্তফ্রন্ট করে তাদের বিরোধিতা করেছে।
প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ কোনকালেই ইসলামের আহবান গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। কেননা, তাদের পার্থিব যাবতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। তবু নবীগন ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম তাদের নিকটেই পেশ করেছেন। পবিত্র কুআনের সুরা আরাফের অষ্টম রুকুতে আল্লাহ পাক নূহ ( আঃ ), হুদ ( আঃ ), সালেহ ( আঃ ), লুত ( আঃ ), শোয়াইব (আঃ ) ও মুসা ( আঃ ) এর ইসলামী আন্দোলনগুলোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাসুলই সমাজের নেতৃস্থানীয়দের কাছে দাওয়াত পেশ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। সেখানে একথাও প্রমানিত হয়েছে যে, সমাজপতিগণ প্রত্যেক রাসুলেরই বিরোধিতা করেছে।
নেতৃবৃন্দের নিকট প্রথম দাওয়াত পেশ করার কারন
নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগত কোন আদর্শকে গ্রহণ না করলেও তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কোন আদর্শের বিপরীত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সমাজে সে আদর্শ কায়েম হবে। তাই নবী করিম ( সাঃ ) পহেলা নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন। নেতাগন এ দাওয়াত কবুল না করলেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাবার ফলে সমাজের অনেক লোকের নিকটই ইসলামের আওয়াজ পৌছবার সুযোগ হল।
ইসলামী আদর্শের উপযুক্ত নেতৃত্ব ব্যতীত দীন ইসলামকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইসলামকে কবুল করতে রাজী নয়। এ অবস্থায় যেসব লোক ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে রাজী হলেন তাদেরকে নিয়েই আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ব্যতীত রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) এর নিকট আর কোন পথই রইলো না।
প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদী নেতৃত্ব কোন কালেই তৈয়ার ( Readymade ) পাওয়া যায় না। আদর্শের আন্দোলনই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজে যখন আদর্শবাদী নেতৃত্ব কায়েম হয় তখনই আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। নেতৃত্বের এ পরিবর্তন হযরতের আন্দোলনের মাদানী স্তরে গিয়ে সম্ভব হল। অতঃপর আট বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর আরবের বুকে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ্ব নবীর এ কার্যক্রম যে সুস্থ রাজনীতির সন্ধান দেয় তা প্রত্যেক আদর্শবাদী বিপ্লবী প্রানকেই সংগ্রামমুখর করে তোলে। মহানবীর বিপ্লবী জীবনকে অধ্যয়ন করার পর কারো মনে এ ধারণা হওয়া সম্ভব নয় যে, তিনি রাজনীতি করেননি।
শেষ কথা
বিশ্ব নবীর দায়িত্ব পালন করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে অপরিহার্য ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রমানিত। রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌছতে পারলে তিনি ইসলামকে বিজয়ী দীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমই হতে না। আজ যদি কেউ দীন ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার আর কোন বিজ্ঞান সম্মত পন্থা নেই।
কিন্তু স্বার্থপর, পদলোভী ও দুনিয়া পূজারিদের রাজনীতি ইসলামের জন্য কোন দিকে দিয়েই সাহায্যকারী নয়। ইসলামের নামে যারা এককালে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা রাজনীতি ক্ষেতেরে নবীর নীতি এবং কার্যক্রম অনুসরণ করেননি বলেই পাকিস্তানে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।
স্বার্থপর এবং গদী ভিত্তিক রাজনীতি যেমন ইসলাম বিরোধী, নবীর অবলম্বিত রাজনীতি থেকে পরান্মুখ হওয়াও তেমনি অনৈসলামী। বরং রাসুলগন যে ধরণের রাজনীতি করেছেন সে ধরণের রাজনীতি করা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য ফরয। এ ফরযটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতিই এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সুতরাং কতক লোক পরহেজগারের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করা অপছন্দ করলেও রাসুলের খাটি অনুসারীদের পক্ষে তা পছন্দ না করে কোন উপায়ই নেই।
দীনদার লোকেরা যদি রাজনৈতিক ময়দানে কাঝ না করেন তাহলে তাদের এ আচরণ এ কথাই প্রমান করে যে, তারা ধার্মিক হওয়ার কারনে রাজনীতি করা পছন্দ করেন না। এ মনোভাব যারা পোষণ করেন তাদেরকে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধার্মিক লোক বলা যায়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যেমন ইসলাম নয়, তেমন রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও ইসলাম নয়। রাসুল ( সাঃ ) এর জীবনাদর্শ এ দুটিরই বিরোধী।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
গণতন্ত্র ও ইসলাম
গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। জনগনের অবাধ ভোটাধিকারের প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকে গণতন্ত্র বলা হয়। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগনের সমর্থন থাকুক এটা সব সরকারেরই ঐকান্তিক কামনা। তাই সামরিক স্বৈরাচাররাও জনগনের দ্বারা নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এমনকি যে সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেতের গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতির প্রবর্তক তারাও গণতন্ত্রের দোহাই দিতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শের জনপ্রিয়তা এবং সার্বজনীনতাই এর প্রধান কারন। অবশ্য সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্র থেকে নিজেদের মতাদর্শকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে “জনগনতন্ত্র” নামে অদ্ভুত এক পরিভাষাও ব্যবহার করে। অথচ “জন” এবং “গন” একই অর্থের দুটি শব্দ।
গণতন্ত্রের মূলনীতি
গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে পাঁচটি। যেমনঃ
১। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা নেয়ার অধিকার রয়েছে।
২। এ নিরবাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাসের সাথে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধীদলও এমন সরকারের বৈধতা এবং নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।
৩। সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করার জন্য জনগনের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন এবং শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।
৪। জনগনের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।
৫। সরকার গঠন, পরিবর্তন এবং পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্র বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন এবং পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।
ইসলামের গণতন্ত্র
ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরোক্ত পাঁচটি মুলনীতির কোন বিরোধ নেই। জনগনের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। রাসুল ( সাঃ ) এর পড়ে যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিখ্যাত তারা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি। জনগনের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কারণে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই ধরণের ছিল না কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তারা কেউ এ পদের জন্য চেষ্টা করেননি। আল্লাহর রাসুলের (সাঃ ) এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের পদের আকাংখী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে।
এ কারনেই হযরত আলী ( রাঃ ) এর পর হযরত মুয়াবিয়া ( রাঃ ) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত নন। কারন তিনি নিজে চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয ( রঃ ) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারন এটাই যে, রাজ বংশের রীতি অনুযায়ী তার পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগন তারই উপর আস্থা জ্ঞাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহনে বাধ্য হন।
ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব থেকে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতির চেয়েও কতো উন্নততর।
ইসলামে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগনের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির লুকমা দেয়া ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলেন রাসুলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রাসুলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধন করার দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি রাসুল ( সাঃ ) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগনের কর্তব্য।
এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামে শুধু মিল নয়, ইসলামের নীতি- রীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অধিক আধুনিক এবং উন্নততর – ত্রুটিমুক্ত।
ইসলাম এবং গণতন্ত্রের পার্থক্য
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর আর গণতন্ত্রে জনগনই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌমশক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। গণতন্ত্রে জনগন বা তাদের নির্বাচিত আইন সভাই সকল ক্ষেত্রে আইন দাতা। আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ইসলামে আল্লাহর দেয়া আইন এবং বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগনের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম এবং গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো ও মন্দ, ন্যায়- অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, হালাল ও হারাম ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সীমা ঠিক করে দেয়া প্রয়োজন। মানুষ যে কোন ক্রমেই নৈতিকতা এবং ইনসাফের সামান্যতমও মানও বজায় রাখতে পারে না তা দুনিয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত।
প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্ভুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরি আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এদিক বিবেচনা করলে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থকস্বরূপ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাময়।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
বাংলাদেশের উপযোগী সরকার পদ্ধতি
সরকার পদ্ধতি ( পলিটিকাল সিস্টেম )
দেশ শাসন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠন অপরিহার্য। কোন ছোটখাটো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকেও সক্রিয় রাখতে হলে এর জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বা কর্ম পরিষদ বা কার্যকরী কমিটি গঠন করতেই হয়। আর রাষ্ট্রের মত সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে সরকার গঠন করা ছাড়া উপায় নেই।
এ সরকার গঠন সব কালে এবং সব দেশে একরকম হয় না। বর্তমান যুগেও বহু দেশে সরকারী ক্ষমতা কোন কোন রাজবংশের হাতে রয়েছে। বাদশাহ বা রাজা ঐ বংশের বাইরে থেকে হতে পারে না। বাদশাহ যে মন্ত্রী সভা গঠন করেন তার মধ্যে ঐ বংশের বাইরেরও কিছু লোক থাকলেও তারা তার আস্থাভাজনই হয়ে থাকেন। এ ধরণের সরকারকে রাজতন্ত্র বা মনারকী বলা হয়। এসব দেশে নামে মাত্র নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকলেও আসল ক্ষমতা বাদশাহ এব্বং তার বংশের লোকজনের হাতেই কুক্ষীগত থাকে।
কোন দেশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে দেশ পরিচালনা করলে তাকে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ত বা ডিক্টেটরশিপে ( Dictatorship ) নামে পরিচিত হয়।
আর যেসব দেশে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত লোকেরা দেশ শাসন করে থাকে সে সরকার পদ্ধতিকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রে সরকারী ক্ষমতা কোন বংশ, এলাকা বা শ্রেনীর লোকদের হাতে কুক্ষিগত হতে পারে না। জনগন যাদেরকেই নির্বাচিত করে তারাই সরকার গঠন করবে। পরবর্তী নির্বাচনের ফলে আবার আরেক দলের হাতে ক্ষমতা চলে যেতে পারে। গণতন্ত্রের আসল রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগনের হাতে।
দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। যে দেশে রাজতন্ত্র আছে সে দেশের জনগণও গণতন্ত্র চায়। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও গণতন্ত্র কোন দান খয়রাতের মাধ্যমে কায়েম হয়নি। যে ইংল্যাণ্ড বর্তমানে আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রশংসিত সেখানেও জনগণ কয়েকশ বছর সংগ্রাম করার পর সফল হয়েছে। আধুনিক যুগে গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের এতো দীর্ঘ সময় না লাগলেও বিনা সংগ্রামে কোন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হতে পারে না। ( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি
গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রধানত দুই ধরণের সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। একটার নাম পার্লামেন্টারি সিস্টেম বা সংসদীয় পদ্ধতি। অপরটি প্রেসিডেন্টশিয়াল সিস্টেম বা রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি।
পার্লামেন্টারি সিস্টেমের পরিচয় নিম্নরূপঃ
১। জনগনের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বা সংসদই সরকারী ক্ষমতার অধিকারী। রাজনৈতিক এবং আইনগত সার্বভৌমত্ব সংসদের হাতে ন্যস্ত। সংসদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।
২। সংসদ সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন যে দল ভোগ করে সরকারী ক্ষমতা সেই দলের হাতেই থাকে। প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রী পরিষদ এ দলের মধ্য থেকেই নিয়োগ করে থাকেন। সংসদে কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে একাধিক দলের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারে।
৩। মন্ত্রী পরিষদ সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। জনপ্রতিনিধিগণ সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন বা অভিযোগ করতে পারেন।
৪। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে গণ্য। সরকারের সকল প্রকার দায় দায়িত্ব তার।
৫। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি মাত্র। দেশের শাসন ক্ষমতা তার হাতে থাকে না। শাসনযন্ত্র যে কয়টি দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে এর অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার তার নেই। শাসনতন্ত্রে উল্লেখ থাকলে তিনি সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন।
প্রেসিডেন্টশিয়াল সিস্টেম বা রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিচয় নিম্নরূপঃ
১। প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধান। তিনিই দেশের প্রধান শাসনকর্তা।
২। প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই জনগনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।
৩। জনগনের নির্বাচিত সংসদ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার অংশীদার।
৪। শাসনতন্ত্রে এমন ভারসাম্য থাকবে যাতে প্রেসিডেন্ট বা সংসদ কেউই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী না হয়।
৫। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রী সভার সদস্যদের জনগনের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক নয়।
( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
দুই পদ্ধতির পার্থক্য
পার্লামেন্টারি এবং প্রেসিডেন্টসিয়াল পদ্ধতি দুইটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য। যেমনঃ
১। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান এক ব্যক্তি নয়। অপরটিতে একই ব্যক্তি দুইটি মর্যাদা ভোগ করেন। প্রথমটিতে প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান। দ্বিতীয়টিতে কোন প্রধানমন্ত্রী নেই। প্রেসিডেন্টই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী।
২। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট বা সংসদ দেশ শাসন করে এবং সংসদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভা প্রশাসনের নেতৃত্ব দেয়। অপরটিতে প্রেসিডেন্ট এবং তার মন্ত্রী সভা দেশ শাসন করে এবং পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় অংশীদার হয় ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করে।
৩। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের কোন শাসন ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপ্রধান সম্পূর্ণ দল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। সরকার গঠন, সরকার পরিবর্তন, আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন ইত্যাদির ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করেন এবং শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকাও পালন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে গণ্য। যখন সরকার ভাংগে এবং গড়ে তখনও রাষ্ট্রপ্রধান সপদে বহাল থাকেন।
( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
গণতান্ত্রিক বিশ্বের সরকার পদ্ধতি
যতগুলো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম আছে তার মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ( United states of America- USA ) ছাড়া আর কোথাও প্রেসিডেন্টসিয়াল সিস্টেম চালু হয়নি। প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেম প্রচলিত আছে। অবশ্য ফ্রান্স এবং জার্মানি এই দুইটি পদ্ধতির কোনটাকেই হুবহু নকল করেনি। তবু বলা চলে যে, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সাথে এই দুইটি দেশের বেশী মিল রয়েছে।
পলিটিকাল সিস্টেম হিসেবে আমেরিকার পদ্ধতিটি পূর্ণ গনতন্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃত হলেও আর কোন দেশেই তা হুবহু গ্রহণ করা হয়নি। সে দেশে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হওয়া সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতায় সিনেটের অংশীদারিত্ব এবং কমিটি সিস্টেমের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকায় গণতান্ত্রিক নীতিমালা সেখানে বহাল রয়েছে।
আমেরিকার পদ্ধতি পূর্ণ গণতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও আর কোন দেশে তা চালু না হওয়ার দুইটি কারনঃ
১। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একটি রাষ্ট্র বটে, কিন্তু একসময় তা ছিল না। দুইশ বছর আগে ১৩ টি স্বাধীন রাষ্ট্র মিলে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে গিয়ে তাদেরকে অনেক নতুন নিয়ম- পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হয়। রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে দেশে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা অন্যত্র অনুপস্থিত। তাই প্রেসিডেন্টসিয়াল পদ্ধতি আমেরিকার জন্য যতই উপকারী হোক অন্য কোন দেশ তা নিজ দেশের জন্য উপযোগী মনে করেনি।
২। বিশেষ করে সেখানে শাসন বিভাগ ( Executive ) ও আইন বিভাগেরই ( Legislature ) মধ্যে একদিকে সাংগঠনিক পার্থক্য, আর একদিকে ক্ষমতার অংশীদারীত্ব এমন নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যতা ( Check and Balance ) কায়েম করেছে যা রীতিমত জটিল। এ জটিল পদ্ধতির নকল করার ঝামেলা আর কোন দেশ পোয়াতে চায়নি।
ব্রিটিশ পদ্ধতিকে সহজবোধ্য ও অনুকরণের অধিক যোগ্য বলে বিবেচনা করেই হয়তো প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে তা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো স্বাধীন হবার পূর্ব থেকেই এ পদ্ধতির সাথে পরিচিত বলে সেসব দেশে এর গ্রহণ যোগ্যতাও বেশী।
( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
সরকার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক
তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে রয়েছে। এসব দেশের কোনটিতেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নেই। এর অনেক কয়টিতে নির্বাচিত সংসদও রয়েছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতেই কুক্ষীগত। এসব দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করলে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবী তুললে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে চালাকী করে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গনতন্ত্র চালু রয়েছে এবং এটা অগণতান্ত্রিক নয়। অথচ বাস্তবে চরম স্বৈরাচারী ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।
জনগনকে ধোঁকা দেবার জন্য এসব দেশের ডিক্টেটররা আমেরিকার দোহাই দিয়ে দাবী করে যে, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এক হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার গণতন্ত্র স্বীকৃত হলে অন্য দেশে কেন হবে না ? সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের গোলামী থেকে স্বাধীন হবার পর তাদের সরকার পদ্ধতির নকল করার প্রয়োজন কি ? এ জাতীয় কুযুক্তি দেখিয়ে স্বৈরশাসকরা শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখার অপচেষ্টা চালায়।
বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনামলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এ বিতর্করেই সম্মুখীন হয়েছিল। আমেরিকার জটিল গণতন্ত্র সম্পর্কে খুব কম লোকই অবহিত বলে এ জাতীয় প্রচারণার আশ্রয় নেয়া সম্ভব হচ্ছে। জেনারেল আইয়ুব খানও এ বিষয়ে একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আমেরিকার পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতারণামূলক দাবীই করেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব কারনে সেখানে গণতন্ত্র বহাল রয়েছে সেসব অনুসরণ না করে শুধু পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হওয়াকেই আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নাম দিয়েছিলেন।
আইয়ুব খান, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সরকার দলীয় প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান একই ব্যক্তি থাকায় প্রকৃতপক্ষে এর কোনটাই গণতান্ত্রিক সরকার ছিলনা। শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল শাসনের পরিবর্তে জেনারেল জিয়া বহু দলীয় গণতন্ত্র চালু করেছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষমতা তখনো এক ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল বলে তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না।
( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
গণতান্ত্রিক সরকার
সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ব আলচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, আমাদের দেশের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয় এবং তা অনুকরণ করা এদেশে সম্ভবও নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি পদ্ধতি কি হুবহু নকল করা সম্ভব ? ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিটিশ ক্রাউন। জাপান ও মালয়েশিয়ায় কিং বা রাজা থাকায় তারা ব্রিটিশ সিস্টেম মোটামুটি হুবহু নকল করতে পেরেছে। কিন্তু তারাও রাজনৈতিক দলের সংখ্যার দিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করতে পারেনি। ইংল্যান্ডে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা অদল বদল করে ক্ষমতায় আসে। এতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবনহগ ভারসাম্য বহাল থাকে। এমনটা আর কোন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে সম্ভব হয়নি। তাহলে ব্রিটিশ পদ্ধতি হুবহু নকল করার কোন উপায় নেই। আরও বহু দেশে কিং বা রাজা ছাড়াই সংসদীয় সরকার কায়েম রয়েছে। এর দ্বারা একথাই প্রমান হয় যে, যে কোন দেশের সরকার পদ্ধতি আরেকটা দেশের পক্ষে শতকরা একশো ভাগ নকল করা সম্ভব নয়। আসলে এর কোন প্রয়োজনও নেই। সব গাছ যেমন সব দেশে হয় না, সব ফলও যেমন সব মাটিতে ভালো ফলে না, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিও সবদেশে হুবহু একই রকম হতে পারে না। প্রত্যেক দেশের মানুষের মন মানসিকতা, ঐতিহ্য- ইতিহাস, সমাজ কাঠামো মিলিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে এর সাথে খাপ খায় এমন সরকার পদ্ধতি গড়ে তোলা সেদেশের নেতৃবৃন্দেরই দায়িত্ব।
একই সংসদীয় সরকার পদ্ধতি কায়েম থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে কাঠামোগত কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। আসল বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্রের দাবী পূর্ণ হওয়া। যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক নীতি চালু থাকে তাহলে সরকার পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সিস্টেম থেকে ভিন্নতর কিছু থাকলেও বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে।
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন। দেশ- কাল পাত্র ভেদে ঐ মূল্যবোধকে ভিত্তি করে পলিটিকাল ইন্সটিটিউশন গড়ে তুলতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারের বাহ্যিক রূপ এক রকম নাও হতে পারে। বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বহাল থাকতে পারে। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির সরকার কাঠামো ভিন্ন হলেও এসব দেশেই পূর্ণ গণতন্ত্র চালু রয়েছে বলে সবাই স্বীকার করে।
যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যারা সত্যিকারভাবে গণতন্ত্রের শাসন চান তারা নিম্নরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে একমত। ----
১। রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির উপরে থাকা উচিত নয়। এক ব্যক্তির উপর উভয় দায়িত্ব থাকলে স্বৈরাচারের আশংকা থেকেই যাবে।
২। দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা জনগনের নির্বাচিত সংসদের হাতে থাকবে। অর্থাৎ শাসকগণ বা মন্ত্রী পরিষদ সংসদের কাছে জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন।
৩। শাসনযন্ত্রকে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে শাসনতন্ত্র বিপন্ন না হয়।
৪। সত্যিকার নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সরকারী দল নির্বাচনের সময় প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ না পায়।
দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে এ পদ্ধতি তুলে দিতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোন দেশের নযীর দেখিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়জনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।
( ৯৩ সালে কারাগারে রচিত )
পার্লামেন্টারি সিস্টেমের রাষ্ট্রপ্রধান
পার্লামেন্টারি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- সরকার প্রধান থেকে ভিন্ন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। যুক্তরাজ্যই এই সিস্টেমের জনক। ব্রিটিশ ক্রাউন না রাজ সিংহাসনের অধিকারীই সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত। ব্রিটিশ ক্রাউন ব্যতীত ব্রিটিশ পলিটিকাল সিস্টেম চলতে পারে না। সেখানে রাজা বা রানী উত্তরাধিকার সূত্রে একটি পরিবার বা বংশ থেকেই হয়ে থাকে। অথচ গণতন্ত্রের পাদপীঠ বলে সারা দুনিয়ায় যুক্তরাজ্য পরিচিত।
পার্লামেন্টারি সিস্টেমে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সরকার প্রধান হবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পৃথক এক ব্যক্তির সত্তার হাতে থাকতে হবে। এ সিস্টেমে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান এক ব্যক্তি হতে পারবে না। ইংল্যাণ্ডে রাজবংশের যে ব্যক্তি সিংহাসনে থাকবেন সেই রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। সে পুরুষ বা স্ত্রী যাই হোক না কেন।
ব্রিটিশ ক্রাউন সহ যে পার্লামেন্টারি সিস্টেম তা কি বাংলাদেশে হুবহু চালু করা সম্ভব ? ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ করা সম্ভব হলেও রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই বলে সবাইকে স্বীকার করতেই হবে।
ভারত সহ কয়েকটি দেশে এ সিস্টেম চালু আছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান একই নিয়মে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হয় না। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় নিজ নিজ সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ক্রাউনের দ্বারা নিযুক্ত হয়।
দেখা গেলো যে, ব্রিটিশ সিস্টেম ঐ কয়টা দেশ অনুসরণ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায় নিজ দেশের উপযোগী ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বেলায় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সে বিষয়ে একাধিক মত থাকতে পারে। যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করেই কোন একটি পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কোন মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে হবে।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি
বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ? পূর্বে একথা স্পষ্টভাবে বলেছি যে, রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির উপরে থাকা ঠিক নয় এবং মন্ত্রী সভা জাতীয় সংসদের নিকটই দায়ী থাকবে। এটা যে পার্লামেন্টারি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য তা সবারই জানা। বাংলাদেশে এসব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পলিটিকাল সিস্টেমের পক্ষে প্রায় সব দলই একমত। মতপার্থক্য দেখা যায় প্রধানত প্রেসিডেন্টের নির্বাচন এবং মর্যাদা সম্পর্কে।
শেখ মুজিবের আমলে প্রথম দিকে যখন পার্লামেন্টারি পদ্ধতি চালু ছিল তখন জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীই সাক্ষী যে তিনি কতটুকু মর্যাদা পেয়েছিলেন। সম্ভবত বিচারপতি ছিলেন বলেই কতকটা আত্মসম্মানবোধ তাকে মর্যাদাহীন পদটি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এরপর অবশ্য এমন এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হল যার হয়তো মর্যাদাবোধের কোন বালাই ছিল না বা সরকারের নির্দেশ পালনকেই তিনি তার দায়িত্ব বলে মনে করতেন।
গণতন্ত্রের দাবী অনুযায়ী সংসদের হাতেই পূর্ণ শাসন ক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা যদি নিরংকুশ হয় তাহলে সীমালঙ্ঘনের আশংকা অবশ্যই প্রবল হয়। ফলে ক্ষমতার দাপটে শাসনতন্ত্র ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিনত হয়। আইনের শাসনের পরিবর্তে দলের শাসন গনতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। শেখ মুজিবের আমলে তাই হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট যদি সরকারী দলের হাতের পুতুল হয় তাহলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক।
প্রেসিডেন্টকে প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ কাজটি এমন এক ব্যক্তির পক্ষেই পালন করা সম্ভব যিনি শাসক দলের করুণার পাত্র নন।
যিনি ক্ষমতাসীন দলের নিযুক্ত বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত ব্যক্তি তিনি সরকারের মর্জির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কি করে পালন করতে সক্ষম হবেন ?
যারা পার্লামেন্টারি সিস্টেম চান তারা ভালো করেই জানেন যে, ইংল্যান্ডের ক্রাউন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করে থাকেন। বাংলাদেশে আমরা কোন ক্রাউন তৈরি করতে চাই না। কিন্তু ক্রাউনের ঐ দায়িত্বটা পালন করার জন্য এমন প্রেসিডেন্ট অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন যিনি ক্ষমতাসীন দলের হুমকী বা দলীয় রাজনৈতিক কোন্দলের স্বীকার হতে বাধ্য মনে করবেন না। যদি জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে তাহলে ঐ হুমকী এবং কোন্দল থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেন না। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর দশা যাতে কোন প্রেসিডেন্টের না হয় সে ব্যবস্থাই করা প্রয়োজন।
কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভারতে তো আইন সভার সদস্যদের ভোটেই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। বাংলাদেশে কেন এ পদ্ধতি চলবে না ? যারা এ প্রশ্ন করেন তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এক দেশে এ ব্যবস্থা চালু থাকলেই তা অন্য দেশের জন্য উপযোগী হয়ে যায় না। তাছাড়া ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানের অবস্থা বাংলাদেশের মত নয়।
ভারতে কেন্দ্রীয় আইন সভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রাদেশিক আইন সভা ২৫ টি। এসব আইন সভার বিরাট সংখ্যক সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয় বলে প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিনত হওয়া সেখানে সহজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যোগ্য নেতৃত্বে গণতন্ত্র ক্রমেই ভারতে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার ডিক্টেটর হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। গণতন্ত্র সেখানে আবার বহাল হয়েছে। দ্বিতীয়বার যখন গণতান্ত্রিক পন্থায়ই ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলেন তখন পূর্বের জনতা সরকারের আমলের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের কোন চেষ্টা করেননি। দীর্ঘদিনে ভারতে যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার ঠিক বিপরীত অবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান।
বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল থেকেই রাজনীতির যে ধারা চলছে তাতে গণতন্ত্রের বিকাশ হতেই পারেনি। ক্ষমতাসীনরা যেমন বিরোধীদলকে নিরাপত্তা আইন ও সরকারী ক্ষমতার ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছেন ঠিক তেমনি এর প্রতিক্রিয়ায় কোন কোন বিরোধীদল হিংসা- বিদ্বেষ ও গুণ্ডামির হাতিয়ার ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনায় এখনো যে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং কোন কোন দল যেভাবে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করে তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তো দুরের কথা, এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসেনি। এ পরিস্থিতিতে যদি সরকারী দল এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাটুকুও খতম হয়ে যাবে। ( বাংলাদেশের রাজনীতি )
প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব
গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমনঃ
১। প্রেসিডেন্ট যাতে শেখ মুজিবের আমলের মত প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিনত না হতে পারে সেজন্য প্রেসিডেন্টকে যোগ্যতার সাথে সরকারের বাড়াবাড়ি অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে শাসনযন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। শাসনতন্ত্রের মজবুত অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের ভার প্রেসিডেন্টের হাতে থাকাই স্বাভাবিক।
২। কোন কারনে একবার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে বিকল্প সরকার গঠন পর্যন্ত বা বার বার সরকার ভেঙ্গে যাবার দরুন স্থিতিশীল সরকারের অভাবে প্রেসিডেন্টকে শাসনতন্ত্রের সঠিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শাসনতন্ত্র যাবতীয় সরকারী ক্ষমতার উৎস হিসেবে এর সঠিক মর্যাদা বহাল রাখা এসব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব।
৩। নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হলে ক্ষমতাসীন দলসমূহের দলীয় স্বার্থ থেকে প্রেসিডেন্টকে ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। তাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনগন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন করতে হবে।
বলা বাহুল্য এসব দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ ক্রাউন পালন করে থাকে। বাংলাদেশ এ দায়িত্ব পালনের উপযোগী মর্যাদায় যাকে অধিষ্ঠিত করা হবে তিনি যদি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুগ্রহ ভাজন হন তাহলে এ মহান দায়িত্ব তিনি কখনোই পালন করতে পারবেন না।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
জনগনের প্রেসিডেন্ট
দেশের অতীত অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পরিস্থিতির দাবী এটাই যে, শাসনতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে ও সরকারী ক্ষমতায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বহাল রাখার প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রেসিডেন্টকে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হতে হবে। জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাসীন দল কখনোই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেনা। প্রেসিডেন্টের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা থাকবে না বলে নিঃস্বার্থভাবে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাথেও তিনি ইনসাফ পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবেন।
এমন মর্যাদা সম্পন্ন প্রেসিডেন্ট তিনিই হতে পারবেন যিনি একমাত্র জনগনের নিকট দায়ী থাকবেন। শুধু ক্ষমতাসীন দলের একক ভোটে তাকে অপসারণ করা চলবে না। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। ব্রিটিশ ক্রাউনের সমমর্যাদার অধিকারী প্রেসিডেন্ট একমাত্র এভাবেই যোগাড় করা সম্ভব।
বাংলাদেশে কয়েকবার জনগনের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ থেকে পিছিয়ে আসা উচিত নয়। যারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণকে ভোট দেবার অধিকার দিতে চান না তারা যতই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দিক নির্বাচনে এটাকে কি তারা নির্বাচনী ইস্যু বানাতে সাহস করবেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগনের ভোটের প্রয়োজন নেই বলে কি তারা জনগণকে বুঝাতে পারবেন ? সুতরাং পূর্বে জনগন যখন সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন তখন এ অধিকার তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী হবেন না। এ বিষয়টা গণভোটে দিলে জনগন কি রায় দেবে তা সবারই জানা।
এ পর্যন্ত একটি যুক্তিই এর বিপক্ষে পাওয়া গেছে। এ গরীব দেশে এ জাতীয় নির্বাচনে সরকারী দল বিপুল অর্থ খরচ করবে এবং বিরোধী দলের প্রার্থী এতো খরচ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এ কথা সংসদ সদস্য নির্বাচনের বেলায়ও সত্য। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতি। সরকারী ক্ষমতা এবং সুযোগ কোন নির্বাচনেই দল বিশেষের হাতে কুক্ষিগত থাকা ঠিক নয়। এ সমস্যাটি ভিন্ন একটা আপদ। এর সাথে প্রত্যক্ষ ভোটের কোন সম্পর্ক নেই।
জনগনের ভোটে প্রেসিডেন্টের মত “টিটিউলার হেড” বা শাসন ক্ষমতাহীন পদের নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই যে বিরাট অংকের খরচ হবে তাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে তাদের নিকট শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা এবং অভিভাবকত্ব তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে মনে হয়। একটা দেশের রাজনৈতিক সিস্টেমকে গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী টিকিয়ে রাখা যদি সরকারী স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে কৃপণতা দেখানো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। অবশ্য নির্বাচনের ব্যয় কমাবার উদ্দেশ্যে পারলামেন্ত এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন একই সাথে অনুস্থান করে যেতে পারে। ( বাংলাদেশের রাজনীতি )
বাংলাদেশের পলিটিকাল সিস্টেম
যে কোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রধানত সে দেশের উপযোগী পলিটিকাল সিস্টেমের উপর নির্ভর করে। শাসনতন্ত্রে যতো ভালো কথাই লেখা থাকুক তার বাস্তব প্রয়োগ দেশের পলিটিকাল সিস্টেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সিস্টেমকে বাংলায় সরকারী অবকাঠামো বলা যেতে পারে।
বাংলাদেশে কোন স্থিতিশীল সিস্টেম এখনো গড়ে উঠেনি। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর কয়েক দশকেও কোন সিস্টেম গড়ে না উঠার প্রধান কারণই গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। একই সময়ের মধ্যে ভারতে একটি সিস্টেম স্থিতিশীল হয়ে গেলো, অথচ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তা সম্ভব হল না। এর কারন বিস্তারিত বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। তবে প্রধান কারন একটাই। শুরু থেকেই দেখা গেছে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যিনিই অবস্থান নেবার সুযোগ পেয়েছেন, তিনি নিজের গদী মজবুত করারই পরিকল্পনা করেছেন। জনগণকে রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস মনে করে তাদের প্রতিনিধিদের মরজি অনুযায়ী দেশ শাসনের নীতি গ্রহণ না করার এটাই পরিনতি।
ব্যক্তিভিত্তিক সিস্টেম
নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, গোলাম মুহাম্মাদ, ইস্কান্দার মির্জা, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন কালের বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রমানিত হয় যে, তারা বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্থাশীল ছিলেন না। তারা নিজস্ব সিস্টেমে মনগড়া পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করায় তাদের ক্ষমতাচ্যুত হবার সাথে সাথে সিস্টেমও খতম হয়ে গিয়েছে। লিয়াকত আলীর একক শাসন, গোলাম মুহাম্মাদের স্বেচ্ছাচার, ইস্কান্দার মির্জার কন্ট্রোল্ড ডেমক্রাসী, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র, ইয়াহিয়া খানের গদীতন্ত্র এবং শেখ মুজিবের একদলীয় সিস্টেম তাদের গত হবার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে গিয়েছে।
জেনারেল জিয়াউর রহমানের দেয়া সিস্টেমে বহু দলীয় গণতন্ত্র থাকলেও রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, দলীয় প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান একই ব্যক্তি হওয়ায় এবং প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নামে পার্লামেন্ট পংগু করে রাখায় সংগত কারনেই কোন সন্তোষজনক গণতান্ত্রিক সিস্টেম গড়ে উঠেনি। জেনারেল এরশাদও নিজস্ব সিস্টেমের পরিকল্পনা নিয়েই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে শাসন ক্ষমতায় এতোটা অংশীদার করার পক্ষপাতী ছিলেন যাতে সামরিক শাসনের দরকার না হয় এবং সেনাপতিরা রাজনৈতিক সরকারের সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন।
১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সংসদীয় সরকার পদ্ধতি কায়েম হয়েছে বটে কিন্তু সত্যিকার গণতান্ত্রিক বিধি- বিধান মেনে চলার ঐতিহ্য গড়ে না উঠা পর্যন্ত রাজনৈতিক সুস্থিরতা ও স্থতিশীলতা আশা করা যায় না।
বিশেষ করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্ট শুধু সরকারী দলের প্রতিনিধি। তিনি শ্বাসতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারের উপর সামান্যতম চাপ সৃষ্টি করারও পজিশন ভোগ করেন না।
১৯৯৩ সালের ৩রা জানুয়ারী জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে সরকারী দলের একান্ত অনুগত ব্যক্তির দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। দেশের ১২ কোটি মানুষের নেতার দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরকারী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা ছাড়া কোন বিষয়েই উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতেও তিনি সক্ষম হননি। এই ব্যক্তিই যদি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি আরও বলিস্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতেন।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি চালু থাকলে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠার আশংকা রয়েছে।
গণতান্ত্রিক সিস্টেম
বাংলাদেশের অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, বর্তমান সংকট এবং জটিলতা ও স্থিতিশীল রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে একটা ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমের প্রস্তাব এখানে পেশ করা হয়েছে। এ প্রস্তাবটির পক্ষে এবং বিপক্ষে যতো যুক্তি থাকতে পারে তা ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব রাজনীতি সচেতন মহলের।
এ প্রস্তাবটিতে ৫ টি দফা রয়েছে যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই পেশ করা হচ্ছে। সংসদীয় পদ্ধতি এবং প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট বলেই আমার ধারণা। ( বাংলাদেশের রাজনীতি )
৫ দফা প্রস্তাব
১। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট
ক। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।
খ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একই সাথে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।
গ। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হবে ৫ বছর।
ঘ। কোন কারনে প্রেসিডেন্টের পদ শুন্য হলে নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। কোন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।
ঙ। যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবিধান গুরতরভাবে লংঘিত হয় বা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে সংসদ সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।
চ। এভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব পালন করলে কোন দলের আপত্তি থাকবে না।
ছ। ভাইস প্রেসিডেন্টকে স্পীকারের দায়িত্ব অর্পণ করলে সংসদে দল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার বেশী সুযোগ পাবেন এবং তিনি সহজেই সকল দলের আস্থা অর্জন করতে পারবেন।
২। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব
ক। শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তার হাতে থাকবে না।
খ। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়োজনে তারা দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না।
গ। নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের পদে বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। অবশ্য নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।
ঘ। সরকার যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মর্যাদা হারায় এবং অন্য কেউ যদি সরকার গঠনে সক্ষম না হন তাহলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেংগে দিয়ে ৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।
ঙ। প্রেসিডেন্ট সরকারকে উপদেশ দিতে পারবেন। তবে তা বাধ্যতামূলক হবে না।
৩। শাসন ক্ষমতা
ক। জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করবেন।
খ। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধানের মর্যাদা ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত পন্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।
গ। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী সভা জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না হারানো পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী থাকবেন।
ঘ। জাতীয় সংসদ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত ফায়সালা দিবেন।
ঙ। সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে দলের টিকিট নিয়ে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সে দল ত্যাগ করলে তিনি সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে ধরা হবে।
৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ক। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রী সভা এবং জাতীয় সংসদ ভেংগে দিতে হবে।
খ। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করবেন।
গ। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন না।
ঘ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং এর উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।
ঙ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।
৫। নির্বাচন কমিশন
ক। সুপ্রিমকোর্টের সর্বোচ্চ বেঞ্চ একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।
খ। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
গ। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপরে ন্যস্ত থাকবে।
ঘ। নির্বাচন সক্রান্ত সকল কাজে গোটা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবেন।
ঙ। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে।
দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন, স্থিতিশীল সরকার, আইনের শাসন, জনগনের সত্যিকার প্রতিনিধিদের সরকার কায়েম এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস রোধ করতে হলে উপরোক্ত পলিটিকাল সিস্টেমের চাইতে উন্নত কোন প্রস্তাব কারো কাছে থাকলে সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হোক।
( বাংলাদেশের রাজনীতি )
সমাপ্ত
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি