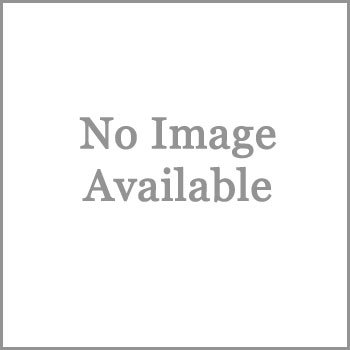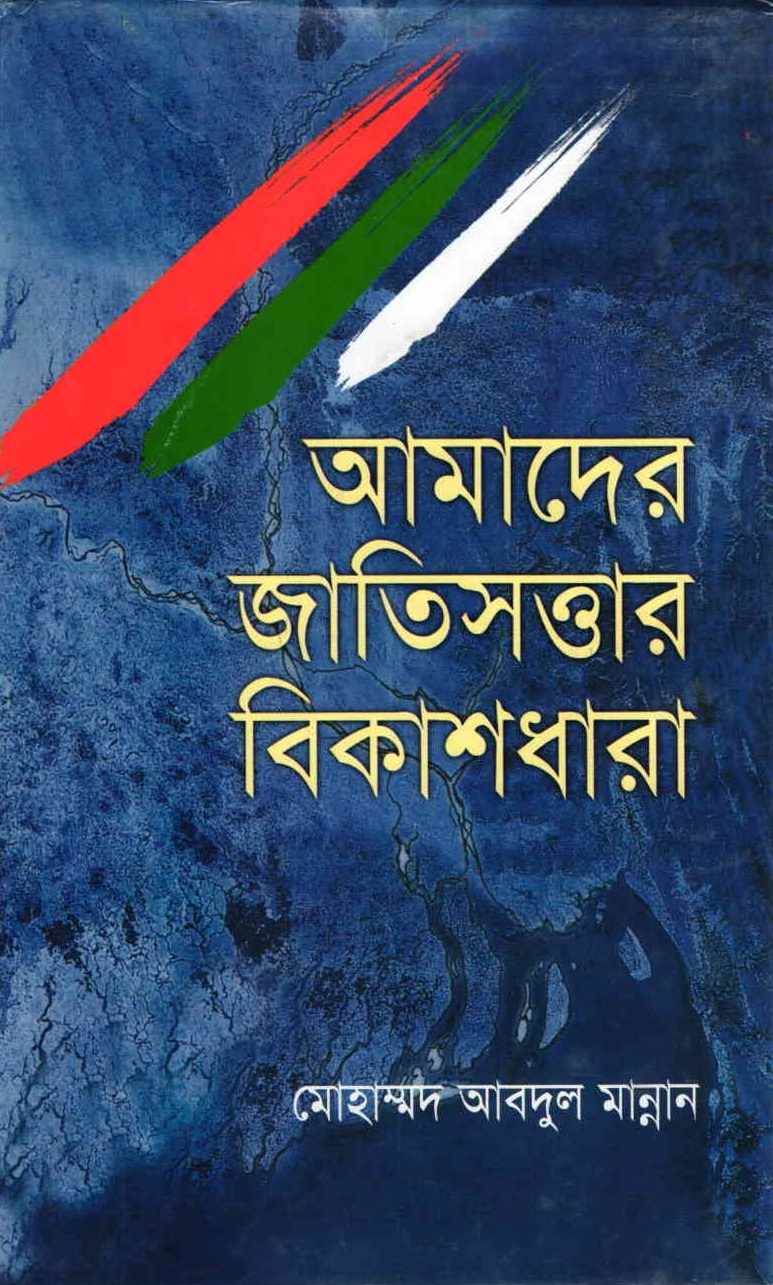৬
পলাশী বিপর্যয় ও কলতার উত্থান
পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্যাস্ত ঘটল ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। পলাশীর শিবিরে দু’দিন সসৈন্যে অবস্থান করলেন ক্লাইভ। তারপর দু’শ ইংরেজ ও পাঁচশ’ দেশীয় সৈন্য নিয়ে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা নীরবে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এই মোড় পরিবর্তনের ঘটনার সাক্ষী হলো। ক্লাইভ নিজে স্বীকার করেছেনঃ
“ইচ্ছা করলে মুর্শিদাবাদের জনতা শুধু লাঠি আর পাথর মেরে এই নতুন বিজেতাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারত। লোকেরা নাকি বলাবলিও করেছে, কোন অস্ত্র ছাড়া শুধু ইটপাটকের মেরেই মুর্শিদাবাদের লোকেরা ইংরেজদের ধরাশায়ী করতে পারত”। (ভোলানাথ চন্দ্র : দি ট্রাভেল অব এ হিন্দু, লন্ডন, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৬৮)
মুর্শিদাবাদের লুটপাট : উত্থানের সূচনা
পলাশী বিপর্যয় মুর্শিদাবাদের সাথে সাথেই কোন বড় রকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায় না। শাসক মহলের অন্তঃপুরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আর বিশেষ সম্প্রদায়ের ‘বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষয়রোগ’ জাতির প্রতিরোধ-চেতনা পঙ্গু করে ফেলেছিল। শাসক ও জনতা ছিল আত্মিক সম্পর্কহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। উদ্যমহীন এই নিস্পৃহ মানুষেরা অবাক চোখে দেখল মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনের ঘটনা। ক্লাইভের নিজ তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ নিঃশেষে লুণ্ঠিত হলো। এরপর ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই পুতুল নবাব মীর জাফর আলী খাঁ রাজকীয় শন-শওকতের সাথে ইংরেজদের ‘যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের’ প্রথম কিস্তির টাকা কলকাতায় পাঠালেন সোনা-চাঁদির মাধ্যমে।
“সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্র করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা দুই শত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইল”। (রমেশচন্দ্র মজুমদার)
কলকাতার উত্থানের সূচনা এখান থেকেই। মুর্শিদাবাদের জনগণ এবারে তারেদ অন্তরে একটা অব্যক্ত জ্বালা অনুভব করল। কোথায় যেন একটা বড় রকম ছন্দপতন ঘটে গেছে!
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করলো ২ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর বাইরে ব্যক্তিগত পারিতোষিক আর উপহার উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ৫৮ লাখ হাজার ৭০ হাজার টাকা। ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত ‘নবাব উঠানো-বসানো’র রাজনীতি করে কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারী প্রচুর অর্থ-কড়ির মালিক হলো। নানা অজুহাতে কোম্পানি করল বিস্তর আয়-রোযগার। সেই অর্থের পরিমাণ এক কোটি ৪৫ লাখ ২ হাজার ৫৬৬ পাউন্ড। তখনকার হিসেবে তেরো কোটি টাকা। (ব্রিজেন কে গুপ্ত : সিরাজউদ্দৌলা এন্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃষ্ঠা ১২৬-২৭) মীর জাফর-মীর কাসিম-নাজমুদ্দৌলার নবাবীর মাশুলে ক্লাইভ আর ভেরেলস্টের ব্যক্তিগত বখরা ছিল ২১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৬৫ পাউন্ড। (রমেশচন্দ্র দত্ত : ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১৭৫৭-১৮৩৭, পৃষ্ঠা ৩২) এছাড়া ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বার্ষিক তিন লাখ টাকা আদায়ের জায়গীর। এই বিরল সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে এদেশ থেকে ক্লাইভ-ভেরেলস্ট-এর দ্বারা বিতাড়িত ইংরেজ কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস লিখেছেনঃ
“The plunder which the superior servants of the Company acquired in the year 1757 ……. suddenly enabled many of them to return to England with princely fortune”. (Considerations on Indian Affairs, part-II London, 1775. P-3)
ইংরেজদের লুণ্ঠন সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেনঃ
“নবাবের সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত করে, জমিদারী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করে এবং আরও নানা উপায়ে উৎকোচ-উপঢৌকন নিয়ে চার্ণক-হেজেস-ক্লাইভ-হেষ্টিংস-কর্নওয়ালিসৈর আমলের কোম্পানির কর্মচারীরা যে কি পরিমাণ বিত্ত সঞ্চায় করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় না। …. দেখতে দেখতে প্রচুর অর্থ ও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কোম্পানি সাহেবরা সত্যি সত্যি নবাব বনে গেলেন। তাদের মেজাজ ও চালচলন সবই দিন দিন নবাবের মতো হয়ে উঠতে লাগল”। (কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৫)
‘হঠাৎ-নবাব’ এই ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে এসেছিল বার্ষিক পাঁচ, দশ, পনের কিংবা পঁচিশ পাউন্ড বেতনের ‘রাইটার’, ‘ফ্যাক্টর’, ‘জুনিয়ার মার্চেন্ট’ বা ‘সেমি-মাচেন্ট’ হিসেবে। ‘লোফার’ শ্রেণীর এই ইংরেজ কর্মচারীরাই স্বনামে-বেনামে বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন-শোষণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে কাড়ি কাড়ি টাকা পাচার করে নিজ দেশেও ‘কিংবদন্তীর রাজপুত্তুরের’ ইমেজ অর্জন করেছিল। কোম্পানির ‘দস্তক’র অপব্যবহার করে পাঁট পাউন্ড বেতনের কর্মচারীরা এদেশে মুৎসুদ্দী-অর্থলগ্নিকারীর মূলধনে বছরে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করছিল্। তার ওপর ছিল নানা প্রকার ঘুষ ও উপঢৌকন। তাদের ব্যবসায়িক লুণ্ঠনের প্রধান অবলম্বন এ দেশীয় বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, গোমস্তা, দালাল ও ফড়িয়ারা। তাঁতি আর কামারশ্রেণীর গরীব উৎপাদকদের কাছ থেকে টাকা লূট করেও তারা বখরা তুলে দিত এসব ইংরেজ কর্মচারীর হতে । এভাবেই কোম্পানির বার্ষিক পাঁচ পাউন্ড বেতনের কেরানী হয়ে ১৭৫০ সালে এ দেশে এসে ওয়ারেন হেস্টিংস চৌদ্দ বছর পর দেশে ফিরেছিলেন ত্রিশ হাজার পাউন্ড সাথে নিয়ে। এরপর দ্বিতীয় দফার গভর্নর জেলারেলরূপে যখন তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে, বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য রূপান্তরের তখন তিনিই প্রকৃত প্রতিনিধি।
এভাবেই স্বল্প বেতনভূক’ বণিক নাবিক আর লোফার’ ইংরেজ কর্মচারীরা’ বেঙ্গল নেবুব’- এ পরিণত হলো। আর তাদের এ দেশীয় লুণ্ঠন-সহচর দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দীরা দালালীর মাহত্ম্যে রাতারাতি পরিণত হলো রাজা-মহারাজারয়। এই সম্মিলিত লুটেরা চক্রটি সম্পর্কেই ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছেনঃ “প্রথমে কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কতগুলো ভাগ্যবিতাড়িত, চরিত্রভ্রষ্ট, ধুর্ত, পলাতক, অল্প শিক্ষিত লোক বেনিয়া-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা-কেরানী-ফড়িয়া দালালরূপে অবাধে অঢেল অজস্র কাঁচা টাকা অর্জন ও সঞ্চয়ের দেদার সুযোগ পেয়ে ইংরেজদের এ দেশে উপস্থিতিকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে জানল ও মানল”। (বঙ্কিম বীক্ষা-অন্য নিরিখে, ভাষা-সাহিত্যপত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৮২)
পলাশীর বিপর্যয়ের ফলে এই দাঁওবাজ মাস্তানশ্রেণীর লোকরাই হলো এদেশের ‘ভাগ্য বিধাতা’। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি রাজস্ব আদায়ের দেওয়ানি কর্তৃত্ব লাভের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই সম্মিলিত লুটেরাচক্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্টিত হলো। তাদের হাতে বাংলাদেশের হাজার বছরের শিল্পের গৌরব মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে অবিশ্বাস্য অল্পকাহিনীতে পরিণত হলো। ইংরেজদের সৃষ্ট শুল্ক-প্রতিরোধ নীতির ফলে এ দেশের বিশ্বখ্যাত সূতি বস্ত্র ও রেশম-বস্ত্র ধ্বংস হলো। কুটির শিল্প হলো বিপর্যস্ত। আগে বাংলাদেশের কাপড় বিলাতে রফতানী হতো। এখন ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র আমাদের বাজার দখল করল।
কলকাতার ‘অবাক উত্থান’ : ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে অন্ধকার
পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাংলার প্রধান শিল্পনগরী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে দ্রুত ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকার। জনগণ শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। এসব শহরের জনসংখ্যা কমছিল দ্রুত, আর অন্যদিকে তখন কলকাতায় বইছিল সমৃদ্ধির জোয়ার। লুটেরা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য, আর তাদের লুণ্টনবৃত্তির জুনিয়র পার্টনার এদেশীয় দেওয়ান-বেনিয়ান-গোমস্তাদের উদ্যোগে তখন সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা-চিতপুর-বিরজি-চক্রবেড়ি গ্রামগুলোর ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকে দ্রুত বেড়ে উঠেলিল টাউন কলকাতা। কলকাতার এই উত্থান সম্পর্কে নারায়ণ দত্ত লিখেছেনঃ
“জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা”। (জন কোম্পানির বাঙ্গালি কর্মচারী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৩)
কাদের নিয়ে জাগল এই কলকাতা ? এরা কারা এ প্রসঙ্গে আবদুল মওদুদ লিখেছেনঃ
“আঠার শতকের মধ্যভাগে কলকাতা ছিল নিঃসন্দেহে বেনিয়ানের শহর-যতো দালাল, মুৎসুদ্দী, বেনিয়ান ও দেওয়ান ইংরেজদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের মধ্যবর্তীর দল। এই শ্রেণীর লোকেরাই কলকাতাতে সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ও বশংবদ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে”। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৮২)
বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল ‘নাবিক, সৈনিক ও লোফার’- এই তিন শ্রেণীর ইংরেজের হাতে। তাদের দেওয়ান, বেনিয়ান ও দালালরূপে এদেশীয় একটি নতুন শ্রেণী রাতারাতি কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হয়ে ইংরেজদের জুনিয়র পার্টনাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। টাউন কলকাতার কড়টা’ বইয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেনঃ
“………. ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে, আঠার শতকের মধ্যে কলকাতা শহরে যে সমস্ত কৃতি ব্যক্তি তাদের পরিবারের আভিজাত্যের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা অধিকাংশই তার রসদ (টাকা) সংগ্রহ করেছিলেন বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ীদের দেওয়ানি করে।…… এক পুরুষের দেওয়ানি করে তারা যে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, তা-ই পরবর্তী বংশধরদের বংশ পরম্পরায় আভিজাত্যের খোরাক যুগিয়ে এসেছে………। বেনিয়ানরা ……. ছিলেন বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রধান পরামর্শদাতা।…….. আঠারো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের কর্মচারীরা এ দেশে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ত করেন, তখন দেশ ও দে শের মানুষ সম্বন্ধে তাদেঁর কোন ধারণাই ছিল না বলা চলে। সেই জন্য তাঁদের ব্যবসায়ের মূলধন নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ-প্রায় সমস্ত ব্যপারেই পদে পদে যাদের ওপর নির্ভর করতে হতো তাঁরাই হলে বেনিয়ান। এই বাঙালি বেনিয়ানরাই প্রথম যুগের ইংরজ ব্যবসায়ীদের দোভাষী ছিলেন, বাণিজ্য প্রতিনিধি ছিলেন,হিসেব রক্ষক ছিলেন, এমনকি তাদের মহাজনও ছিলেন বলা চলে”। (টাউন কলকাতার কড়চা, বিহার সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৯০-৯১)
এই বাঙালি বেনিয়ানরা প্রথম যুগের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দোভাষী ,বাণিজ্য প্রতিনিধি আর মহাজন শুধু ছিল না, তারা ছিল তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরও সহচর। ১৬৯০ সালে জোব চার্ণক হুগলী নদীর উজান বেয়ে যখন কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন, তখন থেকেই এই শ্রেণীর সাথে তাদের বাণিজ্যিক যোগাোযাগের সুবাদে গড়ে উঠেছিল এক ধরনের রাজনৈতিক গাঁটছাড়া। আঠার শতকের শুরু থেকে সে সম্পর্কে আরো জোদার হয়। এ জন্যই দেখা যায় ১৭৩৬ থেকে ১৭৪৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় যে ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করে, তারা সকলেই ছিল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক। ১৭৩৯ সালে কোম্পানি কাসিমবাজারে যে পঁচিশ জন ব্যবসায়ী নিয়োগ করে তাদেরও অভিন্ন পরিচয়। এভাবেই গড়ে ওঠে ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রী। মুসলিম শাসনের অবসানই ছিল এই মৈত্রীজোটের উদ্দেশ্য। (এস. সি. হিল তাঁর গ্রন্হ ‘বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭’-এর ২৩, ১০২, ১১৬ ও ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণপঞ্জীসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।)
এই শ্রেণীর লোকেরাই বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। ব্যক্তিস্বার্থ ও সংকীর্ণ মোহাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশত এই শ্রেণীর লোকেরাই স্বাধীনতার পরিবর্তে পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিষয়টি খোলামেলা তুলে ধরে এম. এন. রায় লিখেছেনঃ
“It is historical fact that a large section of Hindu community welcomed the advent of the English power.” (India In Transition)
আার রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেনঃ
“British could winover political authority without any opposition from the Hindus.” (British Paramountcy and Indian Renaissance. Part-II, P-4)
এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিল ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রধান অবলম্বন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইজারা চুক্তি (১৭৭২-৯৩) এবং কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সুবাদে এই শ্রেণীটিই তাদের অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকার জোরে জমিদারীর মালিক হয়ে দেশের কৃষকদের ওপর স্থায়ী দস্যুতা চালানোর জন্য বৈধ কর্তৃত্ব নিয়ে চেপে বসেছিল। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা হিন্দু, গোত্রীয় পরিচয়ে দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিখ, শীল, তিলি কিংবা সাহা, পূর্ব পরিচয়ে তাদের কেউ পাঁচ টাকা বেতনের সরকার বা কেরানী, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী কিংবা পুরনো জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা। আর তাদের সকলের অভিন্ন পরিচয়-তারা বাংলার নব্য প্রভূ ইংরেজ বণিক-শাসকদের অনুগত দালাল। তারাই ইংরেজ কোম্পানির সমর্থনের ভিত্তি, বিদেশি প্রভুদের তারাই প্রকৃত রক্ষক। তারেদ জমিদারী ছড়িয়ে ছিল বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায়। কিন্তু তাদের বসবাস নিজ জমিদারী এলাকা থেকে দূরে-সদ্য জেগে ওঠা শহর কলকাতায়।
এই নতুন জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভ দমনকারী শক্তিরূপে। পলাশীর পতনে তাৎক্ষণিকভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ-চেতনা শাণিত হয়ে উঠতে বিলম্ব হয়নি। ১৭৬৩ সালেই শাসক মীর কাসিম জাতির সর্বনাম সম্পর্কে সম্বিত ফিরে পেয়ে তলোয়া র কোষমুক্ত করেছিলেন। আর একই সময়ে জনতার কাতার থেকে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের অমর নায়ক ফকীর মজনু শাহ। ইংরেজরা বাংলার সাবেক শাসক জাতির ব্যাপারে একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। লর্ড ক্লাইভ কোর্ট অব ডিরেক্টরকে এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ
“মুসলমানরা সব সময়ই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে জানলেই তারা সাথে সাথে তা সংঘটিত করবে”। (Selections from Unpublished Reords of Govt……1784-67; James Long, 1973, P-202)
বিদ্রোহের এ আশঙ্কার কারণেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয়।, তা কর্ণওয়ালিসের যবানি থেকেই খোলাসাভাবে জানা যায়। তার ভাষায়ঃ
“আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভূস্বামীদেরকের আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। যে ভূস্বাশী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করতে পারে তার মনে তার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না”। (উদ্ধৃত : বদরুদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২২)
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজদের জন্য ধারণাতীত সাফল্য বয়ে এনেছিল। তাই, ইংরেজদের ওপর চরম আক্রোশ নিয়ে বাংলাদেশের নির্যাতিত কৃষকরা যখন যুদ্ধরত, ‘মুসলমান মাত্রই রাণীর বিদ্রোহী প্রজা’- রূপে যখন চিহ্নিত, মহীশূরের টীপু সুলতান-এর মরণপণ আজাদীর লড়াই-এর ফলে ইংরেজ শাসকদের যখন হৃৎকম্প উপস্থিত, তখন কলকাতার সদ্য বিকশিত এই শ্রেণীটি প্রকাশ্যে ইংরেজদের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণার মাধ্যমে প্রভূর শক্তি বৃদ্ধি করেছিলঃ
ইংরেজদের চরম দুর্দিনে ১৮৯৮ সালের ২১ আগস্ট বাংলার জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিভূরূপে কলকাতার সেরা ধনী গৌরচণ মল্লিখ, নিমাইচরণ মল্লিক, গোপিমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা এক সভা অনুষ্ঠান করে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। (সিলেকশন ফ্রম ক্যালকাটা গেজেটস, ভল্যুম-৩, ডব্লিউ এস সিটনকার, পৃষ্ঠা ৫২৫, উদ্ধৃত স্বপন বসু : বাংলার নব চেতনার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৮৩)।
১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান আযাদীর জন্য জীবন দিলেন। কর্ণওয়ালিস বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন কলকাতায়। ‘কলকাতার প্রধান ব্যক্তিরা বাংলা ও ফারসি ভাষায় তাকে মানপত্র দিয়ে বরণ করে। (স্বপন বুস : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩)
মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তর হয় ১৭৬৮ সালে। ১৭৭৩ সালে দ্বৈত শাসন অবসানের সাথে সাথে কলকাতা ইংরেজদের ভারত-রাজত্বের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৭৭৪ সালে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট উদ্বোধন করেন। এ সময়ই তিনি কলকাতাকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তখনো কলকাতা ছিল গঞ্জ। তারপর কলকাতা হলো বন্দর। ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচারের সদরঘাট ছিল এই কলকাতা বন্দর। বন্দর থেকে ক্রমে বিকশিত হলো বন্দরনগরী। এভাবেই সারা বাংলা সম্পদ শোষণ করে বেড়ে উঠল কলকাতা মহানগরী।
এই হাঠাৎ বেড়ে ওঠা কলকাতার অতীত সম্পর্কে স্বরূপচন্দ্র দাস লিখেছেনঃ
“পূর্বকালে ও নগর নবদ্বীপাধীন এক ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। তাতে অনেক দূর পর্যন্ত ছিল বন-জঙ্গল। এই স্থানে ১০ কিংবা ১২ ঘর কৃষিজীবী গৃহস্থ বাস করত”। (দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৩৯)
নিশীথরঞ্জন রায় জানাচ্ছেনঃ
“জলাজঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিল জেলে, শিকারি, শবর প্রভৃতি তথাকথিত জাতির নর-নারী”। (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৭)
এই গ্রাম-কলকাতার পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিল চারটি বসাক ও একটি শেঠ পরিবার। তার পাশেই সূতা ও কাপড়েরন বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুতানুটি। এই গোবিন্দুপুর-ডিহি কলকাতার-সুতানুটি গ্রাম তিনটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ১৬৯৮ সালে সাবর্ন চৌধুরীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। তারপর পাঁচ বছর ধরে সেখানে উইলিয়াম দুর্গ তৈরি করেছিল। (ভারতকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৯)।
কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদী অভ্যন্তরীন ও বহির্বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক ছিল। তার চাইতেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতার গুরুত্ব ছিল এ দেশের শাসকদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার চমৎকার আশ্রয়কেন্দ্ররূপে। জোব চার্ণক হুগলি থেকে পালিয়ে গিয়ে এই স্যাঁতস্যাতে মাটি ও জঙ্গলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নদীপথে সাগরে পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচানোর জন্যও এই কলকাতা ছিল তুলনাহীন। শক্তিশালী সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি তারা তাদের চার পাশে দাঁওবাজ দালালশ্রেণীর দ্বারা গড়ে তুলেছিল দুর্ভেদ্য ‘মানব বন্ধনী;। ইংরেজদেরকে অবলম্বন করে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে অবিশ্বাস্য রকম দ্রতগতিতে বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রণীর বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত দেড় শতাধিক বছর ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর উতরিয়ে উঠে গেছে একবারে শীর্ষদেশে, আর তাদের উত্থান-আরোহণের কার্যকরণরূপে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান প্রজাসাধারণ পতনের একটি পর একটি ধাপ গড়িয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল গভীরে। একদিকে শোষক-ধনিক-জমিদার বর্ণহিন্দুদের উত্থান, অন্যদিকে বাংলার কৃষক-প্রজা মুসলমানদের পতন, এই দু’য়েরই মধ্য-বিন্দুতে কলকাতা।
কলকাতার বাবু জাগরণ
কলকাতার লেখক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ইংরেজদের সাথে সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর লড়াইকে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষ বঙ্গ-দ্রাবিড়গণ হানাদার আর্যদের আগ্রাসন দীর্ঘদিন পর্যন্ত রুখে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের মুখে বারবার পর্যদস্ত হয়েই আর্যরা এ এলাকার দ্রাবিড় জনগোষ্ঠকে ‘অসুর’ নামে অভিহিত করেছিল। আর্যরা ‘দেবতা’ আর দ্রাবিড়রা ‘অসুর’। এই ‘অসুর’ পরিচয়েই আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘদিন আর্যদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই প্রাচীন আর্যদের অধস্তন পুরুষ ভবানী চরণ বাংলার নতুন যুগের প্রতিরোধ সংগ্রামের বীর নায়ক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ‘অসুর’ আখ্যায়িত করেছেন। তাদের চোখে পলাশীর ‘দেবতা’ হলো ইংরেজরা।
ভবানীচরণরা সিরাজকে ‘অসুর’ আর ইংরেজকে ‘দেবতা’ বলেই থেমে যাননি। মুখের কথার সাথে বাস্তব কাজের নমুনাও পেশ করেছেন। পলাশী যুদ্ধের ক’দিন পরই তারা পলাশীর দেবাসুর সংগ্রামের উপজীব্য করে বাংলায় শারদীয় দূর্গাপুজা প্রথম চালূ করেন। এর আগে বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল না। শ্রীরাধারমন রায় ‘কলকাতার দুর্গোৎসব’ নামক এই প্রবন্ধে লিখেছেন, দুর্গাপূজা’ পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎস’। ‘পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব’ হিসেবেই এই পূজা ১৭৫৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া ও কলকাতায়। এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ‘পলাশী বিজয়ী’ লর্ড ক্লাইভের সংবর্ধনা।
রাধারমণ রায় লিখেছেনঃ
“১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর রণাঙ্গনে মীর জাফরের বেইমানির দরুন ইংরেজ ক্লাইভের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটলে সবচেয়ে যাঁরা উল্লাসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র আর কলকাতার নবকৃষ্ণ। কোম্পানির জয়কে তাঁরা হিন্দুদের জয় বলে মনে করলেন। ধুর্ত ক্লাইভও তাঁদের সেরকমই বোঝালেন। ক্লাইভের পরামর্শেই তাঁরা পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব করার আয়োজন করলেন। বসন্তকালীন দুর্গাপূজোকে তাঁরা পিছিয়ে আনলেন শরৎকালে- ১৭৫৭ সালেই তাঁরা বহু টাকা খরচ করে শরৎকালীন দূর্গাপূজার মাধ্যমে পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব পালন করলেন। এরপর ফি বছর শরৎকালে দুর্গাপূজো করে তাঁরা পলাশীর যুদ্ধের স্মারক উৎসব পালন করেছেন আর অন্যান্য হিন্দু জমিদার বা ব্যবসায়ীদেরও তা পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। …… শোনা যায়, শরৎকালীন দুর্গোপূজো যে-বছর প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই ১৭৫৭ সালেই কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণ দু’জনেই লক্ষাধিক টাকা খরচা করেছিলেন। নবকৃষ্ণ টাকা পেয়েছিলেন ক্লাইভের প্রত্যক্ষ কৃপায়। …… আগে এদেশে বসন্তকালে চালূ ছিল দুর্গাপূজো আর শরৎকালে চালূ ছিল নবপত্রিকাপূজো। দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মুর্তির ব্যাপার, আর পবপত্রিকা পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নটি উদ্ভিদের ব্যাপার। পরে এই দু’টি ব্যাপারকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলা হয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে নবপত্রিকা হয়েছেন দুর্গা। তাই শরৎকালে দুর্গাপূজার বোধনের দরকার হয়। আর আগে নবপত্রিকা পূজো করে পুরো দুর্গাপূজো করতে হয়। …… তাহলে দাঁড়ালো এই : ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের বিজয়োৎসব পালন করার জন্য বসন্তকালের দুর্গাপূজোকে শরৎকালে নিয়ে এসে নবপত্রিকাপূজোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ করেছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতার নবকৃষ্ণ। আর তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন ক্লাইভ। ক্লাইভ যে উৎসাহিত করেছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে নবকৃষ্ণের বাড়িতে পূজো অনুষ্ঠানে ক্লাইভের সপরিষদ উপস্থিত। ………. নবকৃষ্ণের পুরনো বাড়ির ঠাকুর দালানটি তৈরি হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। খুবই তড়িঘড়ি করে এটি তৈরি করা হয়েছিল। … দুর্গাপূজোর চাইতেও ক্লাইভকে তুষ্ট করা ছিল নবকৃষ্ণের কাছে বড় কাজ। …. তিনি ভালো করেই জানতের, সাচ্চা সাহেব ক্লাইভ ধর্মে খ্রিস্টান, মনে মনে মূর্তি পূজোর ঘোর বিরোধী। অতএব স্রেফ দুর্গাঠাকুর দেখিয়ে ক্লাইভের মন ভরানো যাবে না, এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি ক্লাইভে জন্যে বাঈ নাচের, মদ-মাংসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই একই সময়ে একই উঠানের একপ্রান্তে তৈরি করেছিলেন ঠাকুরদালান, আকে প্রান্তে তৈরি করিয়াছিলেন নাচ ঘর।…. নবকৃষ্ণর কাছে দুর্গাঠাকুর ছিলেন উপলক্ষ, ক্লাইভ-ঠাকুরই ছিলেন আসল লক্ষ্য। দুর্গাপূজোর নামে তিনি ক্লাইভ পূজো করতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় শরৎকালীন দুর্গোৎব প্রবর্তনের সময় নবকৃষ্ণ সাহেবপূজোর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা পরে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে কলকাতার বাবুদের মধ্যে দুর্গাপূজো উপলক্ষে সাহেব পূজো নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা আরস্ভ হওয়ায়”। (রাধারমণ রায় : কলকাতা বিচিত্র, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৮; দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা)
পলাশীতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে এই উৎসব কেন? এ বিজয় কার বিজয়? তার জবান ভবানীচরণের জনানীতেই পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, পলাশীর লড়াইয়ের ফলে উঠে এসেছে ‘হর্ষের অমৃত’ আর ‘বিষাদের হলাহল’। ‘হর্ষের অমৃত’ পান করে কলকাতা হয়েছে ‘নিরুপমা ও সর্ব্বদেশখ্যাতা’। কিন্তু ‘বিষাদের হলাহল’ কাদের ভাগ্যে জুটল, সে কথা কিছুই বলেননি ভবানীচরণ। ‘দেবাসুর’ সংগ্রামের ‘বিষাদের হলাহল’ গিলতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদ আর ঢাকা শহরকে।
ভবানীচরণ লিখেছেনঃ “ধার্ম্মিক, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম-প্রবর্তক, দুষ্ট নিবারক, সৎ প্রজাপালক, সদ্বিবেচক ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর” এই দেশের লোকদের “অধিক ধনী হওনের অনেক পন্হা’ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ইংরেজ তাই দেবতা। ক্লাইভ ‘মা দুর্গার প্রতীক’। এই দেবতার পূজা করেই পলাশী-উত্তর কলাকাতাকে কেন্দ্র করে রাতারাতি একটি লুটেরা শ্রেণী রাজা-মহারাজায় পরিণত হয়েছিল। ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানার ১৮৩৯ সালের সরকারি নথিপত্র থেকে গবেষক বিনয় ঘোষ সেকালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানদের একটি তালিকা সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তুলে দিয়েছেন ‘টাউন কলকাতার কড়চা’ নামক বইতে। এই পরিবারগুলো শহর কলকাতার ‘প্রাতঃকালীন গাত্রোত্থানের’ সাথে যুক্ত। তাদের কয়েকজন হলেনঃ
১. মীর জাফরের নবাবী আমলের ক্লাইভের দেওয়ান নবকৃষ্ণের পুত্র মহারাপা রামকৃষ্ণ বাহাদুর, ২. নবকৃষ্ণের ভাতিজা বাবু গোপীমোহন দেব, ৩. কর্ণেল ক্লাইভের বেনিয়ান লক্ষীকান্ত ধরের উত্তর পুরুস রাজা রামচন্দ্র রায়, ৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুণ্ঠন-বৃত্তির কুখ্যাত সহযোগী মল্লিক পরিবার, ৫. ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রাজস্ব বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাতি বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ, ৬, গভর্নর ভান্সিটর্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান রামচরণ রায়ের উত্তর পুরুষ আন্দুলের রায় বংশ, ৭. ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ও পরে সন্দীপের জমিদার গোকুল চন্দ্র ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত খিদিরপুরের গোকুল পরিবার, ৮. হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পরিবার, ৯, ঠাকুর পরিবারের ‘জুনিয়র ব্রাঞ্চ’ বা ‘নবীন’ শাখা নামে পরিচিত এবং কোম্পানি সরকারের এজেন্ট,পরে ২৪ পরগনার কালেক্টর ও নিমক এজেন্টের সেরেস্তাদার থেকে নিমক মহলের দেওয়ান ও স্বল্পাকালীন কাস্টমস-সল্ট-ওপিয়াম বোর্ডের দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৭৯৪) পরিবার। ‘কার ট্যাগোর এন্ড কোম্পানি’র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারাকানাথের প্রভাব প্রতিপত্তির কোন প্রতিদ্বন্দী তাঁর সমসাময়িককালে ছিল না। দ্বারকানাথে ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই আমলের অন্যান্য অভিজাত পরিবার হলো- ১০. সুতানুটি বাজারের প্রতিষ্ঠাতা শেঠ পরিবার, ১১. মেসার্স ফেয়ারলি এন্ড কোং-এর দেওয়ান রামদুলাল দে, ১২. ভুলুয়া (নোয়াখালি) ও চট্টগ্রামের নিমক মহলের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাস, ১৩. পাটনার চিফ মি. মিডলটন ও স্যার টমাস রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, ১৪. কোম্পানির আমলের কলকাতার দেওয়ান গোবিন্দরামের পরিবার, ১৫. কুমারটুলির মিত্র পরিবার, ১৬. কোম্পানির ঠিকাদার গোকুল মিত্রের পরিবার, ১৭. পামার কোম্পানির সরকার গঙ্গা নারায়ণ, ১৮. পাল চৌধুরীর পরিবার, ১৯. কুলীন ব্রাহ্মণ ব্যানার্জী পরিবার, ২০. ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সরকার রামলোচনের প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবার, ২১. ক্লাইভের দেওয়ান কাশীনাথের পরিবার, ২২. কোম্পানির হুগলীর দেওয়ান শ্যামবাজারের বসু পরিবার, ২৩. কোম্পানি সৈন্যদের রসদ সরবরাহের ঠিকাদার ও কয়েকজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর বেনিয়ান এবং মেসার্স মুর হিকি এন্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীলের প্রতিষ্ঠিত কলুটোলার শীল পরিবার, ২৪. এককালের লবণের গোলার মুহুরূ বিশ্বনাথ মতিলালের পরিবার, ২৫. ঠনঠনিয়ার ঘোষ পরিবার, ২৬. মেসার্স ভেভিডসন এন্ড কোম্পানির এককালের কেরানী রসময় দত্তের প্রতিষ্ঠিত রামবাগানের দত্ত পরিবার, ২৭. পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালি সরকারের প্রতিষ্টিত কুমারটুলীর সরকার পরিবার, ২৮. আফিমের এজেন্ট হ্যারিসনের দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জীর প্রতিষ্ঠিত বাগবাজারের মুখার্জী পরিবার, ২৯. বেনিয়ান রামচন্দ্র মিত্রের পরিবার, ৩০. বিভিন্ন বিলাতি কোম্পানির সাথে যুক্ত গঙ্গাধর মিত্রের প্রতিষ্ঠিত নিমতলার মিত্র পরিবার”। (টাউন কলকাতার কড়চা, পৃষ্ঠা ৭৭-৮৮)
কলকাতার এই অভিজাত পরিবারগুলোর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,
“কেউ বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়ে, কেউ সর্দারী-পোদ্দারী করে, কেউ দাদানী বণিক ও দালাল হয়ে, কেউ বেনিয়ানী করে, কেউ বা ঠিকাদারি করে, কেউ বা ঠিকাদারি ও স্বাধীন ব্যব্সা-বাণিজ্য করে, কলকাকাতার নতুন শহুরে সমাজে নতুন বড় লোক হয়েছিলেন। সেকালের নবাবী আমলের বড়লোকরা নবযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। কোম্পানির আমলে যাঁরা নতুন বড়লোক হলেন তাঁদেরকে এক পুরুষের বড় লোক বললে ভূল হয় না”। (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১০৩)
উপরের তালিকার ‘এক পুরুষের বড় লোক’ ত্রিশটি পরিবারের সবক’টিই বাঙালি হিন্দু। তাদের অধিকাংশই উচ্চ-বর্ণজাত। মুসলিম শাসনের অব্যবহিত পরের এ তালিকা! অথচ এতে একটিও মুসলিম পরিবারের নাম নেই। এখানেও ‘চিরায়ত ঐতি্যের বিব্রতকর অনুশীলন! পাল, সেন, তুর্কী, পাঠান, মোগল শাসনামলে সকল উত্থান-পতনের রাজনৈতিক বিবর্তনে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ-উচ্চবর্ণ হিন্দুর এই সম্মিলিত শক্তিই শাসন-যন্ত্রের ছত্র-ছায়ায় সমাজে একটানা প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ইংরেজ শাসনেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।
কলকাতার বর্ণহিন্দু অভিজাত শ্রেণীটির আত্মপ্রতিষ্ঠার সে বাস্তব চিত্র বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণীকে পাওয়া যায় তা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা-চিৎপুর-বিরাজি-চক্রবেড়ি গ্রামগুলির ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকে টাউন কলকাতার দ্রুত বেড়ে ওঠার কারণ এবং ইংরেজদের দ্বারা নব্য-সৃষ্ঠ শ্রেণীটির অবাক উত্থানর কারণ সম্পর্কে এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায়।
সুপ্রকাশ রায় লিখেছেনঃ
“বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকগণের মুৎসদ্দিগিরি, লবণের ইজারা, প্রভৃতির মারফত যাহারা প্রভূত ধন-সম্পদ আহরণ করিয়াছিল, তাহারা এবং মার্ক্সের ভাষায় ‘শহরের চুতর ফড়িয়া ব্যবসায়ীগণ’ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে….. নতুন জমিদার শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই নতুন জমিদার শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্য ছিল- ইংরেজ শাসকগণের প্রতি অচলা ভক্তি…. এবং কৃষির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শহরের অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলের ভূসম্পত্তি হইতে ইজারা মারফত অনায়াস-লব্ধ অর্থবিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন এবং ‘বেনিয়ান’ লবণের ইজারাদার প্রভৃতি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বগ্রাসী ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ট সহযোগিতা। ইংরেজ-সৃষ্ট এই নতুন বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীটি আবির্ভূত হয়। দ্বারাকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রভৃতি ছিলেন এই অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য।….. সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যখন বাংলার তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন ……. (এই শ্রেণীটি) সংগ্রামরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষকের সহিত ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল”। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯)
এই লুটেরা শ্রেণীর হাতে পলাশী-উত্তরকালে তাদেরই রুচি অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল কলকাতা। সে কারণেই স্বাধীন মেজাজে মধ্যযুগে গড়ে ওঠা সোনারগাঁও, গৌড়, ঢাকা কিংবা মুর্শিদাবাদের সাথে কলকাতার কোন মিল ছিল না। একদিকে ইংরেজ কোম্পানির রাইটার-ফ্যাক্টর-সেমি মার্চেন্ট প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ কর্মচারী, অন্যদিকে তাদের লুণ্ঠন-সহচর দালাল শ্রেণী। তাদের হাতে বেড়ে ওঠা কলকাতায় জন্ম নিল এক নতুন সংস্কৃতি, যার নাম বাবু কালচার।
কলকাতার ‘বাবু’ সম্পর্কে জে. এইচ ব্রুমফিল্ড তাঁর গ্রন্হ ‘এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি’-তে লিখেছেন:
“Babu : In Bengali a title of respect for an English speaking Hindu. Applied derogatorily by the British to semi educated Bhadralok and by extension to any Bhadralok”.
‘বাবু’ শব্দটি কোম্পানির শাসনের জন্ম-স্থিতি-বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করে আবুল কাশেম চৌধুরী লিখেছেনঃ
“ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে যখন স্বাধীনতা দ্রুত অপসৃয়মান, বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ কুটীর শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য, তখনই এই সামাজিক বিকলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিচ্ছে এই বাবু সমাজ ইংরেজদের প্রত্যক্ষ আনুকূ্ল্যে।,,,,, কালো পথে উপর্জিত বাবুদের অঢেল টাকা শেষ পর্যন্ত গাতানুগতিক ভূমিমুখীন অর্থনীতিতে আটকা পড়ে এবং তার কারণে সমাজকে বিসর্জন দিতে হয় সম্ভাব্য গতিশীলতা”। (বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা : ৭২)
তিনি এই বাবু সমাজের পরিচয় আরো স্পষ্ট করে লিখেছেনঃ
“কলিকাতাবাসী জমিদার শ্রেণী যারা আভিজাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে ক্ষীয়মান সমস্ত পরিবেশকে গোঁজামিল দিয়ে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, তারাই ছিলেন ‘বাবু’। ……… এঁদের উদভ্রান্ত যৌবন কেটেছে বিদেশী বণিক শোষণে উৎক্ষিপ্ত সহজলভ্য ধনস্ফীতিতে”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫)
“কলকাতার এই ‘বাবু’দের সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি ছিল টাকা। সেই টাকার প্রাপ্তি ঘটেছে ইংরেজদের লুণ্ঠন-সহযোগীরূপে। এভাবেই তারা সারা বাংলার রক্ত শোষণ করে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল প্রাচুর্যের পাহাড়। এই কালো টাকার মালিকদের পরিচয় ছিল ইংরেজদের দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, সরকার, কেরানী প্রভৃতি শত নামে। আরো ছিল কোম্পানির উকিল ও জমিদারির সেরেস্তাদার। ইংরেজরা তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতে ‘ব্ল্যাক’ জেমিনদার’। দুর্নীতির নানা কানাগলিপথে ব্ল্যাক মানি অর্থাৎ লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছিল এদের ঘরে”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭)
এরূপ অনেক ‘ব্ল্যাক জেমিনদার’ বা ‘ক্যালকাটা বাবু’ দুই, চার, পাঁচ টাকা বেতনের কর্মচারী থেকে সে যুগের ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিল। রাম দুলাল দে পাঁচ টাকা বেতনের সরকার হিসেবে জীবন শুরু করেন। ১৮২৫ সালে মৃত্যুর সময় কলকাতা শহরে তিনি রেখে গেছের উনিশটি বিশাল বাড়ি, আর সে আমলের পৌনে সাত লক্ষাধিক টাকার সম্পদ। কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু-লাটু বাবুরা ছিলেন তারই সন্তান। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল পুরাতন শিশি-বোতলের কারবার দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। আট টাকা বেতনের চাকরি শুরু করে রামকমল সেন মৃত্যুর সময় নগদ রেখে যান দশ লাখ টাকা। হেস্টিংস-এর মুৎসুদ্দীগিরি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাসিমবাজারের রাজপরিবার, যার বার্ষিক আয় ছিল তিন লাখ টাকা। (সিরাজুল ইসলাম, সূর্যাস্ত আইনের সামাজিক তাৎপর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৮৫)
এই কালো টাকার মালিকদের পরিচয় ছিল ‘চতুর ও বুদ্ধিমান’, শঠ ও প্রবঞ্চক’, এবং ‘হাজার রকম প্রতারণা-কৌশলের উদ্ভাবক’ রূপে। টাকা-পয়সা উপার্জনে তারা যে অভিনব ব্যবসায়িক কৌশলের অবলম্বন করত তা প্রকাশ্য দস্যুতার শামিল। অন্যদিকে সেই লুণ্ঠিত সম্পদ খরচ করার ব্যাপারেও তারা ছিল বেহিসাবী। নানা প্রকার ‘বাবু বিলাস’ তখনকার কলকাতায় চালূ হয়েছিল। বাইজী-চার্চ থেকে শুরু করে বুলবুলির লড়াই, টিকটিকির নাচ পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল তাদের বিকৃত রুচির তৃপ্তি সাধনের উপাদন। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ এমনকি গৃহ প্রবেমের মতো মামুলি উপলক্ষকে অবলম্বন করে তারা আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তার মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সে যুগের প্রায় কুড়ি লাখ টাকা খরচ করেছিল। তার নাতি লালা বাবুর ‘অন্নপ্রাশন’ উপলক্ষে সোনার পাতে দাওয়াত ছেপে বিলি করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে তার ঘরে ‘পুরাণ’ পাঠ করে গঙ্গাধর শ্রীমানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পারিতোষিক পেয়েছিল হাতী, ঘোড়া ও সুসজ্জিত পাল্কি। আশুতোষ দেবের মায়ের শ্রাদ্ধ আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাপের শ্রাদ্ধ সেকালের কলকাতার বাবু-বিলাসের একেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সারা বাংলায় তখন চলছিল ইংরেজ ও তাদের দোসর এই কলকাতা-বাবুদের লুণ্ঠন-শোষণ। ইজারা চুক্তি, সূর্যাক্ত আইন, ব্যবসায়ের নামে লুটপাট প্রভৃতির ফলে একদা-সমৃদ্দ পল্লীবাংলায় দোজখের আগুন জ্বলছিল। উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষে পল্লী বাংলার প্রতি ষোল জনে পাঁচ জন লোক মারা গিয়েছিল। বাংলার পুরনো শহরগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। মানুষ মানুষের গোশত খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করছিল। দেশের শিল্প-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্বাস নিংড়ে নিয়ে কোটি মানুষের রক্ত পান করে কলকাতায় তখন চলছিল এই প্রমত্ত বাবু-বিলাস।
এভাবেই কলকাতা বেড়ে উঠল। কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দুরা লুণ্ঠন-শোষণের বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল এবং এভাবেই উনিশ শতকের আশির দশকের মধ্যে তারা ‘সবকিছু উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করে’ নিজেদের মধ্যে ‘নব জাগরণ’ সৃষ্টি করল।
কলকাতার এই নবশক্তির উত্থান সম্পর্কে স্বপন বসু লিখেছেনঃ
‘উনিশ শতকে বাংলায় শ্রেণীবিশেষের মধ্যে যে সব চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তার প্রায় সবটাই সীমাবদ্ধ ছিল বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে এ-নব চেতনার ছোঁয়া লাগল না কেন?” (বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২০৭)
স্বপন বসুর বক্তব্যেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ
“মুসলমান নবাবের হাত থেকে ইংরেজ যেদিন বাংলা অধিকার করে নিল, মুসলমান সমাজের অবনতির সূচনা তখন থেকেই। নবাব পরিবার এবং তাকে কেন্দ্র করে মর্শিদাবাদের যে মুসলমান অভিজাত-মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল ইংরেজ রাজত্বে তাদের প্রতিপত্তির অবসান ঘটল। সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে তারা পাড়ি জমালেন দিল্লী বা পারস্যে। …. রাজধানীও মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানন্তরিত হলো কলকাতায়- ফলে মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ১৫% হ্রাস পেল। নবাবী আমলে অধিকাংশ উচ্চ পদই ছিল মুসলমানের অধিকারে, ইংরেজ আসার পর শাসন-ব্যবস্থা পুরো পাল্টে গেল। মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজ রাজ্য অধিকার করেছিলেন, সেই কারণে মুসলমাদের ইংরেজরা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। এদেশে আসার অল্পদিন পরেই রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে বিন্দুমাত্র সম্বাবনা আছে জানলেই তারা তা করবে। … সামরিক বাহিনীতে যেসব মুসলামান উচ্চ পদে বহাল ছিলেন সহসা তারা অনুভব করলেন, তাদের দিন শেষ হয়েছে। সামরিক বিভাগের উচ্চ পদগুলো ইংরেজদের করতলগত হলো। অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে যেসব মুসলমান ছিলেন তাদের প্রভাব দ্রুত কমতে লাগল। ১৭৮১-তে মাগল ফৌজদারদের পদগুলোতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলো”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮)
১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি পরিণত হলো পণ্যে। বহু বনেদী পরিবার রাতারাতি হলো পথের ভিখারী। অন্যদিকে ইংরেজ দেবতার পূজা-আর্চনা করে দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী গোমস্তা শ্রেণীর লোকেরা জমিদারী কিনে হলো সামন্ত-অভিজাত। ১৮২৯ সালে বাজেয়াফত হলো লাখোরাজ সম্পত্তি। এই সব নিষ্কর জমির আয়ে পরিচালিত মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলো। সব দিক থেকেই নেমে এলো অন্ধকার। এরপর এলা রাজ-ভাষার ওপর আঘাত। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হলো অফিস-আদালতের ভাষা।হিন্দুরা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিল পুরোনো নিয়মে। কিন্তু লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, অবদমিত, ক্ষুব্ধ, হাতাশা-বিহ্বল, অভিমানাহত মুসলমানরা তখন সারা দেশে সুযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। বাঙালি হিন্দুঘরের ছেলেরা যখন ইংরেজি শেকার জন্য হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে দৌড়াচ্ছে। তখনকার মুসলমান মাত্রই ছিল লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায়- ‘মহারানীর বিদ্রোহী প্রজা’। কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু নব্য বিকশিত বাবুশ্রেণী যখন লর্ড ক্লাইভকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করছে, পল্লী বাংলায় জনগণের মধ্যে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমে পুঞ্জিভূত হচ্ছিল চাপা ক্ষোভ আর ঘৃণাৰ। রামেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেনঃ
“সারা বাংলায় ইংরেজদের অখ্যাতি এমন রটেছিল যে, একজন ইংরেজ কোন গ্রামে এলে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত, জনসাধারণও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে বাঁচত”। (দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১১২)
সাধারণভাবে পল্লী বাংলার মানুষ, আর বিশেষভাবে বাংলার মুসলমান জনগণ যখন লুণ্ঠন-শোষণের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তখন ‘হর্যের অমৃত’ পান করে জেগে উঠছিল কলকাতা। কলকাতার এই জাগরণ বাংলার রেনেসাঁ বা বাংলার নব জাগৃতি নয়। এটাকে বড় জোর কলকাতার বাবু জাগরণ বলা জেতে পারে। কিন্তু ভবানীচরণের মতো সাধারণ লেখক থেকে শুরু করে যদুনাথ সরকারের মতো পণ্ডিত ঐতিহাসিকরা সকলে মিলে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বাবুজাগরণকেই বাংলার জাগরণরূপে প্রচার করেছেন। ভেদবুদ্ধি প্রসূত মোহাচ্ছন্নতায় এদের মধ্যে কোন ফারক নেই। ভবানীচরণ পলাশীর যুদ্ধকে বলেছেন. ‘দেবাসুর সংগ্রাম’, আর যদুনাথ সরকারে ভাষায়, তা ‘এক যুগান্তকারী ঘটনা’। ভবানীচরণ পলাশী যুদ্ধের ফলে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল’ এবং পলাশীতে ইংরেজ বিজয়ের ফলে ‘মধ্য যুগীয় ধর্মীয় স্বৈরাচারী শাসনের’ অবসান হয়েছিল। যদুনাথের মতে, ইংরেজ আমলে পশ্চিমা সভ্যতার পরশে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে জড়তা দূর হয়ে শুরু হয় নব জীবনের স্পন্দন। ‘ভগবানের দান এক যাদুকরের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায়’ যেন স্থবির প্রাচ্য সমাজে সঞ্চার হয় রেনেসাঁ বা নব জাগৃতি। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলার রেনেসাঁ তার চাইতেও ‘ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্লবিক”। (হিস্টি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৯৮)
যদুনাথ সরকার-এর এই পর্যবেক্ষণ ও মতামত সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম লিখেছেনঃ
………. পলাশীর পরাজয়ের মধ্যে তিনি (যদুনাথ সরকার) যে যুগান্তকারী সুফল লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে নেহাতই একজন মস্তিষ্কস্নাত রাজভক্ত ঔপনিবেশিক ঐতিকাহাসিকের তথ্যশূন্য ভাবোদগার ও মনগড়া কল্পনা মাত্র। ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে সর্বপ্রথম কোম্পানির সরকার দেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদানের নামে একটি মাত্র শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। এর পূর্বে পৌনে একশত বৎসর যাবত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকাতার অভাবে হাজার হাজার মোগলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বন্ধ প্রায় হয়ে যায়। ফলে দেশ নিপতিত হয় অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মহা তিমিরে। এটা কি রেনেসাঁ? ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে এসে দেশীয়দের সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল উচ্চপদ লাভের বাধা উত্তোলন করা হয়। এর পূর্বে শত বৎসর যাবৎ সমস্ত দায়িত্বশীল উচ্চ বেতনের সরকারি চাকরি ছিল একচেটিয়া ইউরোপীয়দের জন্য রিজার্ভ। চাকরিহারা দেশের অগণিত পেশাদার পরিবার বেকার হয়ে নিঃস্ব নিস্তেজ সামাজিক বোঝায় পরিণত হয়। উত্তরোত্তর জনবহুল শহর, বন্দর, আর লয়প্রাপ্ত হয়ে পুঁতিগন্ধময় নোংরা জঞ্জালে পরিণত হয়। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে মৃত্যু ও পলায়নের ফলে নাগরিক লোকসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ইহা কি রেনেসা? বাংলার যে বস্ত্র ও রেশম-শিল্ল ছিল একদা বিশ্বনন্দিত সে শিল্পের পতন ঘটে পলাশীর যুদ্ধের পর। বাংলাদেশ পরিণত হয় গ্লাসগো-ম্যানচেস্টারের বন্দীবাজারে (captive market)। ইহা কি রেনেসাঁ? কোম্পানির ভূমি-রাজস্বনীতির ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় অনার্জিত আয় ভক্ষণকারী উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন একটি সুবিধাভোগী জমিদার ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণী। রায়ত ভূমিতে চিরাচরিত অধিকার হারিয়ে পরিণত হয় জমিদারের করুণাপ্রার্থী প্রজায়। ইহা কি রেনেসাঁ? এসবই পলাশী যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের সুদূর প্রসারী ফল”। (বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩০-৩২)
একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য এটি অবশ্যই রেনেসাঁ ছিল। শ্রেণী পরিচয়ে তারা সামন্ত, ব্যবহারিক পরিচয়ে জমিদার, আর আভিজাত্যের কল্যাণে কলকাতার মানসপটে এর ছিল বাবু নামে পরিচিত। রাজনীতিতে এরা ইংরেজদের বংশবদ দালাল, কিন্তু জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনের তারাই ছিল প্রকৃত নিয়ন্তা। পলাশীর প্রানতরে বাংলার নবাব মসনদ হারিয়েছিলেন আর এই নবোত্থিত বর্ণহিন্দুরা পেয়েছিল অনেক শ্বেতাঙ্গ নবাব। তাদরে জন্যই পলাশীর পরাজয় এনেছিল নব জাগৃতি বা রেনেসাঁ। এই জাগৃতি বাংলার জাগরণ নয়, এটি নিতান্তই ছিল কলকাতার ‘বাবু জাগরণ’।
উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের সূচনা থেকে একদিকে সরা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, অন্যদিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দখল সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তারা শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় জীবনের দিকেও থাবা বিস্তার করেছিল। বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে নতুন বাংলা গদ্যধারার বিকাশ ঘটে। কলকাতাকেন্দ্রীক সদ্য বিকশিত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এ কাজে পরম উৎসাহে অংশ নেন। জনগণের মুখের ভাষার আদলে গড়ে ওঠা বাংলাকে বর্জন করে, সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী ছাঁচ বাঁচিয়ে তারা এক নতুন গদ্যভাষা নির্মঅণ করেন। ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে নন্দনকুমার, জগতধীর রায়ের সাহিত্যে মুসলমানের যবানী ভাষার যে প্রভাবটুকু ছিল, তা-ও তারা পরম যত্মে ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলেন। এভাবেই খ্রিস্টান পাদ্রী ও তাদের জুনিয়র পার্টনার বর্ণহিন্দু পুরোহিতদের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার চেহরা বদলে গলে। মৃত সংস্কৃত ভাষা গৌরব লাভ করল একটি জীবন্ত, চলিষ্ণু ভাষার ‘জন্মদায়িনী’রূপে, আর বাংলা ভাষার পরিচয় ঘটল ‘সংস্কৃতের দুহিতা’ নামে। বাংলা ভাষার এই মোড় পরিবর্তনের কার্যকরণ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় : ‘পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়’।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেনঃ
“বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হলো বৈদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধর হলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ”।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ‘বৈদেশীর ফরমাসে’‘সংস্কৃত সূত্রধর’দের দ্বারা করাত-চেরা হয়ে যে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা গদ্যের সূচনা হলো, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সে ভাষায়ই তখন থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্রে মাসিক ‘দিগদর্শন’ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিলে। সম্পাদক একজন ইংরেজ পাদ্রী। নাম জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তাঁরই সম্পাদনায় মাত্র এক মাস পর প্রকাশিত হয় আরো একটি সাময়িকপত্র- ‘সমাচার দর্পন’, ১৮১৯ সালের ডিসেম্বরে। কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি প্রকাশ করে একটি ইংরেজি-বাংলা দ্বি-ভাষিক মাসিকপত্র ‘গসপেল ম্যাগাজিন’। ১৮২২ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় ‘খ্রিস্টের রাজ্যবৃদ্ধি’। খ্রিস্টধর্মের বানী প্রচারের প্রেরণা নিয়ে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো সাময়িকপত্রের জন্ম একটি লক্ষণীয় বিষয়। ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের সাফল্যকে অবলম্বন করে এভাবে তাদের ধর্ম-কৃষ্টির বিজয় অর্জনের হাতিয়ারূপেই এ সকল সাময়িকপত্র চিহ্নিত।
খ্রিস্ট ধর্মের বাণীবাহী এসব সাময়িকপত্রের পাশাপাশি এ সময় থেকেই হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রচার, হিন্দু সমাজের সংস্কার ও হিন্দু ধর্মীয় পনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মুখপত্ররূপে বিভিন্ন সাময়িকপত্র প্রকাশ পেতে থাকে। এগুলোর মধ্যে ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ (১৮১৮), ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ (১৮২১), ‘সম্বাদ কৌমুদী’ (১৮২১), ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ (১৮২২) সাপ্তাহিক ‘শাস্ত্র প্রকাশ’ (১৮৩০), ‘সংবাদ প্রভাকর’ (১৮৩১), ‘সম্বাদ সুধাকর’ (১৮৩১) প্রভৃতি পত্রিকা বর্ণহিন্দুদের প্রকাশিত প্রথম যুগের সাময়িকপত্ররূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজদের দেওয়ানী, বেনিয়ানী, মুৎসুদ্দীগিরি, ঠিকাদারি ও অন্য আরো অনেক প্রকার দালালি করে কলকতাকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ঘটে; তাদের জীবনে আসে রেনেসাঁ বা নব জাগতি। ফলে তাদের হাতে এই নতুন গণ-মাধ্যমটি নানা রূপ-বৈচিত্র্যে পল্লবিত হয়ে ওঠে।
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একশ’ বছর ধরে বাংলার মুসলমানগণ ছিলেন বিদেশী বেনিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধরত। তখন বর্ণ-হিন্দুরা নযীরবিহীন দালালির মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার বর্ণ-হিন্দু মধ্য-শ্রেণীটি ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ এই শ্রেণীটির নেতৃত্বেই বর্ণহিন্দুদের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এই রেনেসাঁর নায়ক। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলো। ১৮৩৯ সালে রামমোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ‘রাজা’ উপাধি নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে রাজ-দরবারে আবেদন জানালেন রাষ্ট্রভাষা ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি চালুর জন্য। ১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালুর ফলে মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকরির দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় বাংলায় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের পতাকাতলে বাংলার মুসলমানরা একদিকে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, অন্য দিকে হিন্দু জমিদাররা ১৮৩৭ সালেই প্রতিষ্ঠা করে ‘বেঙ্গল-ইন্ডিয়া সোসাইটি’। সারা ভারত জুড়ে যখন ইংরেজ উৎখাতের বিপ্লবী প্রস্তুতি চলছে তখন ১৮৫৩ সালে হিন্দু জমিদাররা প্রতিষ্ঠা করে ‘বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস এসোসিয়েশন’। আর ১৮৫৬ সালে কলকাতার নব-উত্থিত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ইঙ্গ-হিন্দু স্বার্থের দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন’।
সিপাহী বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির সুযোগে নবোত্থিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীটি ব্যাপকভাবে ইংরজ প্রশাসনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-স্বার্থপরতা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-লোলুপতায় রূপ পেতে থাকে।
উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার, কর্ণেল টড প্রমুখ ইংরেজ লেখকের চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ও প্রাচীন হিন্দু-ঐতিহ্যভিত্তিক রচনাসমূহকে উপজীব্য করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয়। এভাবেই তাদের ধর্মীয় জাতীয়তারও সূচনা হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-চেতনার ভিত্তিতে তাদের জাতীয় মানস গড়ে উঠতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু, ননীগোপাল মিত্র প্রমুখ এই নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাণীবাহকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখক মুসলিম শাসনকে নির্বিচারে ‘অত্যাচারী শাসন’ বলে আখ্যায়িত করেন। তারা ইংরেজ শাসনের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে যেসব রাজপুত, মারাঠা ও শিখ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তাদেরকে এই লেখকরা বীরের মর্যদায় অভিষিক্ত করেন। এই অভিন্ন ধারার অনুসারী বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লেখকরা হিন্দুদের হিন্দুয়ানী রক্ষার জন্য ‘নেড়ে দেড়ে যবনদের বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিবার’ উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৃহদংশ জুড়ে বিপন্ন মুসলমানদেরকে একেবারে কর্দমে পুতে ফেলার আহ্বান প্রচার হতে থাকে। মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের পাশাপাশি হিন্দুরা একদিকে ইংরেজ তোষণ অন্য দিকে নিজ সম্প্রদায়ের জাগরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি-সংগঠন কায়েম করতে থাকেন।
উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীটির পরিচয় দিয়ে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেনঃ
“ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গ সমাজ ছিল প্রধানত দুইটি মূলশ্রেণী লইয়া। ইহাদের একটি ইংরেকসৃষ্ট ভূস্বামী গোষ্ঠী এবং অপরটি কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক সম্প্রদায়। ……… তৎকালের বিপুল কারিগর সম্প্রদায়ও কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ শাসনের কৃপায় জমিদার শ্রেণী সমাজ-শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভূমির পত্তনি-ব্যবস্থার মারফত জমিদার শ্রেণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ (তালুকদার) মধ্যশ্রেণীটিও জমিদারদের সহকর্মীরূপে সমাজের উচ্চ সীমায় আরূঢ় হইয়াছিল। ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতি এই সমবেত ভূস্বামী গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হওয়ায় সমাজের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইহারা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। …. ইহাদের জাতীয় চৈতন্য মোহাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যখন বাংলার তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশ, বিশেষত প্রতক্রিয়াশীল অংশ সংগ্রামরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল”। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৯)
এই মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায় এই আন্দোলনের জনক। এটি ছিল নব্যসৃষ্ট জমিদারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রামমোহন রায় এই আন্দোলনের জনক। এটি ছিল নব্যসৃষ্ট জমিদারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকোনন্দ- এরা সবাই এই রেনেসাঁর নায়ক এবং ‘কৃষক সংগ্রামের ভয়ে ভীত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর’ প্রধান মুখপাত্ররূপেই তাদের মূল পরিচয়। বর্ণহিন্দু জাগরণের এই নায়করা উনিশ শতকে যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করেন, তা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতি বলতে তারা বুঝতের হিন্দু জাতি। তাদের আদর্শেই কলকাতার বর্ণহিন্দু নেতাদের পরিচালনায় বিকাশ লাভ করেছে বিশ শতকের জাতীয় আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় আন্দোলন ছিল মুলত হিন্দু জাতীয় আন্দোলন। কেননা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির নামে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যা কিছু আলোড়ন, তার অবলম্বন ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের বাণী।
উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীটি ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই উঠতি বর্ণহিন্দুদের পাশ্চাত্যমুখী প্রবণতা কেটে যেতে থাকে। তার পরিবর্তে সেখানে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ও ধর্মের প্রতি জেগে ওঠে নতুন আকর্ষণ। শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের মাঝে হিন্দু দর্শন, হিন্দু সাহিত্য ও হিন্দু শিল্পের প্রতি একটা গর্বের ভাব জেগে ওঠে। ক্রমশ প্রাচীন হিন্দু-ধর্মীয় আদর্শ অব্যাহত রাখার জন্য নতুন নতুন সংগঠন কায়েক হয়। এগুলো সনাতন হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকে। এই সামাজিক পরিবেশে হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবনের প্রধান নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হিন্দু মধ্যশ্রেণীর কাছে হিন্দু ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘নব্য হিন্দুবাদ’ প্রচারের মাধ্যমে সনাতন হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবনের যে কাজ শুর করেছিলেন, বিবেকানন্দ তা বহুদূর এগিয়ে নেন। তার শিক্ষাকেই বর্ণহিন্দুরা তাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। এই জাতীয়তাবাদের মূল কথা ছিলঃ
“স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ, হিন্দু আদর্শের পুনরুত্তান এবং ভারতীয় প্রাচীন আধ্যাত্মিক ধারণার সমষ্টিবদ্ধ রূপ”।
বিপিনচন্দ্র পালের মতো হিন্দু জাতীয়তাবাদের চরমপন্হি প্রবক্তাগণও বিবেকানন্দকেই তাদের রাজনৈতিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।
১৯০১ সালে বিবেকানন্দ ঢাকা এলে তাঁর সাথে এখানকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের লোকদের ঘনিষ্ট আলোচনা হয়। সে আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং ভারতকে রাম-রাজত্বে পরিণত করার ব্যাপারে বল প্রয়োগের নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ
“……… প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া তরুণ বাংলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর-সাধনা এমনকি ভগবতগীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুঃসাহসিক নেশা-পৌরুষ, তেজস্বিতা, অর্থাৎ বীরনীতি দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য। …… হে বঙ্গের তরুণ দল, তোমরা ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈদের আদর্শ অনুসরণ কর। …. জনগণের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্হাগার প্রতিষ্ঠা কর। বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁদের দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুসরণ কর”। (ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বামী বিবেকানন্দ- পেট্রিয়ট এন্ড প্রফেট)
বিবেকানন্দ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেনঃ
“তথাকথিত সমাজবাদী স্বামীজির মতে…… ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনৈতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য এই ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দু ধর্মের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্তিত নব হিন্দুবাদেরই প্লাবন তা বলাই বাহুল্য’। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২১৭)
১৮৫৩ সালে কলকাতায় অবিভক্ত বাংলার বনেদি হিন্দু জমিদারদের উদ্যোগে বেঙ্গল ল্যান্ডলর্ডস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এরপর কলকাতার বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী জমিদার ও বণিক শ্রেণীর উদ্যোগে তাদের স্বার্থ রক্ষার দুর্গরূপে ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এই সমিতির সকল সদস্য ছিলেন ইংরেজদের দ্বারা সদ্য-সৃষ্ট জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনিক গোষ্ঠীর লোক। অভিজাত ও জমিদার ছাড়া অন্যদের এই সমিতিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই সমিতির সদস্যরাই আইন সভার সদস্য হতেন। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এই সমিতির ৩ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য হয়েছেন। তাঁরাই দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও পশা বিষয়ক স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এ বিষয়ে আব্দুল মওদুদ লিখেছেনঃ
“তাদের মধ্যে ঠাকুর বংশই ছিল অগ্রগণ্য। বিশাল জমিদারি, বিপুল ব্যবসায় ও অফুরন্ত ধনসম্পদের অধিকারী হিসেবে এই বংশটির ঐতিহ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা মুখরিত। প্রিন্স দ্বারকানাথের ভ্রাতা মহারাজা রমানাথ ঠাকুর এই সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন দশ বছর এবং ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার ও ১৮৭৩ সালে ভারতীয় বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী নেতা হিসেবে এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সভ্য হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সরকারি ও অন্যান্য সূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও ১৮৬৩ সালে বঙ্গীয় বিধান সভঅর সভ্য হন। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার ও ১৮৭৭ সালে ভারত বিধান সভার সভ্য হন। সামান্য বেনে-নন্দন রামগোপাল ঘোষ বাণিজ্যলব্ধ অর্থবলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স শিক্ষা সভার ১৮৪৫ সালে ও বঙ্গীয় বিধান সভার ১৮৬২ সালে সভ্য হন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন উপরিউক্ত এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সভ্য এবং ব্রিটিশ সাহায্য ও অনুগ্রহ-ধন্য কলকাতার নব্য ‘রইস”। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৬৮)
১৮৬৬ সালে কলকাতার বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও ইংরেজ রাজশক্তিকে মদদ যোগানোর লক্ষ্যে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’ কায়েম হয়। এই সংস্তাটির অনুষ্ঠান-পত্রে ‘হিন্দু ব্যায়াম’, ‘হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা’ ও ‘হিন্দু শাস্ত্র’ অবলম্বনে সমাজ সংস্কার করার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের ভিত্তিতে ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল (বাংলা ১২৩৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিন) বেলাগাছিয়ায় ডানকান সাহেবের বাগানবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্শীবাদে জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রমুখের উদ্যোগে ‘হিন্দু মেলা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণহিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে আত্মানির্ভরশীল করা এই মেলার লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ বার এই মেলায় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতাকেন্দ্রক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াগুলো ‘আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে, আদায়ের লক্ষ্যে পদচ্যুত প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন’ বা ‘ভারত সভা’।
১৮৮২ সালে ভারতীয় বিধান সভায় ‘ইলবার্ট বিল’ নামে একটি বিল পেশ হয়। এই বিলে বিধান ছিল, দেশীয় হাকিমদের কাছেও ইউরোপীয়দের বিচার হতে পারবে। ইউরোপীয়রা এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুর করে। এই আন্দোলন অন্যায় জেনেও ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করে এবং বিলের উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। হিন্দু মধ্যবিত্তরা এই বিলের পক্ষে আন্দোলন করে। ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত জটিলতাকে কেন্দ্র করে ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স স্থাপিত হয়। অবশেষে ইংরেজ প্রাক্তন সিভিলিয়ান এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর উদ্যোগে এবং গভর্নর জেনারেল ডাফরিনের পরামর্শে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বে শহরে এক বৈঠকের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। এ বিষয়ে রজনী পাম দত্ত লিখেছেনঃ
“প্রকৃতপক্ষে বড় লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধে শক্তি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার অস্ত্ররূপে”। (ইন্ডিয়া টুডে)
১৮৮৬ সালে ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স’ জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যশ্রেণী এভাবেই উনিশ শতকের আশির দশক নাগাদ একটি বিকশিত স্তরে উন্নীত হয়। আবদুল মওদুদ এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ
“এই আমলে আমরা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখেছি, পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যেসব উপহার এসেছে সে-স তারাই উজাড়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, নতুন ভাবধারা গ্রহণ করে আত্মীকরণ করেছে এবং সম্প্রসারণও করেছে। সারা উপমহাদেশের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একত্রিত এবং সংহত করেছে। নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষ তাদের একটা সাধারণ ভাষা দিয়েছে, সাধারণ ভাবধারা দিয়েছে এবং সাধারণ জ্ঞানও দিয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক ট্রাডিশনের পাশাপাশি। নতুন প্রেসও বহির্বিশ্বের ভাবধারা ও কর্মধারার সংস্পর্শে এনেছে এদেশবাসীকে এবং তার প্রতিক্রিয়াও সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাদ্রাজ দিল্লীর সঙ্গে যখন-তখন কথা বলছে, বোম্বাই বলছে কলকাতার সঙ্গে। এভাবে নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তনের পর ইলবার্ট বিল উপস্থাপিত হওয়ার সময় (১৮৮২) পর্যন্ত পাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে হিন্দু সমাজ-দেহের মধ্যম স্তর থেকে এমন একটা সুসংহত একই স্বার্থডোরে জড়িত শ্রেণীর উদ্ভব হলো, যারা সর্বভারতে একই শিক্ষা, একই ভাবধারা ও একই মূল্যবোধ প্রবর্তিত ক করল নিজেদের গণ্ডির মধ্যে। অবশ্য এ শ্রেণী ছিল বিরাট সমাজ-দেহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও তেজোদ্দীপ্ত ও বিস্ফোরণ-উন্মুখ। এটিকে বলা যায় হিন্দু ভারতের নতুন আত্মা এবং এই নতুন আত্মার মুখেই অতঃপর হিন্দু ভারতের প্রাণের বাণী শোনা যেত এবং সে বাণী সমগ্র হিন্দু জাতির অন্তরের কথা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করত”। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩)
১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণিহিন্দু ও মারাঠা ব্রাহ্মণদের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের এক সেতুবন্ধ তৈরী হয়। মহারাস্ট্রে স্থাপিত দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের সমর্থক মারাঠা ব্রাহ্মণ ও কলকাতার বর্ণহিন্দুরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষে শাসকগোষ্ঠীর সাথে চরম বোঝাপড়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এ সময়। এম আর আখতার মুকুল এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ
“বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় এলাকার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা যখন দিনে স্যুট-প্যান্ট আর সন্ধ্যায় ধুতি, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের সেতুবন্ধ রচিত হলো। এই সম্প্রদায়ের চোখে তখন ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন”। (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)
কলকাতার বর্ণহিন্দুদের চিন্তা-ভাবনার স্তরে স্তরে এ সময় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা ডালপালা বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে ডক্টর পুলিন দাশ লিখেছেনঃ
“১৮৬৬ সালে ব্রাহ্ম সমাজ দু’ভাগ বিভক্ত হয়ে এক ভাগ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও অপর অংশ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে চিহ্নিত হয়। …… দেবেন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক’ বিখ্যাত বক্তৃতা দেন (১৮৭২)। ‘বংদগদর্শন’- বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রাজনারায়নের বক্তৃতার উচ্ছাসিত প্রশস্তি প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রকেও দেখা যায় হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়ন ও অলোচনায় নিবিষ্ট হতে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘প্রচার’ পত্রিকা হিন্দু ধর্মের প্রচারমাধ্যম হয়ে ওঠে। দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ (১৮৭৫) আন্দোলন হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বেদকে অভ্রান্ত গণ্য করে দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অতঃপর দয়ানন্দ প্রবর্তিত মতবাদের অনুপ্রেরণা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘প্রচার’-এর সঙ্গে বাংলাদেশের আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে ‘বংগবাসী’, ‘নবজীবনী’ হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। …. বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আকৃষ্ট হন। বঙ্গদেশের শিক্ষিত সাধারণের কাছে দয়ানন্দ পরিচিত হয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে। ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ ও ‘সুলভ সমাচার’ পত্রে প্রধানত কেশবচন্দ্রের রচনা-ধারার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমা প্রকাশ পেতে থাকে। হিন্দুর যে পৌত্তলিকতা নব্য শিক্ষিতদের দ্বারা সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়েছিল, রামকৃষ্ণ ছিলেন সেই পুতুল পূজারী। গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্র সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন মার্গী বহু গুণীজনের শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃষ্টান্তে পৌত্তলিক হিন্দুর আত্মপ্রসাদ লাভের যথেষ্ট সুযোগ মিলল”। (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক)
এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেনঃ
“ঊনবিংশ শতাব্দীর আট দশকের সূচনায় হিন্দু পুনরুত্থানের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত চাতুর্যে এতদিন ধরে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আপ্লুত রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু ধর্মরূপী যে চারাবৃক্ষে জলসিঞ্চন করছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে কলিকাতায় সখারাম গণেশ দেউঙ্কর আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে সকলের দৃষ্টিগোচর হলো। আসলে এটাই হচ্ছে বঙ্গীয় এলাকার শতাব্দীকালের বিষবৃক্ষ। … ঊনবিংশ শতাব্দীর আট দশকে কলিকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ‘উদার ও সংস্কারপন্হি মন-মানসিকতা’ উচ্ছিষ্টের মতো নর্দমায় নিক্ষিপ্ত করেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে মেকলের ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে যুক্ত হলো ‘সনাতন হিন্দু ধর্মের’ শ্রেষ্ঠত্ব, আর ‘হিন্দু বাহুবলের আবরণ”। (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)
উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু লেখকরা হিন্দু পুনর্জাগরণমূলক কবিতা, গান আর নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে রাজপুতদের সাথে মোগল বিরোধকে উপজীব্য করে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। লে. কর্নেল জেমস টড-এর রচিত ‘এনালস এন্ড এন্টিকস অব রাজস্থান’ নামক বইটি ছিল শত বছর ধরে হিন্দু লেখকদের অবলম্বন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যে চারণ গীতিকে ‘আফিমখোরদের গাল-গল্প’ বলে অবহেলা করেছেন, টড-এর তা-ই ছিল উপজীব্য। মোগলদের সাথে রাজপুত জাতির আত্মরক্ষামূলক ও সমঝোতামূলক লড়াইকে ঘিরে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় মনে করে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তি এসে হিন্দু লেখকরা নযর ফেরালেন মারাঠা দস্যু ‘পার্বত্য মুষিক’ ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি। শিবাজীর ব্যক্তিত্ব, শোর্য-বীর্যের কাহিনী ও বীরগাঁথা অবলম্বনে এ সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর নেতৃত্ব নিলেন কংগ্রেসের চরম দক্ষিণপন্হি নেতা মারাঠা-ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৩ সালে তিনি ‘গণপতি উৎসব’ প্রবর্তন করলেন। তার উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ১৮৯৬ সালের ১৫ এপ্রিল ‘শিবাজী উৎসব’-এর আয়োজন করা হয়। এর পরের বছর পুনা শহরে বিপুল উৎসাহ- উদ্দীপনার মধ্যে তিনদিনব্যাপী শিবাজী উৎসব পালিত হয়। তিলক ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবেরও প্রচলন করেন। শিবাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। তাই ভবানী পূজা শিবাজী উৎসবের মূল অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। মারাঠাদের অনুসরণে ১৯০২ সাল নাগাদ কলকাতায় শিবাজী উৎসবের সূচনা হলো। এর পরেই বাংলা সাহিত্য, নাটক, কবিতা আর গানগুলো ছত্রপতি শিবাজীর জয়গানে মুখরিত হলো। বাঙালিত্বের নামে হিন্দু বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু রিবাইভালিজম-এর মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু জাতীয়তা প্রতিষ্ঠাই ছিল তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রায় সকল বর্ণহিন্দুর অভিন্ন লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ড. প্রভাকুমার গোম্বামী ‘দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক বাংলা নাটক’ বইয়ে তখনকার অবস্থা চিত্রিত করে লিখেছেনঃ
“মোগলের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংগ্রামের কাহিনী যেমন আমাদের দেশাত্মবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী। শিবাজীকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে উঠেছে। চার বছর ধরে শিবাজী উৎসব চলছিল কলকাতা শহরে। চরমপন্হি স্বাদেশিকরা বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হলো তার অঙ্গ স্বরূপ ছিল ভবানী পূজা। শিবাজী উৎসবে ভবানী মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালূতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শীবাজীকে ‘জাতীয় বীর’ রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল”।
৭
বাংলায় জন-বিদ্রোহ
ইংরেজ কোম্পানি এবং তার এ দেশীয় দালাল শ্রেণীর সর্বাত্মক নিপীড়ন, নির্যাতন ও লুণ্ঠন-শোষণের মুখে বাংলার মুসলমানদের সামনে পথ ছিল দু’টি : অনিবার্য ধ্বংসের কাছে আত্মসমর্পণ; কিংবা বিদেশী দখলদার ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটরদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম। দ্বিতীয় পথটি ছিল মুসলমানদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত-পিচ্ছিল রাজপথে তাই শুরু হয় তাদের পথ চলা।
পলাশীর পতনের ছয় বছরের মাথায় ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহের সূচনা করেন ফকির মজনুশাহ। আযাদী পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির এই প্রথম গণসংগ্রাম ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। এ সময় থেকেই একের পর এক সংঘটিত হয় ত্রিপুরা জেলায় শমশের গাযীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দীপে আু তোরাবের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম-চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৯), রংপুর-দিনাজপুরে নূরলদীনের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), ফকীর বোলাকী শাহের নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯২), মোমেনশাঞী ও জাফরশাহী পরগণায় জমিদার-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), হাজী শরীয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ববাংলায় ফরায়েজী আন্দোলন (১৮১৮-৭০), উত্তরও পশ্চিমবঙ্গে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অনুসারীদের জিহাদ আন্দোণ ও তিতুমীরের নেতৃত্বে জিহাদপন্হি কৃষক বিদ্রোহ (১৮২১-১৮৭০), সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭), সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), টিপু পাগলার নেতৃত্বে পাগলপন্হি গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-৮২) ইত্যাদি। লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায়, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশ’ বছর পর্যন্ত মুসলমান মানেই ছিল ‘রাণীর বিদ্রোহী প্রজা’।
ফকীর ও কৃষক বিদ্রোহ
পলাশীর বিপর্যয়ের ছয় বছরের মাথায় মীর কাসিমের নেতৃত্বে দেশীয় সৈন্যগণ যখন ১৭৬৩ সালে পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধরত, বাংলা ও বিহারের ইংরেজ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে সে সময় বিদ্রোহের ঝান্ডা তোলেন ফকীর মজনু শাহ। বেতনভুক সৈনিকদের শক্তির ওপর ভরসা করে পরিচালিত মীর কাসিমের সংগ্রাম অল্প সময়ের মধ্যে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকীর বিদ্রোহ নামে পরিচালিত এদেশের প্রথম জন বিদ্রোহ প্রায় চার দশক ধরে অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয় এবং দেশের জনগণের মধ্যে অধিকার ও আযাদীর দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তোলে। মাত্র হাজার খানেক লোক নিয়ে মজনু শাহ বিদ্রোহের সূচনা করেন। কয়েক বছরে তাতে বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। জমিহারা-গৃহহারা নিরন্ন চাষী, দিন মজুর, শিল্প ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা থেকে বঞ্চিত কারিগর, বেকার তাঁতী, চাকুরীচ্যুত বুভুক্ষু সৈনিকসহ সকল স্তরের মানুষ শরীক হয় এই বিদ্রোহে। আযাদী পুনরুদ্ধার, ঈমানের হেফাযত এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণ মুক্তির এই সংগ্রাম ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশির ভাগ সময় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা ও মোমেনশাহী এবং মাঝে মধ্যে ঢাকা ও সিলেটে বিদ্রোহীদের অভিযান পরিচালিত হয়। একেকটি অভিযানে কখনো কখনো কয়েক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী অংশ নিতেন। ১৭৬৩ সালে ইংরেজদের ঢাকা কুঠি হামলার মধ্য দিয়ে এ বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কৃষক ও কারিগরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সমগ্র বাংলা ও বিহার কিছুদিনের মধ্যেই মহাবিদ্রোহের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই বিদ্রোহ সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ রাজত্বের জন্য এবং তাদের নব্যসৃষ্ট দালাল জমিদার গোষ্ঠীর জন্য মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা বিভিন্ন স্থানের ফকীর বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বারাবার পরাজিত হয়। দালাল জমিদাররা তাদের এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীদের তৎপরতার ফলে কোন কোন অঞ্চলে রাজস্ব আদায় কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের কাচারী বারবার লুণ্ঠিত হয়। ফলে ঐসব স্থানে ইংরেজদের রাজস্ব ঘাটতি ও জমিদারদের অথসংকট দেখা দেয়। ইংরেজ ও মজনু শাহের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষকালে গ্রামবাসীরা অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং পলায়নপর ইংরেজ সৈন্যদের হত্যা করে তাদের অস্ত্র মুক্তি সংগ্রামীদের হাতে তুলে দিয়েছেন।
১৭৮৬ সালে ১৯ ডিসেম্বন মজনু শাহ ইংরেজ সেনাপতি ব্রেনানের সাথে এক যুদ্ধে আহত হন। এরপর ১৭৮৭ সালের মার্চ কিংবা মে মাসে তিনি ইনতেকাল করেন। মজনু শাহ-এর আসল নাম ও প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত। ইংরেজদের চোখ এড়ানোর জন্যই তিনি মজনু (পাগল) শাহ নামের আশ্রয় নিয়েছেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তাঁর পরিচয় বাকের মুহাম্মদ বা নূরউদ্দীন বাকেরজঙ্গ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। মজনু শাহের প্রধান সাথীদের মধ্যে ছিলেন চেরাগ আলী শাহ, ফেরাগুল শাহ, সুবহানী শাহ, করম শাহ, মাদার বখশ, জরিফ শাহ, রমযান শাহ ও রওশন শাহ। মজনু শাহের মৃত্যুর পরও চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তাঁরা এই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।
ফকীর বিদ্রোহের সমসাময়িককালে ১৭৬৭-৬৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় শমশের গাজী বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। ১৭৬৯ সালে সন্দ্বীপ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন আবূ তোরাব। ১৭৭৫ সালে মোমেনশাহীর সুসংগ ও শেরপুর জমিদারী এলাকায় ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এক যুগেরওর বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষীদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন শের দৌলত খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখশ খাঁ। ১৭৮৩ সালে দিনাজপুরে কোম্পানির ইজারাদার ‘রাজা’ দেবী সিংহ ও তার ‘দেওয়ান’ হরেরামের বিরুদ্ধে নুরুলদীনের নেতৃত্বে পরিচিালিত হয় কৃষক বিদ্রোহ। ১৭৯২ সালে ফকীর বোলাকী শাহের নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জে কৃষকদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এভাবে একটির পর একটি গণবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পলাশী বিপর্যয়ের মসীলিপ্ত ইতিহাস রক্ত রঞ্জিত, গৌরবময়, উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।
১৭৯৮ সালে ফতেহ আলী টিপু মহীশূরের আযাদী হেফাযত করার জন্য যখন জীবন বাজী রেখে লড়াই করছিলেন এবং ইংরেজ শাসকদের জন্য এক ভীতিকার অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় তখন মজনু শাহের অনুসারীগণও আযাদী সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। আর তখন ইংরেজদের এই বিপদের দিনে কলকাতাকেন্দ্রিক সদ্য বিকশিত বর্ণহিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীটি বিদেশী কোম্পানি শাসনের প্রতি তাদের প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা করে ইংরেজদের সন্ত্রস্ত মনে সাহস বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। ১৭৯৮ সালের ২৯ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত এরূপ একটি সভায় কলকাতার নব্যসৃষ্ঠ ধনিক গোষ্ঠীর প্রতিভূ গৌরচন্দ্র মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, গোপিমোহন ঠাকুর, কালিচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকূল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা এক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ও সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ১৭৯৯ সালে ৪ মে মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান দেশের আযাদীর জন্য শাহাদাত বরণ করলেন। বাংলার পথে-প্রান্তরে তখনো ফকীর বিদ্রোহীগণ তাঁদের বিদ্রোহের ঝান্ডা উঁচু রেখেছেন। অন্যদিকে মহীশূর থেকে বিজয়ীর বেশে কর্ণওয়ালিস কলকাতায় ফিরে এলে শহরের নব্যসৃষ্ট বর্ণহিন্দু প্রধান ব্যক্তিরা তাকে বাংলা ও ফারসি ভাষায় মানপত্র দিয়ে বরণ করে নেয়।
ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলন
ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ বছর ধরে বাংলার মুসলমানদের যেসব আপসহীন মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তার মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ও জিহাদ আন্দোলন ছিল সবচে ব্যাপক ও সুসংহত এবং বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারক। হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৬৪-১৮৪০) নেতৃত্বে ১৮১৮ সালে পূর্ববাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা হয়। জিহাদ আন্দোলন ছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) ও তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আযীযের (১৭৪৬-১৮৪৩) বিপ্লবী ভাবধারায় উৎসারিত। শাহ আবদুল আযীয খেলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনের প্রবীণদের মধ্যে তাঁর তিন ভাই শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) শামিল ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয শেষোক্ত তিনজন আলেমকে সামনে রেখেই উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী গঠন করেন। এর আগে তিনিই ১৮০৩ সালে ইংরেজ পদানত হিন্দুস্থানকে সর্বপ্রথম ‘দারুল হরব’ বলে ঘোষণা করেন এবং আযাদী পুনুরুদ্ধারের জন্য জিাহদের আহবান প্রচার করেন। এই আন্দোলন ‘তরীকয়ে মুহাম্মদিয়া’ বা ‘জিহাদ আন্দোলন’ নামে পরিচিত হয়। সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ১৮২১ সাল থেকে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সারা উপমহাদেশ জুড়ে।
জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের উৎসভূমি, সংগঠন-কাঠামো ও কর্মসূচিতে পার্থক্য ছিল। কিন্তু মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আচার-আচরণ, নীতি-প্রথা ইসলামের আলোকে পুনর্গঠন, তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিজাতীয় কুসংস্কার, কুপ্রথা ও বিদআত থেকে মুক্ত করা এবং ইসলামের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে থেখে ইংরেজদের উৎখাত করার ব্যাপারে তাঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। জিহাদপন্হিগণ তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্য সকল শক্রর বিরুদ্ধেও প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্থ করেছেন। বাংলাদেশেই ইংরেজ শাসন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে এবং এখানেই বর্ণহিন্দু জমিদারদের জুলুম-শোষণ ব্যাপকতর ও গভীরতর হওয়ার কারণে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈকি জীবনের অবক্ষয় ছিল সবচে বেশি। ফরায়েজী নেতৃবৃন্দকে বাংলার মুসলমানদের সেই ক্ষতস্থানগুলোর পরিচর্যা করতেই অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির পরই তাঁরা সশস্ত্র লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।
ফরায়েজী নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক কর্মসূচি ছিল ফরয প্রতিষ্ঠা, শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন, তওবার, আন্দোলন, মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার এবং বিধর্মীয় নাম, পোশাক ও আচার-অনুষ্ঠান বর্জন, ধর্মের নামে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী নির্মূল, মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, সামাজিক ভে-বৈষম্য দূরূকরণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি ছিল জমিদার-মহাজন-নীলকরদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিকার, সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, ইংরেজদের হাত থেকে আযাদী পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইংরেজ কবলিত ভারতকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা, দেশ শক্রমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জুমুআ ও ঈদের নামায বর্জন এবং মুক্ত স্বদেশে স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা। অল্পদিনের মধ্যেই শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে বারো হাজার কৃষক সংগঠিত হয়। ঢাকা, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালী, নদিয়া ও মোমেনশাহীতে তাঁর আন্দোলনের প্রভাব বেশি ছিল। সবচে বেশি প্রভাব ছিল কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে। এসব আন্দোলনের কারণে হিন্দু জমিদার-মহাজনরা ক্ষেপে যায়।
১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী যখন বালাকোটের প্রান্তরে এবং তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সে বছরই হাজী শরীয়তউল্লাহ পূর্ববাংলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সময় জিহাদ আন্দোলনের পূর্ব-ভারতীয় নেতা মওলানা ইনায়েত আলী (১৭৯৪-১৮৫৮) ‘কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য’ পল্লী বাংলার জনগণকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান এবং ইসলামের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ফরায়েজীগণ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে ব্যাপক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয় এক অভূতপূর্ব প্রজাবিপ্লব। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরায়েজী নেতাদের সংগ্রামের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। প্রজাদের জন্য ‘পিতার দরদ’ এবং অবিচারের বিরুদ্ধে ‘মুজাহিদের তেজ’ নিয়ে প্রতিপত্তিশালী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। শান্তিপূর্ণ সকল প্রচেষ্টা ব্যার্থ হওয়ার পরই তাঁরা প্রজাদের সংগঠিত শক্তিকে অস্ত্রবলে বলীয়ান করেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের কাছে অত্যাচারী জমিদাররা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্র দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ঘোষণা করেন : “সব মানুষ ভাই ভাই। পৃথিবী আল্লাহর : সৃষ্টি যার শাসনও চলবে তাঁর”। তাঁর স্লোগান ছিল : “লাঙ্গল যার, জমি তার”, “সৃষ্টি যার, আইন তাঁর”। বস্তুত জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের বক্তব্যের মূল সুর ছিল অভিন্ন।
জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে বাংলার জনগণ একেবারে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। ১৮২১ সালে হজ্জ সফর উপলক্ষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী কলকাতায় আসেন। বাংলার ওলামায়ে কেরাম ও সচেতন জনগণের একটি বিরাট অংশ সে সময় সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে এসে জিহাদ আন্দোলনের বাইআত বা শপথ গ্রহণ করেন। তিতুমীর তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ১৮২৫ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর প্রত্যক্ষ লড়ইয়ের অংশীদার পাঁচ-ছয় হাজার মুজাহিদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই যোগ দিয়েছিলেন বাংলা থেকে। তাঁদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সীমান্ত প্রদেশে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারের ‘মজলিসে শূরা’ বা মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন পূর্ববাংলার বিপ্লবী মুজাহিদ নেতা ইমামউদ্দিন বাঙালি। ১৮২৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের কঠিন সংকটকালে জনশক্তি ও আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশ থেকেই প্রথম গিয়ে পৌঁছেছিল। জিহাদ আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাধণতাকামী মুসলমানদের ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল রাখঅর ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় মা-বোনেরা তাঁদের অলংকার এবং অনেকে তাঁদের গরু-বাছুর বা জমি বিক্রি করে জিহাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন। ১৮৩১ সালে ৬ মে বালাকোটের প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মওলানা শাহ ইসমাঈল-এর সাথে দুই শতাধিক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় অন্তত নয়জন বাঙালি মুসলমানের নাম এ পর্যন্ত জানা গেছে। ইমামউদ্দীন বাঙালিসহ বাংলার প্রায় চল্লিশ জন মুজাহিদ বালাকোটের লড়াইয়ে আহত হন। বালাকোট-এর ময়দান থেকে ফিরে এসে তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন।
এই সময় বাংলার জিহাদ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকার বংশালে। পাটনা ছিল মূল কেন্দ্র। ফরায়েজী আন্দোলনের বেশি প্রভাব ছিল মোমেনশাহী থেকে বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে। আর জিহাদ আন্দোলন বেশি শক্তিশালী ছিল উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে। ফলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে সে সময় ইংরেজ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে এই দু’টি আন্দোলনের মিলিত প্রভাব বাংলার প্রায় সবটা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বাইরে থেকে অনেকের চোখেই এই দু’টি আন্দোলনের পার্থক্য ধরা পড়তো না। উভয় আন্দোলনকে ইংরেজ ও তাদের সমর্থকরা ‘ওয়াহাবী আন্দোলন’ নামে চিহ্নিত করত।
জিহাদপন্হি তিতুমীরের লড়াই
মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ১৮২১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর সাথে সাক্ষাত এবং মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে তিনি সাইয়েদ সাহেবের একজন খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় জিহাদ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনের সমসাময়িককালে পরিচালিত তিতুমীরের আন্দোলনের সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন। মারাঠা-বর্গীদের দ্বারা লুণ্ঠিত পশ্চিমবাংলায় হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা নিষ্পেষিত জনগণ অথনৈতিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের ওপর কায়েক হয়েছিল হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তহবন্দ-এর পরিবর্তে ধুতি, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলমানী নাম রাখতে জমিদারের পূর্বনুমতি ও খারিজানা, হিন্দুদের পূজার জন্য পাঁঠা যোগানো ও চাঁদা দেওয়া, দাড়ির ওপর ট্যাক্স, মসজিদ তৈরি করলে নজরানা, গরু জবাই করলে ডান হাত কেটে নেওয়া প্রভৃতি জুলুম ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। এই পটভূমেই জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত মওলানা তিতুমীল কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করে তিনি জনগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ পূর্ণরূপে অনুসরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণায় তিনি সকলকে উজ্জীবিত করেন। বিরান হয়ে যাওয়া মসজিদসমূহ তিনি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রচলন করেন। তিনি পূজার চাঁদা দান বা তাতে অংশগ্রহণের মতো কাজ বন্ধ করেন। শিরক-বিদআত বন্ধ করেন। মুসলমানী নাম রাখা, ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, পীরপূজা ও কবরপূপা বন্ধ করা, কুসংস্কার ও অনৈসলামী কাজের মূলোচ্ছেদ তথা কুরআন-হাদীসের খেলাফ কোন কাজ না করা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠন তাঁর র্কসূচির অন্তর্ভুক্ত।
তিতুমীরের আন্দোলনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানগণ এবং বহু অমুসলমান কৃষক দ্রুত জোটবদ্ধ হলেন। তিতুমীরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক বিরাট ইসলামী জামাত। তিতুমীরের সংগ্রাম ছিল জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর স্লোগান ছিল ‘লাঙ্গল যার জমি তার’। তাঁর বক্তব্য ছিল ‘প্রত্যেকের শ্রমের ফসল তাকে ভোগ করতে দিতে হবে’।
এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রীদেবনাথ রায়, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার শ্রীরায়বল্লভ, তারাবুনিয়ার জমিদার শ্রীরামনারায়ণ নাগ, নাগরপুরের জমিদার শ্রীগৌরপ্রসাদ চৌধুরী, সরফরাজপুরের জমিদার শ্রী কে পি মুখার্জী ও কলকাতার গোমস্তা লাটু বাবুরা ঐক্যবদ্ধ হয়। ইংরেজ নীলকররাও ছিল তাদের পক্ষের শক্তি। একদিকে তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন, অন্যদিকে জমিদারদের জুলুমের মাত্রা বাড়ছিল তীব্র গতিতে। তিতুমীরের একজন পত্র-বাহককে পুঁড়ার জমিদার নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। জমিদারের লোকেরা বশিরহাটের জামে মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের ঘরবাড়ি তারা লুট করে। এভাবেই একটির পর একটি ঘটনা ঘটতে থাকে।
এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মুসলমানগণ তিতুমীরের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়াতে থাকেন নানা জায়াগায়। এরূপ পটভূমিতে তিতুমীরের বাহিনীর সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নারিকেলবাড়িয়ার এক বিরান মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রতিরোধের দুর্গ। গড়ে ওঠে বাঁশের কেল্লা। তিতুমীরের বাহিনী নদিয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার অধিকাংশ ভূখণ্ড মুক্ত করে। এই সীমিত ভূখণ্ডে মুসলমানদের স্বরাজ কায়েক হয়। এভাবেই তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন মাতৃভূমি আযাদ করার রক্ত-পিচ্ছিলপথে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে জমিদার ও ইংরেজদের পরাজয় হয়।
এরপর পূর্ণাঙ্গ লড়াই। বড়লাট লর্ড ব্যান্টিঙ্কের নির্দেশে ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ড, ক্যাপ্টেন শেক্সপীয়রসহ ইংরেজদের অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী হামলা চালায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। ১৯ নভেম্বর ফযরের নামাযের পর তিতুমীর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বী ভাষায় অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি জাতির ঈমান, অধিকার ও আযাদী রক্ষার সংগ্রামে শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য তাদেরকে বুলন্দ আওয়াজে আহ্বান জানালেন।
যুদ্ধ শুরুর আগে ইংরেজ সেনাপতি ও তিতুমীরের মধ্যে রামচন্দ্র নামক একজন দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা হয়। দোভাসী উভয় পক্ষের বক্তব্য বিকৃতভাবে পরিবেশন করে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীর, তাঁর পুত্র মীর জওহর আলী ও আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ময়েজউদ্দীন বিশ্বাসসহ বহু যোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। তিতুমীরের দুই পুত্র মীল তোরাব আলী ও মীর গওহার আলী এবং সেনাপতির ভাগ্নে গোলাম মাসুমসহ বন্দী হন সাড়ে তিন শত মুক্তিযোদ্ধা। গোলাম মাসুমকে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলা হলে তিনি ঘৃণার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেল্লার পুব পাশে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়। এ্ই যুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজ সেনাপতি মেজর স্কট মন্তব্য করেছেনঃ
“যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, কিন্তু জীবন দিয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ”।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব
পলাশী বিপর্যয়ের ঠিক একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। শত বছর ধরে এদেশের আযাদী পাগলা মুসলমানরা যে নিরন্তর বিদ্রোহ পরিচালনা করে ‘ রাণীর বিদ্রোহী প্রজা’ অভিধা লাভ করেছিলেন, সিপাহী বিপ্লব নামে পরিচিত আযাদীর লড়াই ছিল তারই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কগণই ছিলেন সিপাহী বিপ্লবের মূল শক্তি ও অনুপ্রেরণা। ১৮৩১ সালে বালাকোটের সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর বাহিনীর বিপর্যয়ের পর জিহাদের বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জীবিত নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অন্যতম অনুসারী হাফিয কাসিম।
জিহাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনারেল বখত খান, মওলানা আহমদ উল্লাহ শাহ ও মওলানা ফজলে হক খায়বাদী দিল্লী কেন্দ্রে, হাজী ইমদাদউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীগণ শামেলী, সাহারানপুর ও থানাভবনে সক্রিয় ছিলেন। হাফিয কাসিমের অনুসারী নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের মধ্যে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসিম নানুতুভী, মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী, মওলানা মোহাম্মদ মুনীর প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ,দিল্লী ও কানপুরসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে এক সুগ্রন্হিত যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল।
জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক মওলানা আহমদউল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৬৫ সাল থেকেই বিপ্লব ও বিদ্রোহের সংকেতবাহী চাপাতি রুটি ও রক্তজবা ফুল বিতরণ শুরু হয়ে যায়। এক গ্রামের নেতার হাত থেকে দ্রুত অন্য নেতার হাতে ঘুরছিল বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী চাপাতি রুটি। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন রক্ত-রঙিন আযাদী বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী জবা ফুল। সে কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সবখানে বিপ্লবীদের কার্যক্রমের খবর প্রতিদিনই সতর্কতার সাথে পৌঁছে যাচ্ছিল।
১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা আহমদউল্লাহর বিরুদ্দে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারপত্র বিলির অপরাধ প্রমাণ করে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ৈ শহীদ করা হয়। তার আগে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ভ ও সংগঠিত করেন। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারিতে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ
“দেশবাসী, আপনারা জেগে উঠুন। ফিরিঙ্গি কাফেরদের উৎখাত করতে আপনরারা সংঘবদ্ধ হোন। এই কাফেররা ন্যায়ক পদদলিত করেছে, আমাদের স্বরাজ্য তারা লুণ্ঠন করেছে। এই কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সে সংগ্রাম হবে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য জিহাদ”।
জিহাদ আন্দোলনের অসংখ্য বিপ্লভী নেতা এ সময় হিন্দুস্থানের প্রত্যন্ত এলাকায় এমনিভাবে দেশবাসীকে আযাদী পুনরুদ্ধারের লড়ইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বদ্ধ করছিলেন। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরও জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রাম দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এ সময় এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।
১৮৫৭ সালে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের রাজধানী কলকাতার ব্যারাকপুরে। বাংলায় সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, যশোর প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার বিদ্রোহ চলাকালে একজন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও চারজন আহত হয়। অন্য দিকে ৪০ জন দেশীয় সিপাহীসহ বহু আহত হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য ১৮৫৭ সালে লালবাগের যে স্থানটিতে সেদিন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্ত ঝরেছিল, সে স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য ইংরেজরা সেখানে কারাগার নির্মাণ করে, যা এখনো বিদ্যমান। ইংরেজদের হাতে বন্দী বিপ্লবী মুসলমান সিপাহীদের ষাট জনকে সদরঘাটের অদূরে ‘আন্টাঘর ময়াদনে’ গাছের শাখায় ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁদের লাশ মাসের পর মাস সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবকামী জনগণকে আতঙ্কিত করার জন্য। সেই আন্টাঘর ময়দানই এখন ‘বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি স্মৃতির মিনাররূপে তা আজো আমাদের পূর্বপুরুষদের মহান আত্মদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
১৮৭৫ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরেজরা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়াকে প্রেফতার করে এ জন্য যে, তাঁর আহ্বানে যে কোন মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার লোক সাড়া দিতে এবং তিনি তাদেরকে যা আদেশ দেবেন, তারা তাই করতে প্রস্তুত ছিল।
১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ নামে বিকৃত করার চেষ্টা করা হলেও এই বিদ্রোহের পেছনে আযাদী পাগল বেসামরিক মুসলিম বিপ্লবীদের ভূমিকাই মুখ্য ছিল। একথা কোন কোন ইংরেজ লেখকও স্বীকার করেছেন। স্যার জেমস আউটরামের মতেও বিপ্লবী মুসরমানগণই ছিলেন এই বিদ্রোহের মূল শক্তি। বিদ্রোহ দমনের কাজে নিয়োজিত দু’জন ইংরেজ সৈন্য ১৮৫৭ সালে বেনামীতে লেখা বিদ্রোহের ইতিহাস বইয়ে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীকে এই ঘটনার সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁরা লিখেছেনঃ
“রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় নির্বাসিত হন এবং তিনি ব্রিটিশ শাসন উৎখানের উপায় তালাশ করতে থাকেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সৈন্যদের সমর্থন আদায়ের জন্যী তিনি চেষ্টা চালাতে থাকেন। অযোধ্যার নবাবের সভাসদ ও অনুচরগণ সন্দেহাতীতভাবে এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিলেন”।
১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজরা জনগণের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করে। বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ কতজনের যে ফাঁসি হলো, কত লোকের হলো কারাবাস, সে হিসাব পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিতদের সংখ্যাই ছিল দশ হাজারের বেশি।
জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক আন্দামান-বন্দী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেনঃ
“স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন একজন মুসলমনাও সে দিন বাঁচেনি”।
আপসহীন বিপ্লবী ধারার অবসান
সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের নেতা মওলানা ইনায়েত আলী এবং ১৮৬২ সালে ফরায়েজী আন্দোলনের নায়ক দুদু মিয়া ইন্তেকাল করেন। বিপ্লবোত্তর ব্যাপক মুসলিম নির্যাতনের পটভূমিতে এবং আন্দোলনের দুই প্রধান কান্ডারীর ইনতেকালের পর এই দু’টি আন্দোলনের ধারা কিছুটা দুর্বলভাবে হলেও আরো বহু দিন অব্যাহত থাকে। ১৮৬৬ সালে জিহাদী বিপ্লবীগণের উদ্যোগে তাঁদের আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটিরূপে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই জিহাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। অন্যদিকে দুদু মিয়ার পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দার ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এবং আবদুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এ সময়ও ফরায়েজী আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল।
১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত তথাকথিত ‘ওয়াহাবী মামলাগুলো থেকে জানা যায় যে, সে সময় পর্যন্ত বাংলায় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ধারা চালু ছিল। এ সময়ও বিভিন্ন গ্রামে ফরায়েজীদের একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন এবং বিচার-ফয়সালা থেকে শুরু করে জনগণের শাসনকার্যের বিরাট অংশ তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯০১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখানো হয়েছে যে, বগুড়ায় ফরায়েজীরা তখনো সক্রিয়। সরকারবিরোধী জিহাদের জন্য তাঁরা চাঁদা তুলতেন এবং প্রতিটি ফরায়েজী পরিবারে জিহাদের জন্য মুষ্টি-চাল রাখা হতো।
নয়া মিয়ার পুত্র খান বাহাদুর সাঈদউদ্দীন আহমদ ১৮৮৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এবং এর পর তাঁর পুত্র আবু খালিদ রাশিদউদ্দিন ওরফে বাদশাহ মিয়া (মৃ. ১৯৫১) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সাঈদউদ্দীন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। বাদশাহ মিয়া খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেন।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি