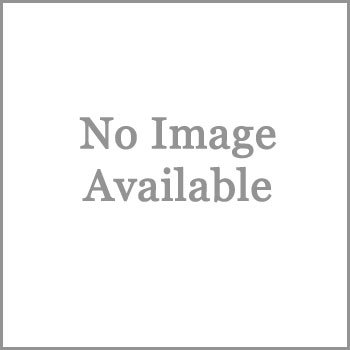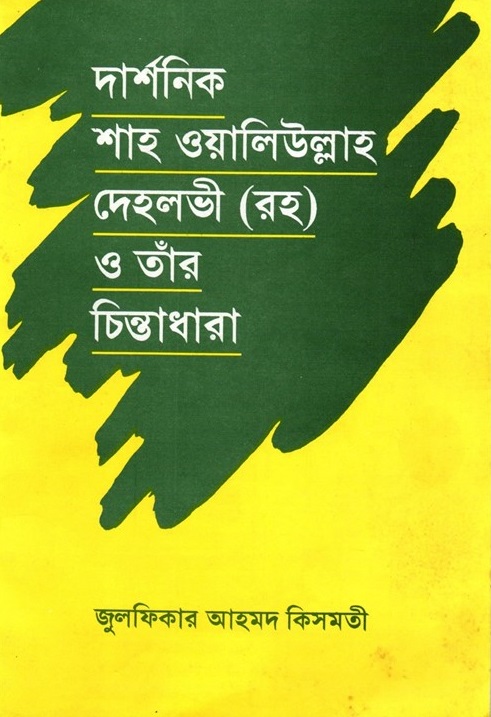দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ) ও তাঁর চিন্তাধারা
হিজরী পঞ্চম শতক পর্যন্ত মুসলমানগণ সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, আইনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, স্থাপত্যশিল্প, রাজ্য জয় তথা বৈষয়িক দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে উন্নতির উত্তুঙ্গ চৃড়ায় সমাসীন থাকলেও তার পরবর্তীকালে সারা মুসলিম জাহানে চিন্তার বন্ধ্যান্ত্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এমন স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার এক রকম বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কেবল চোখ বুঁজে পূর্ববর্তীদের অনুসরণই করা হতো না বরং অনেক জটিল সমস্যার ক্ষেত্রেও মনে করা হতো যে, এ ব্যাপারে উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর গবেষণার যুগ হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী লোকদের এ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোন অধিকার নেই।
এছাড়া এমনিতেও দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ইমাম-মুজতাহিদগণ এক দিকে বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী চিন্তা-গবেষণায় রত রয়েছেন, অপরদিকে ক্ষমতালোভীগণ ইসলামী মূল্যবোধকে নানাভাবে ব্যাহত করে আসছে। বনী উমাইয়া ও আবাসিয়াদের শাসনামলে (উমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া) ইসলামের সাংস্কৃতিক জীবন এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়। গ্রীক সাহিত্য-দর্শনের নির্বিচার তরজমা ও প্রচার মুসলমানদের চিন্তা জগতে এক নৈরাজ্যের সূচনা করে। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে জাহেলী যুগের চিন্তাধারার প্রসাবের ব্যবস্থা করে। হিজরী পাঁচ শতকের শেষার্ধে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, গ্রীক সাহিত্যানুরাগ ও দর্শন-প্রীতির প্রবণতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। মুসলিম শাসক ও জনগণের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের মারাত্নক অবনতি ঘটে। এক শ্রেণীর আলিম, ফকিহ, মুফতী বিজাতীয় দর্শনের মাপকাঠি দিয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়। তার পরবর্তী পর্যায়েও দেখা যায় মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে আরও নানাবিধ কুসংস্কার ও বাতিল চিন্তাধারা গজিয়ে উঠেছে। মানুষ এ সময় দমননীতি মূলক রাজতান্ত্রিক পরিবেশে থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা সম্পর্কেই অপরিচিত হয়ে পড়ছিল। মানবজীবনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনসমূহ তথা ইসলামের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ বিজয়ী জীবন-বিধান, সাধারণ ভাবে মুসলিম সমাজ থেকে এ ধারণা বিধায় গ্রহণ করছিল। আর তার স্থান দখল করছিল সুফিবাদ তথা ইসলামের আংশিক রূপ-বরং ক্ষেত্রে বিশেষে বিকৃত রূপ-যার জের এখনও চলছে এবং এখনও কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক কতিপয় ইবাদতকেই পূর্ণ ইসলাম বলে মনে করছে। দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাজশক্তির অধীনে ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারা নিয়ে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এলেও সমগ্র সমাজের সামগ্রিক নিস্পৃহতা ও নিরাশক্তির সম্মুখে তা সহজেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। ঐ ভাবধারা মূলক কোন কিছু বলা ও লেখাও ছিল জীবনের পক্ষে বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। এ ছাড়া ঐ পরিবেশে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অনুসৃত কৌশলগত নীতিরও ছিল তা পরিপন্হী। এসব কারণে মহানবী (সা) ও তাঁর ত্যাগী সাহাবীগণ প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনার দ্বারা জাহিলিয়াতের সকল দুর্ভেদ্য প্রাচির চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মানব জাতির সামনে যে আল্লাহ প্রদ্ত্ত জীবনবিধান পেশ করেছিলেন, ক্রমে তা থেকে মুসলমানদের বিচ্যূতি ঘটতে থাকে।
উপমহাদেশের অবস্থা
একদিকে ইসলামের ব্যাপারে সুষ্ঠু জ্ঞান-গবেষণার অভাব, অপরদিকে নিত্য নতুন ভ্রান্ত চিন্তাধারার উদ্ভাব-এ উভয় অবস্হার মধ্য দিয়ে যখন ইসলাম গতিশীলতা হারিয়ে দ্বাদশ হিজরীতে পদার্পণ করে, তখন এই চিন্তার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্হা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে স্বার্থদুষ্ট মুসলিম শাসকদের হাতে ইসলাম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, তা আর কোথাও হয়নি।কেননা, দুই একজন ছাড়া দিল্লীর মুসলিম রাজা-বাদশাহরা পাক-ভারতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করা তো দূরের কথা বরং ইসলামী আদর্শের খেলাপ নানারূপ কাজ করে এ দেশের সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের এক বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরে। মোগলদের আমলে বিশেষ করে হিজরী দশম শতাব্দীর শের্ষাধ থেকে পরিস্হিতির আশংকাজনক অবনতি ঘটে। ইসলামের সঙ্গে সম্রাট আকবরের (৯৬৪-১০৬৪ হিঃ) সীমাহীন ধৃষ্টতা মুসলিম সমাজ জীবনে বিরাট বিষফোঁড়ার সৃষ্টি করে। সম্রাট আকবর যে কোন মূল্যে হিন্দুদের মন রক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। আকবরের ধারণা ছিল এই যে, প্রয়োজনে হিন্দুদের সক্রিয় সমর্থন ভিন্ন কেবল মাত্র সংখ্যালঘু মুসলমানদের শক্তির ওপর মোগল শাসন ভারতে দীর্ঘ স্হায়ী হতে পারে না। তাই পূর্বপুরুষদের সিংহাসন সংরক্ষণের জন্য আকবর নিজস্ব জাতীয় তাহযীব-তমদ্দুন এবং ঈমান-আকীদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, উপরোক্ত চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর বহু হিন্দু রীতিনীতি গ্রহণ করেন এবং অমুসলমানদের উপর থেকে জিযিয়া কর প্রত্যাহা করেন। তিনি এ সবকিছুই বহু নিন্দিত সেই ‘দীনে ইলাহী’নামক নিজের উদ্ভাবিত প্রহসনমূলক ধর্মের নামেই করতেন। উল্লেখ্য যে, ৯৮৩ হিজরী থেকে আকবরের মনে এ দুষ্টামি চেপে বসে এবং এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা স্হির করার জন্য এক শ্রেণীর আলিম, পীর ও হিন্দু পন্ডিত ছাড়াও শিয়া, খৃষ্টান, ইয়াহুদি. অগ্নিপূজক প্রভৃতি ধর্মের পন্ডিতদেরও দরবারে হাযির করেন। পরে প্রত্যেকের বক্তব্যের আলোকে নিজ স্বার্থ বুদ্ধিকে কার্যকরী করেন এবং ৯৯০ হিজরীতে ‘দীনে-ইলাহী’ প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা করেন। আকবরের এই গোমরাহীর পশ্চাতে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার সাথে সাথে তাঁর অমুসলিম বেগমদের গভীর প্রভাবও কাজ করেছিল। হেরেমে হিন্দু রমণীদের অস্তিত্ব গোটা পরিবেশকে হিন্দু বানাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রাঁসাদের অভ্যন্তরে নানা ধর্মের উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়। হিন্দু মেলা-তেহারের সময় সম্রাটের প্রাসাদে সাধারণ উৎসব পালন করা হতো। সন্ধ্যা বাতির সময় আকবর দাঁড়িয়ে সম্মান গ্রহণ করতেন। আযান ও গরু যবাই নিষিদ্ধ। ছিল। দরবারের লোকদের পোষাক- পরিচ্ছনদ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ছিল।মুসলিমদের মুখ থেকে দাড়ি বিলুপ্ত হতে শুরু করলো। এক কথায় সারাটি পরিবেশ, প্রাসাদের যাবতীয় কাজকর্ম, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান একান্তভাবেই হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল। ঐ যুগের পোষাক, স্থাপত্য, চিত্রনির্মাণ সকল কিছুর মধ্যেই হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। ফতেহপুর সিক্রির সমজিদ ও শায়খ সলীম চিশতীর সমাধি একইভাবে হিন্দু স্থাপত্যের প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করা হয়। শায়খ সলীম চিশতীর সমাধি সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইনস্টন স্মিথ সন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ “মুসলমান সমাজের একজন তেজস্বী মহান আধ্যাত্মিক সাধকের সমধিগাত্রে হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের প্রতিক লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত হয়েছি। গোটা সমাধি সৌধটিতেই হিন্দু ভাবধারার অভিব্যাক্তি সুস্পষ্ট। (Akbar the Great Mughal. P.P. 442-443) এমনিভাবে Henell- এর মন্তব্যও লক্ষণীয়। তিনি বলেনঃ “ফতেহপুরের মসজিদটিকে মসজিদ অপেক্ষা বৈষ্ণাব মন্দির বলে মনে হয়।“ (A Hand Book of Indian Art, p 65)।
এক শ্রণীর আলিমের ভূমিকা
আকবরের এই পথভ্রস্টতার জন্য তৎকালীন সরকারের এক শ্রেণীর তল্পিবাহক আলিম এবং পীরও কম দায়ী নন। তাদের পাস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ, হিংদ্ধতা এবং দীন ইসলামের মূল দাবীর ব্যাপারে জ্ঞানের স্বল্পতা বা অজ্ঞাতা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। ক্ষমতাসীনদের প্রতি তাদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং দীনের ব্যাপরে তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই তারা ৯৮৭ হিজরী সনে আকবরকে “যিল্লুল্লাহ” (আল্লাহর ছায়া বা রহমত), ন্যায়পরায়ণ নেতা’‘যুগ ইমাম’’তিনি সকল আনুগত্যের উর্ধে’ তাঁর হুকুমই সকলের উপর প্রযোজ্য’ প্রভৃতি আল্লাহর গুণে অভিহিত করে ফতোয়া জারি করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেননি। তাঁর প্রতি সম্মানসূচক সিজদ করারও ফতোয়া তাঁরা দিয়েছিলেন। মরহুম মওলানা আবুল কালাম আযাদ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ “আকবরের শাসনামলে মখদুমুল মুলক ও আবদুন নবীর মতো ওলামায়ছূ- অসৎ আলিমরা [ ইসলামী ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের বিকৃত ঈমান ও বিকৃত আমলের আলিদেরকে ‘ওলামায়ে ছূ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি বর্তমানে একটি পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত। তাযকিরা, পৃষ্ঠাঃ ২১।] উক্ত ফতোয়ায় দস্তখত করে নিজেদেরকে যে কঠোর শাস্তির যোগ্য করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ কি ধরনের ব্যবহার করবেন সেটা তিনিই ভালো জানেন। তাবে এতে কোন সন্দহে নেই যে, ঐ সকল আলিম এহেন নিন্দানীয় কাজের মাধ্যে যে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সত্য কথা বলতে কি, বিভিন্ন যুগে ইসলামের ওপর যত আঘাত এসেছে এহেন‘ওলামায়ে ছু’ এর কারণেই এসেছে। আমি বলবো যে, আকবরের এই গোমরাহী সৃষ্টর জন্য সব চাইতে যারা বেশী দায়ী তারা আবুল ফজল ও ফয়েজী নয় বরং এসব ‘দুনিয়ার কুকুর’ রাই অধিক দায়ী। দুর্ভাগ্য, ঐ সময় এই স্বর্থপর ব্যক্তিরাই আলিমের আবরণ পরে রেখেছিল।
যা হোক, আকবর কর্তৃক সৃষ্ট এই ঘোর তমসার বুকে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মুজাদ্দিতে আলফেসানীর ন্যায় এক প্রচন্ড সূর্যের উদয় ঘটান এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর দুর্বার আন্দোলন, ত্যাগ- তিতিক্ষা ও প্রতিরক্ষামূলক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে তার অবসান ঘটে। কিন্তু আলফেসানী (রহ) এই গোমরাহী ও তার সঙ্গে সঙ্গে বিদআত শিরকের অপরাপর বেগবান স্রোতের গতি প্রশামিত করতে সক্ষম হলেও উক্ত দুষ্ট ক্ষতের দাগ সম্পুর্ণ মুছে যায়নি। তার কিছু জীবণু পরবর্তী পর্যায়েও অবশিষ্ট ছিল। কেননা দেখা গেছে, আকবরের ‘দীনে ইলাহীর’ অনুসারীর সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও এর সাধারণ প্রভাব ব্যাপকভাবে সংক্রমিত ছিল। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন, মুসলিম লেখকগণ যেখানে সাধারণত নিজ নিজ লেখা বিশেষ করে গ্রন্হাবলী ‘হামদ ‘ও ‘নাত দ্বারা শুরু করতেন সে ক্ষেত্রে বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন সরকারী লোক ও শাহী দরবারের মূসলান লেখকগণ নিজেদের হিন্দু সংস্কৃতি ভাষার গ্রন্হাদির সুচনা করতেন গনেশ বা স্বরসতী প্রভৃতি হিন্দু দেব- দেবীর নামে। এ ছাড়া ‘দীনে ইলাহীর ধারণা ও প্রভাব আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলেই কেবল নয় তার প্রপৌত্রের আমলেও যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে দারাশিকে। শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো প্রথম দিকে সফী ভাবধারা প্রভাবান্বিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি ক্রমশ হিন্দু ধর্মমতের প্রতি ঝুকে পড়েন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বহু হিন্দু ধর্মগ্রন্হ ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়। হিন্দু সর্বশ্বরবাদের পরিভাষার সাথে স্বমতের পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সমম্বয় সাধনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তঁর এই চিন্তাধারা লক্ষ্যে- অলক্ষ্যে অনেক নিষ্ঠাবান সুফীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। দারাশিকো এভাবে সুফিদের দ্বারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন (islam the Straight path)
সম্রাট আওরঙ্গজেব (১০৬৮- ১১১৮ হিজরী) ও দারাশিকোর বিরোদ এবং পরিনামে দারাশিকোর বিরোধ এবং পরিণামে দারাশিকোর পরাজয় ও নিহত হবার পেছনে মূলত এ কারণই কার্যকর ছিল। উভয়ের বিরোধকে দুই ভাইয়ের রাজক্ষমাত দখলের ঝগড়া মনে করা কিছুতেই ঠিক হবে না। বরং এ বিরোধ ছিল দুটি চিন্তাধারার এবং দুটি আদর্শে। আবুল মুযাফফর মুহিউদ্দিন আলমগির আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন উপমহাদেশে মহানবীর আদর্শ তথা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং দারাশিকো চেয়েছিলেন এখানে প্রপিতামহ আকবরের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে। কারো কারো মতে দারাশিকো ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হলে মোগল সাম্রাজ্য আজো টিকে থাকতো এবং টিকে না থাকলেও উপমহাদেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এসব কারণেই আওঙ্গজেবের মতো ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী একজন মুসলিম শাসকের যুগ অতিক্রন্ত হবার পরও দেখা গেছে যে, পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত শাসকের অযোগ্যতায় সেই হিন্দুয়ানী ভাবধারা এবং এরই সঙ্গে শিয়া মতবাদ ও নানাবিধ অনৈসলামিক ভাবধারাপুষ্ট ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (৯৭১-১০৩৪ হিজরী) ও পরবর্তীকালে সাধক সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রচেষ্টায় যেসব অনৈসলামী রীতিনীতে ও ভাবধারা বিলপ্ত হয়ে গিয়েছিল, উক্ত শাসকের দুর্বলতার সুযোগে সেগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে এঠে। এ ছিল পাক-ভাবতের সাধারণ অবস্থ। তার পাশাপাশি সমাজের শিক্ষার অঙ্গন এবং সুধীমহল তথা ওলামা ও পীর- মাশায়েখদের কার্যকলাপ ছিল আরও আরও অধঃপতিত। এক ধরনের সুফী ও ফকীর দরবেশ নামাধারী ব্যক্তি ফকীরী মারেফতীর ছদ্মবরণে সাধারণ মানুষের ধন-সম্প লুট করে যেতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তখনো এরিস্টটালের প্রচারিত মতবাদের পচা লাশের ওপর অস্ত্রোপচার চলছিল। মাদ্রাসাগুলোতে ‘শামসে বাজেগা’ও ‘কাযী মুবারক ‘ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পঠিত হলেও কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার প্রতি করুরই ভ্রক্ষেপ ছিল না। মূলত ‘উলুমে ইলাহিয়া’র মধ্যে তাঁরা এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, ‘কালামে ইলাহীর’র প্রতি ভ্রক্ষেপ করার সময়ই তাদের হাতে থাকতো না। তৎকালীন সাধারণ শিক্ষা তথা দরসে নিজমী [ বর্তমান সময়ের প্রচালিত কওমী মাদ্রাসার শিক্ষানীতি।] থেকে যদি কোন বিষয় পাঠ্যের বহির্ভূত থেকে থাকে তো তা ছিল কুরআন মজীদ। ‘বড় বড় আলিমদের শিক্ষাচক্রেও একমাত্র মিশকাত শরীফ ও ‘মাশারেকুল- আনওয়ার’ পড়ানোকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। অবস্থা এই ছিল যে, মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁর সমকালীন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)-এর (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) চিন্তাধারা পরিবেশের আলিমগণ। মুফতিগণের অবস্থা ছিল এই যে, তঁরা ‘মাতায়াখখিরীন’ অর্থাৎ ৫ম হিজরীর পরবর্তী ফকীহ মুজদাহিদদের ফতোয়াকেই চুড়ান্ত বলে করতেন। ইবনে নাজীম (৯৭০ হিজরী) এবং মোল্লা আলী ক্বারীর (১০১৪ হিঃ) কোন ফিকহী মতের বিরুদ্ধেচরণ করা অসম্ভব ছিল। কেই এ ব্যাপারে ঔদ্ধত্য (?) দেখাতে গেলে হয়তো তাকে ওহাবী নতুন মুবতাদিন (বিদআতী) কিংবা লা- মাযহাবী ও অন্যান্য ধমীয় তিরস্কারবাপে জর্জরিত হতে হতো।
ওলামা ও শিক্ষাব্রতীদের এ অবস্থার পাশাপশি সাধারণ মুসলমান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক ছিল। জনৈক অমুসলিম লেখকের মতে ‘সাধারণভাবে উপমহাদেশে ইসলাম তার প্রাণসত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। কেবল ইসলামের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ও কল্পনা প্রসূত অলৌকিকতার প্রতি আসক্তিই প্রধান ছিল। যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করতেন, তাহলে তিনি তাঁর এসব অনুসারীদের মধ্যে ধর্মবিমুখতা ও প্রতিমা পূজা দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। [স্টুয়ার্ড তাঁর গ্রন্হ অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরেছেন। আমীর শাকীব আরসালানের মতে স্টুয়ার্ডই একমাত্র লেখক যিনি মুসলিম দুনিয়ার চিত্র এমন বিজ্ঞাতার সঙ্গে ফুটেয়ে তুলেছেন, যা বিচক্ষণ মুসলিম লেখকের পক্ষেও সম্বব হয়নি। সীরায়েদ আহমদ’পৃষ্ঠা ৫০-৫১তে স্টুয়ার্ডের পূর্ণ রয়েছে।
ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)
পাক-ভারত মুসলমানদের এই বিশেষ অবস্থা এবং সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বের দীনি চিন্তার এই বন্ধ্যাত্বের মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এক আলোর দিশারীর- যিনি তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক থেকে মুসলিম মিল্লাতের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনগুলোর সঠিক তাৎপর্য স্পষ্টরূপে তুলে ধরবেন। যারা চিন্তা- গবেষণার মাধ্যেমে ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ উন্মক্ত হয়ে উঠবে এবং মুসলিম মিল্লাহ ইসলামকে শুধু মসজিদ-মাদ্রসা এ খানকার চার দেয়ালের অন্তর্ভক্ত তথাকথিত ধর্মই মনে করবেন: বরং একে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান রূপে মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তারাই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠান জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করে যাবে, ইসলামের মধ্যে তারা খোঁজ করবে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সমাধান। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ঠিক ঐ সময়ই এ মহান দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত আল্লাহভীরু পরিবারে এক শিশুর জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনিই মুসলিম মিল্লাতের বিশেষ করে পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তার দিক থেকে মুসলিম পনর্জাগরণেরে অগ্রদূত হিসাবে সারা দুনিয়ার ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রূপে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।
তার পিতার নাম হচ্ছে শাহ আবদুর রহিম (রহ)। ইসলামী জ্ঞান- গবেষণার জন্য আবদুর রহীম পরিবার পূর্বে থেকেই দিল্লীতে অধিক মশহুর ছিল। এ পরিবারে বহু খ্যাতনামা আলিম রয়েছেন। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)- এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর পিতামহ শাহ ওয়াজীহুদ্দীন (র) অত্যন্ত সাহসী পরুষ ছিলেন। তিনি সম্রাট আলমগিরের শাসনামলে কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধেও তিনি মোগল সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ পিতা শাহ আবদুর রহীম সম্রাট আলমগীরের শাসনামলেই ইসলামী জ্ঞানের সমাবেশ ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয় ও ধর্মীয় তথ্য-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আল্লহভীরু। সম্রাট আলমগীর যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্র ফতওয়ায়ে আলমগীরী সংকলনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আলিমদের উচ্চ পরিষদ গঠন করেন, তখন তাতে তাঁর নামও ছিল। স্বভাবগত ভাবে তিনি রাজদরবারে চাকরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেও বারবার তিনি এ ব্যাপারে পরিষদকে সাহয্যে করে যান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সম্রাট আলমগীরের ইনতিকালের চার বছর পূর্বে ১১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং ১১৭৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এদিক থেকে তিনি আলমগীরসহ মোট দশজন মোগল সম্রাটের যুগ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা হচ্চেনঃ (১) আলমগীর (আওরঙ্গজেব), (২) বাহাদুর শাহ (৩) মুয়েযযুদ্বীন জাহাদার শাহ (৪) ফররুখ শিয়ার, (৫) রফিউদ্দারাজাত, (৬) রফিউদ্দৌলা, ( ৭) মাহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা, (৮) আবু নসর আহমদ শাহ, (৯) দ্বিতীয় আলমগীর, (১০) সম্রাট শাহ আলম।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ বাল্য বয়স থেকেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি সাত বছর বয়সের সময় কুরআন মজীদ কন্ঠস্থ করেন এবং পনর বছর শেষ হবার আগেই যোগ্য পিতার তত্ত্ববধানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বস্তুত এ কারণে ১১৩১ হিজরীতে যখন শাহ আবদুর রহীমের ইনেতিকাল হয়, তখন সতর বছর বয়সেই তিনি পিতার শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেমে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাদিক্রমে বার বছর পর্যন্ত দিল্লীর রহিমীয়া মাদ্রাসায়া অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সময় ইসলামী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধিত হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের চিন্তাগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক অধপতিত সাক্ষাৎ – অসক্ষাৎ অবস্থা তাঁকে এ সময়ে বসে থাকতে দিল না, বিশেষ করে তৎকালীন ভারতের ধর্মীয়, রাজনৈতক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহের গতিধারা লক্ষ্য করে তিনি গভীর ভাবে চিন্তাযক্ত হয়ে পড়েন। কেননা, সম্রাট আলমগীরের জীবদ্দশাতেই ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ভায়াবহ দু’টি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটি দক্ষিণ ভারত থেকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা আন্দোল, অপরটি শিখ আন্দোল। এছাড়া অন্যান্য বিষয়তো আছেই। ভারতে হিন্দু সভ্যতা ও সং স্কৃতির নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠানই ছিল মারাঠা আন্দোলনের লক্ষ্য। শিখদের যাবতীয় ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলতো পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করেই। প্রথম দিক থেকে এটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন হলেও পরে গরু গোবিন্দের নেতৃত্বে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের দুশমনির সং ক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে সিয়ারুল মুতায়াখাখিরীন গ্রন্হের লেখক উল্লেখ করেন। যে, তাঁরা যেখানেই মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে সেখানেই তাদের বিষয় সম্পত্তিই কেবল লুটতরাজ করে নিয়ে যেতো না, বরং মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলতো। এমনকি তাদের হাত থেকে শিশু- সন্তান পর্যন্ত রক্ষা পেতো না। গর্ভবতী রমণীদের পেট চিরে সন্তান বের করে মা বাপের সামনেই তাদের হত্যা করতো। (সি,মু ৪২ পৃঃ) জনৈক হিন্দু লেখক বলেনঃ মুসলমানদেরকে শিখেরা নিজেদের চরম শক্র মনে করতো। নিজেদের প্রভাবিত এলাকায় মুসলমানদেরকে আযান দিতে দিত না। সমজিদগুলোকে তাদের ধর্মীয় গ্রণ্ঠপীঠ ও উপসনালয়ে পরিনত করতো এবং সমজিদের নাম বদলিয়ে একে ‘মস্তগড়’ বলে অভিহিত করতো। তারা মুসলমানদের ব্যবহৃত পাত্রকে অপবিত্র মনে করতো। প্রয়োজনবোধে তাতে পায়েরে জুতো দিয়ে পাঁচটি আঘাত কারার পর উক্ত পাত্র ব্যবহার করতো।
মারাঠো আন্দোলনের হোতা শিবাজী মারাঠাদেরকে উদয়পুরের রাণাদের বংশোদ্ভুত বলে-পরিচয় দিতে বলে এ আন্দোল সহজেই অভিজাত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা লাভ করে। পরবর্তী পর্যয়ে সারা ভারতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মারাঠা দস্যুদের হাতে মুসলমানদের জান-মালের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ইতিহাস খ্যাত। ‘খাযানায়ে আমেরা’ ও ‘তাবাতা বায়’ গ্রন্হে বলা হয়েছে, মারাঠা কর্তৃক দিল্লীতে লুটতরাজ এবং মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রতি যেরূপ অবমাননাকর আচরণ করা হয়, তা যে কোন মুসলমাদের জন্য বেদনার উদ্রেক করে।
মক্কায় গমন
এসব আন্দোল শাহ সাহেবের মনে গভীর রেখাপাত করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর খোদাদাদ চিন্তাশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে বর্তমান মুসলমান সমাজকে বহুমখী সমস্যার রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে হলে শধু মাদ্রাসায় বসে গতানুগতিক শিক্ষাদান করলেই চলবে না বা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কিছু বক্তৃতাও এ জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়নে সক্ষম হবে না। তিনি চিন্তিত মনে এ জন্য সঠিক পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি বার বৎসরের অধ্যাপনার কাজে বিরতি দিয়ে ২৯ বছর বয়সে ১১৪৩ কিংবা ১১৪৪ হিজরীতে পবিত্র মক্কা-মদীনা সফর গমন করেন। উল্লেখ্য যে, পবিত্র মক্কা গমনও ঐ সময় সহজ ব্যাপর ছিল না। ঠিক ঐ সময়ই পর্তুগীজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি কেউ শাসকের ভূমিকায়, কেউ বণিকের বেশে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে মুসলিম জাহানের জাহানের দিকে এগিয়ে আসছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১১৪৩-১১৪৫ হিজরীত পর্যন্ত সফরে ছিলেন ( অন্যমতে ১৪৪-১১৪৬ হিজরী)। তম্মধ্যে মক্ক- মদীনায় চৌদ্দ মাসে ও বাকী সময় যাতয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। এতে তিনি দুই বার হজ্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের সান্নিধ্যে গিয়ে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য কন্নকাটির মাধ্যমে এ জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তিনি কিরূপ প্রজ্ঞাশক্তি অর্জন করেছিলেন পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাবার সন্ধান পেয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি যে আধ্যত্মিক শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন, ‘ফয়ুযুল হারামাইন’ নামক তাঁর উচ্চঙ্গের গ্রন্হটি পাঠে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি উক্ত গ্রন্হের ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় ১১৪৪ হিজরীর ২০ শে যিলকদের জুমা রাত্রির একটি দীর্ঘ স্বপ্নের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি আল্লাহর একটি নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। নিছক বৈষয়িক ও জড়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটি বিষয়কে যারা বিচার করে তাদের নিকট ঐ বিষয়টি ভিন্নরূপ ঠেকলেও যেহেতু শাহ সাহেব নিজেই তার বর্ণনাকারী তাই এটা ব্যক্ত না করার বার্পণ্য দেখানো কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। স্বপ্নের এক পর্যয়ে বলা হয়েছে – তিনি নিজেকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে দেখতে পান। তাতে আরব-অনরব প্রায় সকল মুসলিম দেশের লোকই রয়েছে। প্রত্যেকেই মুসলমানদের ওপর ক্রমবর্ধমান বিজাতীয় প্রভাবে ক্রোধে ফেটে পড়েছে। সকলে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞস করছে যে, এ মুহূর্তে আল্লাহর কি নিদের্শ? তাঁর মখ দিয়ে তখন বের দাও। ‘অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত শাহ সাহেব পরবর্তীকালে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও লেখনীর আঘাতে তাই করেছিলেন। ঠিক অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ গ্রন্হের মুখবন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন- বৃত্তান্তের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, “আমি একদা আসরের নামাযান্তে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছি। হঠাৎ অনুভব করি যে, প্রয় নবীর পবিত্র আত্না আমাকে আচ্ছান্ন করে ফেলেছে। মনে হচ্ছিল যে, আমার ওপর কোন চাদর রাখা হয়েছে। ঐ অবস্থায় আমার অন্তরে একথা ঢেলে দেওয়া হয় যে, ‘দীনের ব্যাক্যার ব্যাপারে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করো।‘ তার পরক্ষণেই আমি আমার অন্তরে এমন এক (জ্ঞানের) জ্যেতি অনুভব করতে থাকি যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে থাকে।“
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ
শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১১৪৬ হিজরীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর যাবত শধু গ্রন্হ রচনার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। মক্ক মুয়াজ্জমা থেকে তিনি যে পরিকল্পনা নেয়ে ভারত_ভূমিতে পা রাখেন, তাঁর মন_মস্তিষ্ককে যে ভাবধারা অস্থির করে তুলেছিল, সে অবস্থার মধ্যে বহু বছরের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষাদান রীতির রুচিই তাঁর থেকে বিদায় নেয়। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করার কোন অবকাশই তাঁর আর রইল না। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীযের ভাষায়- “শ্রদ্ধেয় পিতা সকল বিষয়ের জন্য এক এক জন শিক্ষ তৈরী করে গিয়েছিলেন, যে বিষয়ের যে ছাত্র তিনি ঐ বিষয়ের শিক্ষকের নিকট যেতেন। তাঁর কাজ ছিল শুধু তথ্য জ্ঞান দান লেখা ও হাদীস বর্ণনা।“ তিনি ঐ সময়ের মধ্যে আরবী ফরসী ভাষায় ন্যূনাধিক পঞ্চাশখান গ্রন্হ রচনা করেন। এগুলো অধিকাংশই ইসলামী জ্ঞন-গবেষণা, দর্শন ও তথ্যের দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানব জীবনের তাঁর গবেষণার সবচাইতে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে এই যে তিনি দু’শো বছর আগের পরিবেশে বসেও বংশ শতাব্দীর জ্ঞন-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে লালিত-পালিতে ব্যক্তির ন্যায় সম্পুর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী জীবনবিধানের ব্যাখ্যাদান করে গেছেন। ফররুখ সিরায়, মুহাম্মদ শাহ রঙ্গীলা ও শাহ আলমেম শাসনকালীন ভারতের অশন্ত পরিবেশ সম্পর্কে ইতিহাস পাঠক মাত্রই পরিচিত। শাহ সাহেবই এমন একজন গবেষক যিনি চতুর্দিকের বিলাসিতা, ইন্দ্রয় পূজা, হত্যা, জুলুম নির্যাতন অশান্তি ও বিশৃংখলার অবাধ রাজত্বের মধ্যে বসে একজন মুক্ত বিচার_ বু্দ্ধিসম্পন্ন ভাষ্যকাররূপে যুগপরিবেশের সকল বন্ধন ও প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রতিটি সমস্যার ওপর গভীর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। শাহ সাহেব যেভাবে তাঁর গ্রন্হবলীতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাঙ্গিতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার আলোকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মূলনীতি এবং ইসলামী অনুশাসনসমূহের দার্শনিক দিক সহজেই পরিষ্ফট হয়ে ওঠে। তিনি যে ব্যাপারেই লখনী ধারণ করেছেন, মনে হয় তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যয়ে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আরবী কিংবা ফারসী উভয় ভাষায় লিখিত গ্রন্হবলীই ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রঞ্জলতা, প্রমাণ-পদ্ধতির দার্শনিক রীতি ও আবেদনশীলতার দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যর অধিকারী। বস্তু তিনি ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞানকে এমন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী ছিলেন যার মাধ্যেমে অনাগত বংশধরদের নিকট ইসলামী বিধিব্যবস্থার মূল সহস্য, তথ্য ও দার্শনিক দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এরই ভিত্তিতে মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ ও ইসলামী রাজনীতির অভ্যুদ্বয় ঘটে। এদিক থেকে চিন্তা করলে অনেকের যে কোন বৈপ্লবিক ভাবধারাপুষ্ট লেখার চাইতে তাঁর লেখনীকে অধিক বিপ্লবাত্মক বলতে হবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা ইসলামের স্বপক্ষে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাঁর উপস্থাপিত ইসলামী সমাজব্যবস্থয় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি এবং সমাজিক উন্ননের যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে সম্পষ্ট পথনির্দেশ রয়েছে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে কোন রাষ্ট্রে তা কার্যকরী করার উপযোগী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যে কোন দেশ যে কোন জাতির জন্য ইসলামই একটি শাশ্বত জীবন-বিধান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ইতিহাসের ঐ সকল মহামনীষী মহাত্মদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা যুগে যুগে মতবাদের বিভ্রন্তিজাল ছিন্ন করে চিন্তা ও গবেষণার একটি পরিচ্ছন্ন সরল রাজপথ তৈরী করেন এবং মানস জগতে সমকালীন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নতুন সৃষ্টির এমন এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র তৈরী করেন, যার ফলে অনবার্যরূপে অন্যায় ও অসন্দরের ধ্বংস সাধান এবং ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পুনগঠনের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন জন্ম লাভ করে। এ ধরনের চিন্তানায়কের পক্ষে নিজের চিন্ত ও মতাদর্শ অনুযায়ী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা খুব কমই সম্ভব হয় কিংবা বিবৃত পৃথিবীকে ভেঙ্গেচুরে স্বহস্তে একটি নতুন পৃথিবী তৈরীর জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবকাশও থাকে তাদের কম। এহেন চিন্তানায়কদের আসল কাজ হয়, তাঁরা সমালোচনার ছুরি চাপিয়ে শত শত বছরের বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন ছিন্ন- ভিন্ন করে বুদ্ধি ও চিন্তাজগতে নতুন দীপশিখা প্রজ্জলিত করেন। জীবনের বিকৃত অথচ শক্তিশালী কাঠামোকে ভেঙ্গে তার ধ্বসাবশেষ থেকে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সত্যকে আলাদা করে দুনিয়ার সম্মখে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বও (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) রীতিমতো যদ্ধ ক্ষেত্রের অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধ করত। কিন্তু চিন্তার পুনগঠনের ব্যাপারেই তাঁর সকল সময় ব্যয়িত হয়েছে। এ বিরাট কাজ থেকে তিনি এতটুকুও অবসর পানিনি। তিনি যে পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে সক্রয় প্রচেষ্টা চালাবার জন্য অন্য একদল লোকের প্রয়োগন ছিল এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তারা স্বয়ং শাহ ওয়ালিউল্লহ শিক্ষা ও অনুশীলনাগারের মধ্য থেকে শক্তি ও পরিপুষ্ট লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবগরণ করেন।
ওয়ালিউল্লাহর কর্মী দল
এখানে সেই দল ও ব্যক্তিদের আলোচনা ও তাদের কর্মতৎপরতা সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। এ আলোচানর মধ্য দিয়ে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আজকে এদেশে বা উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সেতুবন্ধন হিসাবে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৮০৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লী শাসক সম্রাট শাহ আলমকে লালকেল্লা, এলাহাবাদ ও গাজীপুরের জায়গীর ছেড়ে দিলেও এগুলোর উপর থেকে তাঁর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ক্ষমতার শেষে বিন্দুটি পর্যন্ত মুছে দেবার পূবূই ইংরেজরা সমগ্র ভারতে নিরকুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। সারা উপমহাদেশে আলিম ও গায়ের আলিম সুধী সমাজের মধ্যে এমন কারও প্রকাশ্যে এ ঘোষণা করার সাহস ছিল না যে, বিদেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে ‘দারুল হরব’ যেখানে জিহাদ করা প্রতিটি। খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য। সর্বত্র নৈরাশ্যের ছায়া ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। সকল শ্রেণীর মুসলমান কিংকর্তব্যবিমঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজগণ উপমহাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, ধ্যান- ধারণা কৃষ্টি- সংস্কৃতির প্রসারে দান ও এদেশের ঐতিহ্যবাহী শাসক জাতি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যমুখী করে গড়ে তোলার জন্য গভীর পরিকল্পনা নিয়োজিত ছিল। মুসলমানদের ঐ সময়টি এক কঠিন পরীক্ষা।
ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী ফতওয়া
ঠিক ঐ সময় শাহ ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের প্রধান এবং ওয়ালিউল্লাহর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয দেহলভী এক বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করে এই হতেদ্যম জাতিকে পথের সন্ধান দেন এবং তাদেরকে ইসলামের জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানান। শাহ আবদুল আযাযী তাঁর পিতা মহামনীষী ও ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর তিরোধানের পর ( ১৭৬৭খৃস্টাব্দ ) দিল্লীর রহিমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ওয়ালিউল্লহর চিন্তাধারার প্রচার, জনসংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে ‘তারগীবে মোহাম্মদী’ নামে ইসলামী পুনর্জগারণ আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন। এই নির্ভী মুজাহিদ দ্বর্থহীন কণ্ঠ ঘোষণা করলেনঃ
“ এখানে অবাধে খৃস্টান অফিসারদের শাসন চলছে আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো তারা দেশরক্ষা, জননিয়ন্ত্রণবিধি, রাজস্ব, খেরাজ, ট্যাক্স উশর, ব্যবসায়পণ্য, দন্ডবিধি, মোকদ্দামার বিচার, অপরাধমূলক সাজা প্রভৃতিতে নিরুকুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ সকল ব্যপারে ভারতীয়দের কোনই অধিকার নেই। অবশ্য জুমার নামায, ঈদের নামায, গরু জবাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন না। কিন্তু এগুলোতো হচ্ছে শাখা-প্রকাশ যেসব বিষয়ে উল্লেখিত বিয়ষসমূহের এবং স্বাধীনতার মূন ( যেমন মানবীয় মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার) তার প্রত্যেকটিই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে। মসজিদসমুহ ধ্বংস করা হচ্ছে, কি হিন্দু কি মুসলমান পাসর্পোট পারিমিট ব্যতীত কারও শহরে আগমন- নির্গমনের সুযোগ নেই। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদেরকে শহরে আসা-যাওয়ার অনুমতি দানও দেশের স্বার্থে কিংবা নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থ দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য হায়দ্রাবাদ, লাক্ষ্ণৌ ও রামপুরের শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের আনগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় সরাসরি খৃস্টান সরকারের আইন সেখানে চালু হয় নাই কিন্তু এতেও গোটা দেশের উপরে দারূল হরবেরই হুকুম বর্তবে।“
[ফতওয়া- এ আযীযী ( ফারসী, পৃষ্ঠা ১৭ মুজতবায়ী প্রেস।] এমনিভাবে তিনি অন্য একটি ফতওয়ার মধ্যেও অবিভক্ত ভারতকে ‘দারুলহরব’ বলে ঘোষণা করেছেন। এই ফতওয়া যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যার সারর্মম দাঁড়ায় এই যে, আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা খৃস্টানদের হাতে তারা ধর্মীয় মুল্যবোধকে হরণ করেছে। কাজই প্রতিটি দেশপ্রমিকের কর্তব্য হলো বিদেশী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নানাভাবে সংগ্রাম করা এবং লক্ষ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখা
ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ার প্রভাব
সাধারণ মুসলমানগণ এ যাবত যেখানে ইংরেজদের প্রতাপের সমানে নিজেদেরকে অসহায় মনে করতেন এবং দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত ছিলেন এ ফতওয়া প্রকাশের পর মুসলমানরা কর্মনীতি নির্ধারণের পথ খুঁজে পেলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দর দ্বারা উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানের নিকট এই বিপ্লবী ফতওয়ার বাণী প্রচারিত হয়। আর এমনিভাবে মুসলমানদের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজেদের বিরুদ্ধে জিহাদীভাব জাগ্রত হতে থাকে।
পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাঁরই শিষ্য সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা মওলানা আবদুল হাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা ইসমাইল (শহীদ)_ এর সেনাপতিত্বে (আনু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) বিরাট মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়। এই মুজাহিদ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (শিখ ও পরে ইংরেজ) দের বিরুদ্ধে জিহাদ করা । তাঁরা এ উদ্দেশ্য পূর্ব ভারত কিংবা দক্ষিণ অথবা উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পেশোয়ার কাশ্মীর এলাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের এ আন্দোলনে পূর্বে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাসমুহ (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, সিলেট প্রভৃতি জেলা) থেকেও মুলমানরা যোগদান করেছিলেন। বাংলাদেশেও বিলুপ সাড়া জাগিয়াছিলো। যার ফলে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ফরিদপুরের হাজী শরীয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন নামে এক শাক্তিশালী ইসলামী আন্দোল গড়ে উঠেছিল। প্রায় ঐ সময়ই মুজাহিদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার মাওলানা হাজী তিতুমীর (নেছার আলী) ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে বহু স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মওলানা হাজী তিতুমীর ছিলেন ‘শহীদে বালাকোট’ সাইয়েদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ১৮৩১ খৃস্টাব্দে (সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী যে সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন ঐ সালেই বাংলাদেশে) ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হন। সাইয়েদ আহমদ শহীদের শিষ্য মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ) বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা_ সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচারে বিরাট কাজ করেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী শিক্ষা- সংস্কৃতির প্রভাব দূর করেন। এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর হয়ে থাকবে। যা হোক, মুজাহিদ বাহিনীর নেতা সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী জাহাদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় ও অন্যান্য দেশের মুসলিম মনীষি ও ইসলামী শাক্তির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৮১৯ খৃস্টাব্দে মক্কা শরীফে হ্জ্জ করতে যান। ১৮২৩ খৃঃ তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে থেকে এসেই ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর দলের প্রতিটি মুজাহিদকে তিনি ইসলামের সোনালী যুগের কর্মীদের আদর্শ গঠন করতে চেষ্ট করেন। তাঁদের রাত্র দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভোর প্রচার কার্য, দিবাভাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম ও রাত্রিতে তাহাজ্জুদ ও অন্য ইবাদতে জাগরণএসব ছিল এই খোদাভক্তদের দৈনিক সাধারণ কর্মসূচী। অবিভক্ত ভারতের সবত্র জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা শেষ করে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ১৮২৬ খৃস্টাব্দে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে সময় মুজাহদদের সংখ্যা ছিল এক লাখ। তাঁরা গষনী, কাবুল ও পেশোয়ার হয়ে নওশেরায় হাজির হন। শিখরা ইংরেজদের সাথে গোপনে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্ব পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। শিখরা শেরসিংহ ও জনৈক ফরাসী জেনারেলের অধীন প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পনজতারে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে মুকাবিলা করে। এ যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হয়ে পালয়ন করে এবং মুজাহিদ বাহিনী পেশোয়ার আধিকার করে-১৮৩০ খৃস্টাব্দ) এভাবে বালাকোট যুদ্ধের আগ পযর্ন্ত আরও বহু যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শিখদের শিখদের সঙ্গে জড়িত হন। শেষ পরর্যয়ে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাড়িয়েছিল তিন লাখে। রণজিৎ সিংহের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করার পর মুজাহিদরা পেশোয়ার অধিকার করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ মাযহার আলীকে প্রধান বিচারপতি ও কাবুলের সলতান মুহাম্মদকে প্রধান প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন।অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ মাযহার আলীকে প্রধান বিচাপতি ও কাবুলের সুলতান মুহাম্মদকে প্রধান প্রশাসন নিয়োগ করেছিলেন। এ নবগঠিত ক্ষুদে ইসলামী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজ কবলিত সাবেক ‘দারুল ইসলাম ভারত পুনরুদ্ধরের জন্য আরও
অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক ঐ সময় পরাজিত রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শঠাতার আশ্রয় নেয়। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সীমান্তে পাঠান ও উপজাতীয়দেরকে তাঁর দলছাড়া করার চেষ্টা করে। সাইয়েদ আহমদ কুসংস্কার বিরোধী ছিলেন। ফলে অনেক পাঠান ও উপজতীয় লোক অর্থলোভে বা কুসংস্কারবশত অকপটে এ আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটে নামক স্থানে শিখদের সঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে খুবি খা নামক এক পাঠানের বিশ্বাসঘাতকতায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী এ মওলানা ইসমাইল দেহলভী শাহাদত বরণ করেন। তারপরও এই ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীরা দমেননি। সীমান্তের ইয়াগিস্তানের সিত্তানায় সাইয়েদ সাহেবের বিশ্বস্ত খলীফাদের নেতৃত্ব সমবেত হন। সাইয়েদ সাহেব শাহাদাতের পূর্বে বালাকোটের রণাঙ্গন থেকে তাঁরই বিশিষ্ট খলীফা মওলানা বেলায়েত আলী আজীমাবাদীকে ভারতের অভ্যন্তরে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনার পর মওলানা বেলায়েত আলী তাঁর ভ্রাতা মওলানা এনায়েত আলী এ অপর বিশিষ্ট নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী বহু কষ্টে সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করে ইয়াগিস্তান থেকে শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধ সাড়ে চার বছরকাল স্থায়ী থাকে। অতপর ইংরেজ সরকার সরাসরি এতে হস্তক্ষেপ করে অনেক মুজাহিদকে গ্রেফতার করে-কাউকে শহীদ করে, কারুর প্রতি চলে অমনুষিক নিযাতন। অবশ্য ভারত সীমান্তের বাইরে থেকে মুজাহিদদের এক দল সব সময়ই সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বালাকোটের সাময়িক ব্যর্থতা, নেতৃবৃন্দের শাহাদত ও পরবর্তী পর্যয়ে মুজাহিদ বাহিনীর উপর ইংরেজদের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও এই সংগ্রামী বাহিনীর কর্মীরা নিশ্চুপ বসে থাকেননি। তাঁরা বিভিন্নভাবে উপমহাদেশের মুসুলমানদের মধ্যে ইসলামেরে শিক্ষা, আদর্শ প্রচার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করে গেছেন। শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক প্রচারিত সেই দারুল হরবের ফতওয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর অসুসারিগণ কর্তৃক স্বল্পকাল স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও বালাকোটের লড়াই এবং তারপরও বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যেমে ইংরেজ বিরোধীভাবে জাগ্রত করা-এসব কিছুই ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে_যারা সূচনা করেছিলেন শুকরের চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটা ব্যবহার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বেরাকপুরের মুসলিম সৈন্যগণ। এই বিপ্লবকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেলও মূলত সেটাই ছিল উপ-ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আক্যায়িত করেলও মূলত সেটাই ছিল উপমহাদেশের প্রথম বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আযাদী আন্দোলন এবং অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার ব্যাপারে প্রচণ্ড আঘাত।
আধুনিক অস্ত্র, পারস্পরিক ঐক্যের অভাব ইত্যাদি করণে এ বিপ্লব ব্যর্থ হয়। ও বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ সংগ্রামী আলিমরাই নানা কৌশলগত কারণে নেতৃত্বদানকারী অনেক আলিমের নাম সেই সময় উহ্য ছিল বিধায় অনেক ঐতিহাসিকের লেখাতে তাঁদের মধ্যে মওলানা ইয়াহইয়া আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বালাকোট মুজাহিদ বাহিনী অন্যতম নেতা হিসেবে ১৮৫৭ সালের ইসলামী বিপ্লবে পরোক্ষভাবে প্রধান নেতার আসনে সমসীন ছিলেন। ভারতের অভ্যন্তরে ঐ সমকার এ ইসলামী বিপ্লবের গতিধারা তাঁর দ্বারাই অনেকটা নিয়ন্ত্রত হতো। ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মীদের এ দান আমাদের দেশের কোন কোন অজ্ঞতা বশত কিংবা ইর্ষাপরায়ণতার কারণে উপেক্ষা করলেও অনেক হিন্দু লেখক এবং বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হান্টারও অস্বীকার করতে পারেননি। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে সবচেয়ে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। হিন্দুরা ইতিপূর্বেই ইংরেজদের সহযোগিতায় লেগে গিয়েছিল সেই মুসলমানদের পক্ষ থেকেই। তাই মুসলমানদের রাজনেতিক জীবনের ন্যায় তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও সংকীর্ণ এ দুর্বিসহ হয়ে উঠে- যাবতীয় আধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। ইংরেজরা বিপ্লবের জন্য একমাত্র মুলমানগকেই দায়ী করে তাদেরই উপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাতে থাকে। বিপ্লবের নায়ক এ কর্মী শত শত আলিম ও হাজার হাজার সাধারণ মুসলমানগণ এ জন্য ইংরেজদের রোষানলে পড়ে ফাসিঁকাষ্ঠ ঝুলেন, কেউ মাল্টা বা আন্দোলন দ্বীপে নির্বাসিত হন, কেউ দীর্ঘকাল যাবত কারা অন্তরালের আধাঁর কক্ষে তিলে ক্ষয় হন। এক তথ্যে দেখা যায়, বিপ্লবের পরে একস্থানে ২৮ হাজার মুসলমানকে ফাসিঁ দেয়া হয়, এবং শত শত আলিম শাহাদত করণ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে বালাকোট আন্দোলনের মুজাহিদ ও তাঁদের ভাবশিষ্যরা সংগ্রামের পথ ছেড়ে দেননি। তাঁরা একদিকে সীমান্তের ইয়াগিস্তানে যুদ্ধে অব্যাহত রাখেন, অপরদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহর সুযোগ্য বংশধর সাইয়েদ সাহেবের মন্ত্রশিষ্য মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্ব ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজদের চুক্ষ এরিয়ে শিক্ষা –সংস্কৃতি ও জিহাদের অনুকূলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ চলিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধারা স্থনে স্থানে মাদ্রাসা কায়েম এবং ধর্মীয় সভা-সমিতির মাধ্যেমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি মূল্যবোধের প্রচার, জিহাদী প্রচারণা ও জাগরণকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। বস্তুত সে প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমরা দারুল উলুম দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যলয়ের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখতে পাই। এগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অসংখ্য শিক্ষা ও জিহাদী প্রতিষ্ঠন গড়ে উঠা এবং উপমহাদেশ ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ উন্মক্ত হয়। উত্তরকালে “অসযোগ আন্দোলন’ ও খিলাফত আন্দোলন”কে উপলক্ষ করে মুসলমানদের মধ্যা আযাদী আন্দোলনের যে সাড়া জাগে এবং ১৯৪৭ ইং সালে ইসলামের নামে আমরা যে পাকিস্তান অর্জন করি এর প্রত্যাকটি ঐ সকল কাজের অনিবার্য ফল বৈ কিছু নয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী খিলাফতও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিভক্ত পাকিস্তান দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিভিন্নভাবে যে প্রচন্ড আন্দোলন চলে, সেটাকোট ও১৮৫৭ সালের মুজাহিদদেরই ভাবশিষ্যদের দ্বারা পরিচালি বলতে হবে। মোটকথা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয দেহলভী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ মওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী ও মওলানা আবদুল হাই প্রমখ ইসলামী আন্দোলনের অগণিত বীর সিপাহী যে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, উপমহাদেশের সমকালীন প্রতিটি ইসলামী আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা তারই পরিশিষ্ট।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) -এর কাজ চিন্তাধারা
পবিত্র মক্কয় অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম রাষ্ট্রর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্থান- পতনের খবরাখবরের আলোকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহাযো শাহ ওয়ালিউল্লাহর নিকট এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল যে, জীবনাদশের অন্তনিহিত শক্তি ছাড়া কেবলমাত্র রাষ্টীয় ক্ষমতাই কোন জাতিকে বাচিয়ে রাখতে পারে না। অন্যথায় বহুশত বছর যাত দোর্দন্ড প্রতিাপে শাসনদন্ড পরিচালনা করার পরও মুসলিম মিল্লাতের এ দুরবস্থা কেন? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র ইসলামের অন্তনিহিত শক্তির দ্বারাই মসলমানরা দুনিয়ার দিকে দিকে বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই মুসলিম জাতির উপযোগী রাস্ট্রয় পরিকল্পনা পেশ করার সাথে সাথে ইসলামী শক্তির বাদের একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখাও মানুষের সামনে পেশ করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারলেই মুসলমানগণ তাদের গৌরবোজ্জল অতীতকে ফরে পাবে-লাভ করবে তার আদর্শ জীবন, আর এভাবেই জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে সমর্থ হবে। রাজতান্ত্রিক পরিবেশের প্রতিকূতার মধ্যে সৃষ্ট বিশেষ এক সকম সুফী ভাবধারার ক্রমবিকাশের ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের যে অসম্পূর্ণ রূপে ফুটে উঠেছিল, তার কারণে অধিকাংশের মধ্যেই এ ধারণা বদ্ধমুল হতে চলেছিল যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তথা রাজনীতি এ ধর্ম আলাদা জিনিস, ব্যক্তিগততভাবে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কতিপয় বিধি-বিধান পালিত হলেই মানুষ পরকালে মুক্তি পাবি, আর রাজনীতি দুনিয়াদারির ব্যাপার, এটা দুনিয়াদারদের জর্নই শোভা পায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছেন। তাঁর মতে মানুষের পার্ধিব ও পারলৌকি উভয় জীবনের উন্নতি সাধনই নবুওতের মূল্য। তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদে দেখতে পাই, যখন কোন জাতির নৈতিক অবনতি ঘটেছে তখনই তাদের মধ্যে নবী- রসূলের আগমন হয়েছে আর তাদের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে চলার ফলে জাতির নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আর্থিক তথা জাগতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তার মতে, দীনের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে কোন তফাত নেই। জাতীয় উন্নতি বলতে নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতি দু’ই বুঝতে হবে। মুসলমান জাতির ক্রমোন্নতির ইতহাসই তার সাক্ষ্য। এ জন্যই পবিত্র কুরআনের ভাষায় মুসলমানদের এ বলে মুনাজাত করতে বলা হয়েছে যে, ‘হে আমাদের প্রতপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া এ আখিরাতের কল্যণ দান করো।,
যা হোক মানব জীবনের সার্বিক উন্নতিকল্পে ইসলামকে জীবনের পরিপূর্ণ একটি বিজয়ী ও শক্তিশালী আদর্শ হিসাবে তুলে ধারা জন্য খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের এ শ্রেষ্ঠ চিন্তনায়ক দার্শনিক হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর নতুন পরিকল্পনা মাফিক ইসলাম সম্পর্কে যেসব অমর গ্রন্হ রচনা করে গেছেন, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষ করা যায় (১) সমালোচনা ও সংশোধনমূলক বিষয়, (২) গঠনমূলক বিষয় (৩) এসবের আলোকে গণসংগঠন। তবে যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে, যে তৃতীয় বিষয়টির প্রতি হাত দেয়ার সময় তাঁর হয়ে উঠেনি, কিন্তু তাঁর রচনায় এদিক ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তাঁর কাজ ও চিন্তাধারার প্রথম দু’টি বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনার প্রয়াস পাবে।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) মক্কা থেকে আগমনের পর নতুন পরিকল্পনা মাফিক যেসব সংস্কারমূলক কাজ করেন প্রধানত ঐগুলোকে দু’ভাগে বিভক্ত করা চলে (১) সমালোচনা ও সংশোধনমূলক এবং (২) গঠনমূলক। বিশেষজ্ঞদের মতে শাহ ওয়ালিউল্লাহই প্রথম ব্যাক্তি যাঁর দৃষ্টি ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানের ইতহাস- এ সূক্ষ্ণ ও মৌল পার্থক্য পযর্ন্ত পৌছেছে, যিনি ইসলামী ইতিহাসের দষ্টিভঙ্গি দিয়ে মুসলিম ইতিহাসের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং যিনি এ কথা অবগত হবার চেষ্ট করেন যে, বিভিন্ন শতকে ইসলাম গ্রহণকারী জাতিদের মধ্যে আসলে ইসলামের কি অবস্থা ছিল। এটা অত্যন্ত জটিল বিষয়বস্তু। অতীতেও এ ব্যাপারে কিছু লোক বিভ্রান্তির শিকার হন এবং আজও হচ্ছেন। এ ব্যাপারে ‘ইযালাতুল খিফা [ ১২৮৬ হিজরীতে বেরিলী থেকে প্রকাশিত সংস্করণ] গ্রন্হের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠায় তিনি ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম ইতহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রত্যেক যুগের বিশেষত্ব এবং উদ্ভুত ফিতনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ উব্ধত করেন। তাতে তিনি মোটামুটিভাবে মুসলমানদের আকীদা, বিশ্বাস শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও রাজনীতি সংমিশ্রিত সকল প্রকার জাহিলিয়াতের দিকে অঙ্গুলি নিদের্শ করেন। অতপর যাবতীয় ক্রটির মধ্য থেকে যেগুলো মৌলিক এবং সকল ক্রটির উৎস, এমন দু’টির প্রতি অঙ্গুলি নিদের্শ করেন। এক নবুওত পদ্ধতির খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক কর্র্তত্বের গতি পরিবর্তন। দুই, ইজতেহাদের প্রাণ শক্তির মৃত্যু ও মনে মস্তিষ্কর উপর অন্ধ অনুসারিতার আধিপত্য। প্রথমটির ব্যাপারে তিনি। বর্ণিত কিতাবে রাজতন্ত্রের নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে এমন সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন এবং হাদীসের সাহায্যে তার এমন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রধান করেন যে, তাঁর পূর্বেকার লেখকদের রচনায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লবের ফলাফলকে তিনি যেরূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, পূর্ববর্তীদের রচনায় তেমনটি দেখা যায় না। এক স্থানে তিনি লেখেনঃ “ইসলামের মূল স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিরাট ক্রটি পরিলক্ষিত হয়েছে। হযরত উসমান (রা) এর পর কোন শাসক হ্জ্ব কায়েম করা ইসলামে অপরিহার্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সিংহাসনে আরোহণ করা, রাজমুকুট পরিধান করা এবং অতীত রাজা- বাদশাহদের আসনে বসা যেমন কায়সার ও কিসরার জন্য রাত্বের প্রতীকরূপে পরিগণিত হতো, তদ্রপ নিজের কর্তৃকত্ব হজ্ব প্রতিষ্ঠ করা ইসলামে খিলাফতের প্রতীক হিসাবে পরিচিত।“ ( ইযালাতুল খিফা- ১ম খন্ড, ১২৩- ১২৪ পৃষ্ঠা)
অতপর তিনি ‘ইযালা’ গ্রন্হের ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেনঃ “এদের সরকার অগ্নিপুজকদের সরকারের ন্যায়। শুধু পার্থক্য এ জায়গায় যে, এরা নামায় পড়ে এবং মুখে কলেমায়ে শাহাদত উচ্চরণ করে। এ পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের জন্ম। জানি না, পরবর্তীকালে আল্লাহ আরও বা কতকিছু দেখান। এ ব্যাপারে “ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা”‘বদুরে বাজেগাহ “তাফহীমাত’“মুসফফা’ ও তাঁর অন্যান্য গ্রন্হ আলোচনা রয়েছে।
দ্বিতীয় ক্রটি অর্থাৎ কোন ব্যাপারে নিরপক্ষ এ মুক্ত চিন্তা নিয়ে কুরআন ও সুন্নহর সঠিক অনুশাসন বা তার অনুকূলে বিধানের খোঁজ না নিয়ে অন্ধভাবে অপরের অনুসরণ করা। এ ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) আলোচ্য গ্রন্হের ১৫৭ পৃষ্ঠা বলেনঃ
সিরীয় শাসকদের ( উমাইয়া সরকার) পতনকাল পর্যন্ত কেই নিজেকে হানাফী বা শাফেয়ী বলে দাবী করতো না। বরং সবাই নিজেরদর ইমাম ও শিক্ষকগণের পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। ইরাকী শাসকদের ( আব্বাসীয় ) আমলে প্রত্যেকেই নিজের জন্য আলাদা নাম নির্দিষ্ট কের নেয়া। তাদের অবস্থা এ পর্যয়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, নিজ নিজ মাযহাবের নেতাদেরর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তারা কোন কিছুর সিদ্ধান্ত করতো না। এভাবে কুরআন ও সুন্নহার ব্যাপারে ব্যাপারে অনিবার্যরূপে যেসব মতবৈষম্যের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলো স্থায়ী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতপর আরব শাসকদের পর যখন তুর্কী শাসনামলে মানুষ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রত্যেকেই ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাব থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রত্যেকেই ফিকহ ভিত্তিক মাযহাব থেকে যা কিছু স্মরণ করতে সক্ষম হয় ঐ টুকুকেই নিজেদের আসল দীনে পরিণত কর। পূর্বে যে সকল বস্তু কুরআন ও হাদীসের সূত্র উদ্ভূত মাযহাব ছিল, তখন তা স্থায়ী সন্নহতে পরিণত হয়েছে।‘ তিনি ‘মসফফা গ্রন্হের ১ম খন্ডের ১১ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ আমাদের যুগের সরল লোকেরা ইজতিহাদ থেকে বিমূখ। এদের নামে। তাদের ব্যাপার্ই আলাদা। ঐসব ব্যাপার বুঝার যোগ্যই নয়। শুধু অন্ধনুসরণ না করে স্বাধীন ও মুক্ত বিচারবুদ্ধি নিয়ে কুরআন-সান্নাহ থেকে সমস্যার মসধান খোঁজ করা সম্পর্কে “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা”র সপ্তম অধ্যায়ে ও “আল-ইনসাফ” গ্রন্হে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্ধনুসরণের ও ব্যাধির পূর্ণ ইতিহাসে তাতে বিবৃত হয়েছে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় ক্রটির প্রতি তিনি অঙ্গুলি নিমের্শ করেছেন, যা পরে বিবৃত হচ্ছে।
সমসাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা
সমালোচনার উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ দু’টি বিষয়ের উদ্ধুতির পর সংক্ষেপে তাঁর সমকালীন পরিস্তিতি সম্পর্কিত সমালোচনামূলক কয়েকটি উদ্ধুতি নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছেঃ
১. সূফীবাদের একটি ত্রুটির সমালোচনা
“অনুভূতির পূজা সুফীদের জনপ্রিয়তা এ তাদের ভক্তদলে শামিল হাবার কারণে এর উদ্ভব হয়েছে। মাশরিক ও মাগরিবের সমগ্র এলাকায় এ জিনিসটি ছেয়ে আছে। এমনকি সুফীদের কথা ও কর্ম সাধারণ মানুষের মনের উপর কুরআন ও সুন্নাহ তথা সবকিছুর চাইতে অধিক আধিপত্যশালী। তাদের তত্ত্বকথা ও ইঙ্গিতসমূহ এত বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, কেই এগুলোকে অস্বীকার কিংবা এর প্রতি আমল না দিলে সে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না এবং ‘নেককার’ ও মুত্তাকীদের মধ্যে গণ্য হয় না। মিম্বরের উপর দাড়িয়েঁ এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, সুফীদের ইশারা-ইঙ্গিত সম্বলিত বক্তুতা করে না। মাদ্রাসায় অধ্যাপনারত এমন কোন আলিমও নেই, যে তাদের কথায় বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ না করে। অন্যথায় তারা নির্বোধ বিবেচিত হয়।
২. অযোগ্য পীর ও পীরজাদাদের কঠোর সমলোচনা
‘কোন যোগ্যতা ছাড়াই যেসব পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীন হয়েছে, তাদেরকে আমি বলিঃ ‘তোমরা কেন এসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো? তোমাদেরকে প্রত্যকেই নিজের নিজের পথে ( তরীকা) চলেছো কেন? আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদ (সা) কে যে পথে বাতলিয়ে দিয়েছেন সেটি পরিত্যাগ করেছো কেন? তোমাদের প্রত্যেক এক একজন ইমামে পরিণত হয়েছে। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। নিজেদেরকেই হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতকারী মনে করছে অথচ নিজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। পর্থিব স্বার্থের গরজে যারা মানুষকে ‘বয়’আত’ করায় তাদের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ঠ নই। আর যারা দুনিয়ার স্বার্থে ইলম হাসিল করে অথবা, মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে, তাদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আমরা সন্তুষ্ঠ নই। তারা সবাই দস্যু, দাজ্জাল, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত। (তাফহীমাত)।
বস্তুত এ কারণেই কেউ বলে যে, তাসাউফের বিরুদ্ধে ভারতে সর্বপ্রথম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহই বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তার বিপরীত। আসলে তিনি ইসলামের খাৎটি তাসাউফ যাকে কুরআনের ভাষায় ‘তাযকিয়ায়ে নাফস’ বলা হয়েছে তাকে বহিরাগত আবর্জনা মুক্ত করেছেন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যা নির্ভেজাল তাসাউফ তিনি তাই পেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, শাহ ওয়ালিউল্লাহ যদি তথাকথিত তাসাউফের এরূপ সমালোচনা ও তার সঠিক রূপরেখা তুলে না ধরতেন, তাহলে পাশ্চাত্য লেখকরা যেভাবে একে “বিভিন্ন দেশ ও ধর্ম এমনকি ভারতীয় যোগীদের ভাবধারা থেকে ধার করা” পর্যন্ত বলে হালকা করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তার ফলে আজ তার অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দোহ।
৩. শিক্ষা পদ্ধতির ক্রটির প্রতি নির্দেশ
“নিজেদেরকে ওলামা (শিক্ষিত) আখ্যাদানকারী জ্ঞানার্জনকারীদের বলিঃ “নির্বোধের দল, তোমরা গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানতিক-বালাগত তথা ন্যায়শাস্ত্র ও অলংকাল শাস্ত্রের গোলক ধাঁধাঁয় আটকে পড়েছো। আর ধরে নিয়েছো যে, জ্ঞান কেবল এগুলোতেই আছে। অথচ সত্যিকার বিদ্যা আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতে এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নাতের মধ্যে নিহিত। তোমরা পূর্ববর্তী ফকীহগণের খুটিঁনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনাবলীতে ডুবে গিয়েছো। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যা বলেছেন সেটিই একমাত্র হুকুম। তোমাদের বেশিরভাগ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, নবীর কোন হাদীস যখন তাদের নিকট পৌছে তখন তারা তার উপর আমল করে না।“
আলিম সমাজের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেছেনঃ “তোমরা আল্লাহর বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। ইসলামের নমনীয়তাকে তোমরা উপেক্ষা করছো।“
৪. কুরআন-হাদীসের শিক্ষার প্রত গুরুত্ব আরোপ
ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের উপরই জাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ জন্য তিনি এ দিকে বিশেষ মনোযোগ দান করেন এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা ফার্সীতে কুরআন মজীদ ও ‘মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক’- এর তরজমা করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে উর্দু ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসীর করেন।
কুরআন মজীদ অধ্যয়েনের পর যাতে হাদীসের জ্ঞান লাভ করা যায় তিনি তদ্রুপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। একমাত্র শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র ও তাদেঁর শাগরিদদের প্রচেষ্টায়ই উপমহাদেশে ‘ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রসার ঘটে।
মিসরের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, আল্লমা রশীদ রেযা এ সম্পর্কে বলেনঃ “মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশে হিজরী দশম শতক থেকেই ‘ইলমে হাদীসে’র প্রচার হ্রাস পেতে থাকে। অথচ আমাদের ভারতীয় ভাইগণ বহু পরিশ্রমে উক্ত ইলেমকে জিন্দা রেখেছেন।“
৫. ইমাম সাহেবের প্রতি রক্ষণশীল ধর্ম ব্যবসায়ীদের হামলা
সত্যের ধারকরা যুগে যুগেই স্বার্থপর কিংবা রক্ষণশীলদের নির্যাতনের শিক্ষার হয়েছেন। ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীও এ থেকে রেহাই পাননি। এক শ্রেণীর মতলববাজ ধর্ম ব্যবসায়ী আলিম ও পীর ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থ নষ্ট হবার আশংখায় ইমাম সাহেব কর্তৃক কুরআন তরজমা করণের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা চিরাচরিত্র কায়দায় তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত হয়। এমনকি, একবার তিনি ফতেহপুর মসজিদে অবস্থানকালে এই গোঁড়া প্রকৃতির ধর্মব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে তাঁর উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। ঐ সময় তাঁর নিকট শুধু একটি কাঠের টুকরা ছিল। তিনি তা হাতে নিয়ে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করে সকলকে স্তব্ধ করে দেন এবং তাদের মধ্য দিয়েই নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন।
৬. শাসকদের প্রতি
-তোমরা আরাম আয়েশে লিপ্ত হয়ে সাধারণ গণমানুষকে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবার সুযোগ দিচ্ছো। প্রকাশ্যে শরাব পান চলছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার, জুয়া ও শরাবের আড্ডা চালু হচ্ছে অথচ তোমরা এগুলো বন্ধ করো না। এ বিরাট দেশে কাউকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা যাকে দুর্বল মনে করো তাকে খেয়ে ফেলো, যাকে শক্তিশাল মনে করো, তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান অভিমান এবং গৃহ-বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে গিয়েছো। একবার আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমীর-ওমরাহরা নিজেদের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছো। যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তোমরা সেই জনগণের অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছো না। দায়িত্বহীনতার ফলে (সমাজের) এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর উপর বেপরোয়া জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে’’
৭. জিহাদের জন্য আহ্বান ও তার মূল লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ
“বর্তমান অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের পক্ষে শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে আপোষহীন মনোবল নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদে ঝাপিয়েঁ পড়া দরকার। অত্যচারীরা পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখা কর্তব্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হবার পর তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হবেন এবং সাধ্য মতো সংগ্রাম করে দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান প্রতিস্ঠা করবেন, তখনই দেশের দিকে দিকে দেখা দিবে প্রকৃত শান্তি। তার ফলেই আমাদের জীবন হবে আনন্দমুখর ও সাফল্যমন্ডিত।“
৮. সৈনিকদের উদ্দেশ্য
“আল্লাহ তোমাদের জিহাদ করার জন্যে, সত্যের সুমহান বাণীকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে এবং শিরক ও মুশরিকদের শক্তি খতম করার জন্য সৈনিকে পরিণত করেছেন। তোমরা ঐ কর্তব্যকে অবহেলা করে নিছক ঘোড়সওয়ারী ও অস্ত্রশজ্জা করাকেই নিজেদের পেশায় পরিণত করেছো। অর্থোপার্জন করার জন্যে তোমরা সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছো।“
৯. শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থার সমালোচনা
“বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রতিপালক থেকে গাফিল এবং এ সংঙ্গে শিরকে লিপ্ত রয়েছো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল সে নিজের খানাপিনা ও পরিচ্ছদে বেশী খরচ করে। ব্যয় অনুপাতে আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় অপরের অধিকার নষ্ট করে।“
১০. আলিম সমাজের প্রতি
“তোমরা আল্লাহর বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। তোমরা ব্যাপকতার জন্যে আদিষ্ট –সংকীর্ণতার জন্য নয়।“
এভাবে তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু রীতি-নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যারা পরলোকগত বুযুর্গের দরবারে গিয়ে তার নিকট কিছু চায়, তারা ব্যাভিচারের চাইতে বড় অপরাধে অপরাধী বলে উল্লেখ করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কত গভীরভাবে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করেছেন।
গঠনমূলক কাজ
গঠনমূলক কাজের মধ্যে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো, তিনি ফিকাহ্ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রে একটি যুক্তিপূর্ণ মধ্যপন্থা পেশ করেন। এতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী একটি বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অন্য একটি মতের সমালোচনা করা হয়নি। একজন গভীর অনুসন্ধানকারীর ন্যায় তিনি সকল ফিকাহ্ ভিত্তিক মাযহাবের নীতি-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনভাবে রায় প্রদান করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মাযহাবী বিরোধের প্রবণতা হ্রাস এবং মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে অনুসন্ধান ও ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি সকল মাযহাবের মধ্যে সমঝোতা, বিশেষ করে শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবদ্বয়কে একটি মাযহাবের রূপ দিতে প্রয়াসী ছিলেন। ‘তাফহীমাত’ এবং ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা’ ও ‘আল ইনসাফ’-এ এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এই মধ্যপ্রন্থা গ্রহণ করার ফলে বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, অন্ধ অনুসৃতি ও অনর্থক দীর্ঘ আলোচনায় সময় ক্ষেপণের অবসান ঘটে। আর এরই মাধ্যমে নানা মতের মুসলিমদের একটি গতিশীল জীবন্ত জাতি হিসেবে বিশ্বে দাঁড়ানো সম্ভব। এ জন্যেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইজতিহাদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
ইজতিহাদ
‘মুসাফফা’ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেনঃ “ইজতিহাদ প্রতিযুগে ‘ফরযে কিফায়া’। এখানে ইজিতহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধানাবল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন এবং সেগুলোর বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের আইন-কানূনকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোন বিশেষ মাযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজতিহাদ প্রতি যুগে ‘ফরযে কিফায়া’ হবার যে কথা বলছি তা এ জন্যে যে, প্রতি যুগে অসংখ্য স্বতন্ত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ জানা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর ইতিপূর্বে যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে। তা এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয় না বরং তার মধ্যে নানান মতবিরোধও থাকে। শরীয়তের মৌল বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করলে এ মত বিরোধ দূর করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাও মাঝপথে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।“
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) ইজতিহাদের উপর কেবল জোরই দেননি, বরং বিস্তারিতভাবে ইজতিহাদের নিয়ম-রীতি, সংবিধান ও শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। ‘ইযালাতুল খিফা’‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’, ‘ইকদুল জীদ’, ‘আল ইনসাফ’, ‘বদুরে বাযেগা’, ‘মুসাফফা’ প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও তার নিছক ইঙ্গিত এবং কোথাও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার গ্রন্থ পাঠে মানুষ ইজতিহাদের কেবল রীতি নিয়মই শিখতে পারে না, এ বিষয়ে শিক্ষা লাভও করতে পারে।
উল্লেখিত কাজ দু’টি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছেন। কিন্তু যে কাজ তাঁর পূর্বে আর কেউ করেননি তা হলো এই যে, তিনি ইসলামের সমগ্র চিন্তা, নৈতিক সাংস্কৃতিক ও শরীয়ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেস্টা করেছেন। এ কাজের ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছেন। যদিও প্রথম তিন চার শতকে অনেক বেশী ইমামের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাদেঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাদেঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাদেঁর চিন্তারাজ্যে ইসলামের জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ছিল এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও এমন অনেক অনুসন্ধানকারী গবেষকের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যাদেঁর সম্পর্কে ধারণা করা যায় না যে, তাদেঁর চিন্তা রাজ্যও এ চিন্তা শূন্য ছিল। তবু তাদেঁর একজনও সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে লিপিবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেননি।
তিনিই ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাকেঁ ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধকরণের ভিত্তি বলেছেন ও লিখেছেন, লোকেরা তাকে ভ্রান্তিবশত ইসলামী দর্শন নামে আখ্যায়িত করেছে। অথচ সেগুলো ছিল মুসলিম দর্শন। ঐ সব দর্শনের বংশসূত্র গ্রীস, রোম, ইরান ও হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কিত। যদিও শাহ্ সাহেবের পরিভাষার ক্ষেত্রে পুরাতন দর্শন, কালাম শাস্ত্র কিংবা সেখানকার বহু চিন্তা ও ধারণা লক্ষ্য করা যায়, তা শুরুতে নতুন পথ আবিস্কারদের জন্য স্বভাবতই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
শাহ ওয়ালিউল্লাহর সমাজ দর্শন
তিনি বিশ্ব জাহান ও এর মানুষ সম্পর্কে এমন এক দর্শন সৃষ্টি চেষ্টা, করেছেন, যা ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও তার সমভাবাপন্ন প্রকৃতিক অধিকারী হতে পারে।
নৈতিক ব্যবস্থা উপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের (Social Philosophy) ইমারত নির্মাণ করেন। ইরতিফাকাত (মানুষের দৈনন্দিন সংগঠন, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা (Taxation), দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এ সঙ্গে সমাজ সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতি সৃষ্টির কারণসমূহের উপর আলোকপাত করেন। তারপর তিনি শরীয়ত, ইবাদত, আহকাম ও আইন কানূনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা পেশ করেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের গুঢ় তথ্য বুঝাতে থাকেন। ইমাম গাযযালীকেও তিনি এ ব্যাপারে ছাড়িয়ে গেছেন। শেষের দিকে তিনি বিভিন্ন জাতির ইতহাস ও আইন-কানুনের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন।
উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এখানে শুধু তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। একটি অর্থনৈতিক, অপরটি রাজনৈতিক।
অর্থনৈতিক চিন্তাধারা
ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ অর্থনৈতিক দর্শনের মূলকথা হলো দেশের সামগ্রিক সম্পদ যে জনগোষ্ঠীর যৌথ বা বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাতে এমন সুষম বন্টন বা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে সম্পদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে। একচেটিয়া মালিকানা কিংবা দৈহিক বা মানসিক কোনরূপ শ্রমবিহীন মালিকানার তিনি বিরোধী। তাঁর মতে, নাগরিকত্বের প্রাণসত্তা হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, আর এই সহযোগিতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকে একের প্রতি অপরের কল্যাণকারিতার উপর, যা একমাত্র শ্রমের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, তিনি পুজিঁ ও মানসিক প্রচেস্ঠাকেও শ্রমের মধ্যে গণ্য করেন। অতএব তাঁর মতে, সমাজে কোন ব্যক্তি বিনাশ্রমে সম্পদ ভোগ করতে কিংবা অল্প শ্রমে অধিক সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। কেননা, তাদের মধ্যে নারিকত্বের এই মূল শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি তারা সম্পদের অধিকারী হয়, তা হলে স্মপদের যারা মূল উপার্জন শক্তি তথা কৃষক, শ্রমিক, পুজিঁ ও মানসিক শ্রমদাতা, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। আর তার অবশ্যন্তাবী পরিণতি হিসাবে সমাজে একদিকে শোষিত ও বঞ্চিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তাদের উপর নাগরিক দায়িত্বভার বেড়ে যাবে, তারা করভারে জর্জরিত হবে, অনাদায়ে নির্যাতন ও কঠোরতার সম্মুখীন হবে, অপরদিকে আর এক শ্রেণী কর্তৃক বিলাসিতা, বাহুল্য ও ইন্দ্রীয়পূজার বাজার গরম হয়ে উঠবে, যাতে কোন অবস্থায়ই জাতীয সম্পদ তো বৃদ্ধি পাবে না, পরন্তু তা অনেকের পকেটশূন্য হয়ে এক স্থানে এসে কুক্ষিগত হবে।
এক কথায়, তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী চাষী-মজুর এবং অন্যভাবে শ্রমদাতা যেসব ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য চিন্তামূরক কাজে নিয়োজিত, তারাই সম্পদের আসল অধিকারী (অবশ্য অক্ষম ও বিকলাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র)। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই মূলত জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। এ শক্তিসমূহকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে কোন ব্যবস্থা (চাই সেটা রাজতন্ত্রমূলকই হোক কিংবা অন্য কোন প্রকারের) সচেষ্ট হয়ে উঠলে সেটা কোন দেশ ও জাতির জন্য অবশ্যই মারাত্মক। এহেন অশুভ শক্তিকে অবশ্যই খতম করা উচিত-(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)। যে সমাজ ব্যবস্থা শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেয় না তার অবসান হওয়া আবশ্যক- (হুজ্জাতুল্লাহিল বারিগা, সিয়াসাতুল মাদানীয়া অধ্যায়)। তাঁর মতে, অভাবী শ্রমিকের সম্মতিকে তার সন্তুষ্ঠি মনে করা চলে না, যে পর্যন্ত না তার ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করা হবে, যা পারস্পরিক সহযোগিতার মূল নীতির ভিত্তিতে অপরিহার্য বলে গণ্য;(হুজ্জাত)। শ্রমিকের কাজের সময়কাল নির্দিষ্ট থাকতে হবে। তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং পরকালের ধ্যান ও চিন্তাভাবনার জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত সুযোগ দিতে হবে। জনগণের উপর অধিক করের বোঝা চাপানো অন্যায়-(হুজ্জাত)। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার বা প্রভাব দেশের জন্য মারাত্মক-(হজ্জাত)। কোন রাজকীয় জীবন ব্যবস্থার অধীনে-যেখানে বিশেষ গোষ্ঠী বা পরিবারের অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা, খামখেয়াল ও ব্যয়-বাহুল্যের ফলে সমাজে সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের দুঃখ মোচনার্থে উক্ত ব্যবস্থার অবসান হওয়া একান্ত জরুরী-(হুজ্জাত)।
এ থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর নিকট রাজতন্ত্রের অপকারিতাসমূহ সুস্পষ্ট ছিল এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার মধ্যেই তিনি মানবতার মুক্তি লক্ষ্য করেছেন। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিককালে যদিও এসব বিষয় অহরাত্র চর্চা হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি যে যুগে বসে এ কথা বলে গেছেন, সে সময়কাল পরিবেশ চিন্তু করলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। কেননা, তখনও ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হতে অর্ধশতক বাকী। কম্যুনিজমের জনক কার্লমার্ক্স ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস-এর জন্মেরও এক শতক পরে। তখন ইউরোপের যান্ত্রিকযুগের বয়স মাত্র চল্লিশ বছর। তাই এ কথা নিসন্দেহে বলা চলে যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মতো চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের যে যুগে আবির্ভাব ঘটে, সে সময় যদি উপমহাদেশে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতো কিংবা তিনি কার্লমাক্স বা এঙ্গেলসের মতো কোন মুদ্রাযন্ত্রের দেশে জন্ম নিতেন-যেখান থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারাকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তা হলে সম্ভবত সকলের পূর্বে তার সমাজদর্শন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদই বিম্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতো।
রাজনৈতিক চিন্তাধারা
এক. সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। এতে কোনরূপ অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী মানুষ হচ্ছে প্রবাসীর ন্যায়।
দুই. মানুষ হিসাবে প্রতিটি আদম সন্তানের সমান মর্যাদা। একের প্রতি অপরের প্রভুত্ব দাবী করার কোন অধিকার নেই-এক মানুষ আর এক মানুষের দাসত্ব করতে পারে না। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র বা জাতির মালিক হতে পারে না। কোন মানুষের পক্ষে ক্ষমতাশালী কোন শাসকের প্রতিও এরূপ ধারণা পোষণ করা অবৈধ।
তিন. রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা ‘মুতাওয়াল্লী’র সমতুল্য। মুতাওয়াল্লী প্রয়োজনবোধ করলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সে পরিমাণই অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন, যে পরিমাণ দ্বারা রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন নির্বাহ হয়ে থাকে।
চার. রাষ্ট্রের সর্বস্তরে একমাত্র আল্লাহর দীনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।
মৌলিক অধিকার
এ ব্যাপারে ‘হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’, ‘আল বদুরুল বাযেগাহ্’, প্রভৃতি গ্রন্থে ‘ইরতিফাকাত’-জনকল্যাণ অধ্যায়ে যা বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছেঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিবাহ, স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ প্রভৃতি জাতি-ধর্ম বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। ঠিক অনুরূপভাবে উচু নীচু নির্বিশেষে ভেদ-বৈষম্যবিহীন রাষ্ট্রের সকল মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা, তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর হিফাজত করা, প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সমান নাগরিকত্বের অধিকার লাভ সকল জন্মগত অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। তদ্রুপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকারও মৌলিক অধিকারসমূহের শামিল।
ইসলাম একটি বিপ্লবী দীন-একটি বিপ্লবী জীবন ব্যবস্থা
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ইসলামকে একটি বিপ্লবী জন বিধান বলেছেন। তাঁর মতে, ইসলাম যুক্তি ও শক্তিবাদের ধর্ম। বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণের খাতিরে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই আদর্শের পতাকা তলে সমবেত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব হয়। কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তিবাদ ও সুষ্ঠু বুদ্ধিমত্তার পথেই মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে হয়। শান্ত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূল কথা। তবে ইসলামের আহ্বানে একান্তভাবে যুক্তিযুক্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে হলেও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, মিথ্যা, অহেতুক আভিজাত্যবোধ ও স্বার্থপরতা ইসরামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হতে পারে। এ জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) বিশ্বাস করতেন যে, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য, এ সত্য ও শান্তির জবিন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যদি কখনও তদ্রুপ বিপ্লব দেখা দেয়, তবে তাকে সকল মানুষের সমর্থন করা উচিত মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের খাতিরেই। তাঁর মতে, বৃহত্তম কল্যাণের খাতিরে ছোটখাট ক্ষয়-কস্থির কথা চিন্তা করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়। কুরআন মজীদে উক্ত হয়েছে যে, “আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশমূলক হুকুম ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে একমাত্র এউদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন যে, এটাকে (সঠিক জীবন বিধানকে) অন্যান্য সকল (মানব রচিত) জীবন বিধান ও বিধি-ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করতে হবে-যদিও তাতে মুশরিক অবাধ্য লোকেরা জ্বলে পুড় উঠবে।“ এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলাম মানুষের পথ নির্দেশ সত্য জীবন-বিধান হওয়া সত্ত্বেও তাকে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সুব্যবস্থার অবশ্যক। ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মতে, এটা একমাত্র কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন একটি ত্যাগী, একনিষ্ঠ, সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ দলের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। ভাড়াটিয়া বা পেশাদার কোন ফৌজ দ্বারা এরূপ কাজ সম্ভব নয়।
ওয়ালিউল্লাহ চিন্তাধারার ফসল
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা এহেন যুক্তিগ্রাহ্য ও সুসংগঠিত খসড়া পেশ হবার অর্থই হলো এই যে, তা সকল সুস্থ প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হবে, আর তাদের মধ্যে যারা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী তারা এ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসবে। শাহ্ সাহেব জাহেলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, এ ব্যাপারটাকে বার বার এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে ঈমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র খতম করে সে স্থলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্ঠা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ ও ‘ইযালাতুল খিফা’তে এ বিষয়টির উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে তিনি হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী খেলাফত ও রাজতন্ত্র দ্ইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস অতপর একদিকে রাজতন্ত্র এবং সে সব বিপর্যয়কে স্থাপন করেন, যেগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের পথে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী এবং সে সব অবদান পেশ করেন, যা ইসলামী খিলাফত আমলে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে অনুসৃত হয়। এরপরও মুসলমানদের পক্ষে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কি করে সম্ভব হতে পারে? আর পারে না বলেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর ইনতিকালের (১৭৮৬-১৮৩১) অর্ধশতক অতিক্রান্ত হবার আগেই ভরতবর্ষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী ও ইসমাঈল শহীদ দেহলভীর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্ভব হয়। তারা একটি অস্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। অবশ্য কতিপয় বৈষয়িক কারণে তা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব উপমহাদেশে এখনও বিদ্যমান। অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে সেই আন্দোলনের প্রভাব কাজ করেছে এবং বলতে কী এ অঞ্চলে খাটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিস্ঠার যে আন্দোলন প্রকট, মূলত এটাও ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারার ও বালাকোটে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের চরম আত্মত্যাগেরই ফল। কেননা, বালাকোটের ব্যর্থতার পর যখন উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর বিজাতীয় কর্তৃত্ব প্রাধান্য লাভ করে, তখনও আলিম সমাজ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি, তাঁরা ঘোর তমসার মধ্যেও ইসলামের নিভু নিভু দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা পরিকল্পনার মাধ্যমে উপমহাদেশে জালের ন্যায় দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মাদ্রাসা সমূহ কায়েম করে এগুলোর মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষা-সঙস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এ পরিকল্পনাধীন মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দই ছিল প্রধান। আযাদী ও ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্টিত দারুল উলুম দেওবন্দ ও এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে উপমহাদেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে ইসলামী জাগরণ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, পরবর্তী পর্যায়ে খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে তারই অতিব্যক্তি ঘটে। তাই উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণ ও পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলন ও র্বমানে এদেশসহ সারা মুসলিম দুনিয়ায় যে ইসলামের নবজাগরণের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটাকে নির্দ্বিধায় ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা ও তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের আন্দোলনেরই ফলশ্রতি বলতে হবে।
উল্লেখযোগ্য যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর আকাংখিত ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে প্রথম ইসলামী আন্দোলন (বালাকোট) এবং পরবর্তী পর্যাযে সিপাহী বিপ্লব, বাঙলাদেশে ফরায়েযী আন্দোলন, হাজী তিতুমীর মুন্সী মেহেরুল্লাহর আন্দোলন প্রভৃতি সকল জাতীয জাগরণের পটভূমি রচনায় যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির মাধ্যমে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা কাজ করেছিল তিনি ছিলেন তারই সুযোগ্য জেৌষ্ঠপুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) (১৭৪৭-১৮২৪ খৃস্টাব্দ)। পিতার ইনতিকালের পর সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উক্ত মহান লক্ষ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি পিতৃ শিক্ষা প্রতিস্ঠানের (টীকা: উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম সাহেব হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুরাতন রহীমিয়া মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যার আধিক্য হেতু সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ কর্তৃক মাদ্রাসার জন্য যে বিশাল অট্টালিকাটি প্রদত্ত হয়েছিলো সেটি ১৮৫৭ সালের হাঙ্গামায় ধ্বংস প্রপ্ত হয়) মাধ্যমে প্রথমে দীনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আজকের উপমহাদেশে অগণিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর পত্যেকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শাহ্ আবদুল আযীযের মাধ্যমে অসংখ্য লোক বিপ্লবী বাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর চার ভ্রাতা, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ দেহলভীসহ কতিপয় প্রখ্যাত শিষ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ (১) মওলানা শাহ্ রীফউদ্দিন, (২) মওলানা শাহ্ আবদুল কাদের, (৩) মওলানা শাহ্ আবদুর গনী, (৪) মওলানা শাহ্ মুহম্মদ ইসহাক, (৫) শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব, (৬) মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হাই, (৭) মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল, (৮) সাইয়েদ আহমদ শহীদ, (৯) মওলানা রশীদুদ্দীন, (১০) মওলানা মুফতী সদরুদ্দীন, (১১) মুফতী এলাহী বখশ, (১২) হযরত শাহ্ গোলাম আলী, (১৩) মওলানা মাখসুল্লাহ, (১৪) মওলানা করীমুল্লাহ, (১৫) মওলানা মীর মাহবুব আলী, (১৬) মওলানা আবদুল খালেক, (১৭) মওলানা হাসান আলী লক্ষৌভী, (১৮) মওলানা হোসাইন আহমদ মলীহাবাদী প্রমুখ।
শাহ্ আবদুল আযীয (রহ)-এর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল-
(১) ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারাকে মন-মস্তিস্ক দিয়ে উপলব্ধি করা, (২) আল্লাহভীতি ও আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা লাভ, (৩) রাজতন্ত্র ও সরকার তোষণ মনোভাব মন-মস্তিস্ক থেকে দূর করা, (৪) ইসলামী বিপ্লবকে পরিপূর্ণ জয়যুক্ত করণার্থে ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করা, (৫) সমাজসেবা ও দুঃস্থ মানবতার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করা, (৬) রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করে সহজ-সরল জীবন-যাপন করা, (৭) জিহাদী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং যে কোন দুর্যোগ মুহুর্তে দৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা, (৮) সমাজ বিধ্বংসী সকল প্রকার অনাচার, কুসংস্কার ও রীতিনীতি উৎখাতের চেষ্টা করা, (৯) বিলাসিতার আড্ডাখানাসমূহের অবসান করা, যা সমাজকে আরাম প্রিয় ও দুর্বল করে তোলে। এ ছাড়া শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) রীতিমতো সপ্তাহে দুবার মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসভায় বক্তৃতা করতেন।
বাংলাদেশে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ চিন্তাধারার প্রভাব
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা ও রচনাবলীর ফলে সার্বিকভাবে সমস্ত উপমহাদেশ উপকৃত হলেও বাঙলাদেশে তার চিন্তাধারার বিস্তার লাভের যে সব কারণ দেখা যায়, তন্মধ্যে দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমরা ছাড়াও তার পূর্বে ১৭৮১ সালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর শাগরিদ মওলবী মজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদনের ব্যক্তিত্ব ও অপ্যাপনাও কম কাজ করেনি। তিনি ১৭৬৪ সালে দিল্লী থেকে কলকাতা আসেন। এখানে তিনি একান্ত অজ্ঞাত জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু আগুন কখনও কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় থাকে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও আল্লাহভীরতার সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় মুসলমান সুধীবৃন্দ তাকেঁ কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে তদানীস্তন বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনুরোধ করলে তিনি তাদের কথায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে সায় দেন। তিনি মন্তব্য করলেন হ্যাঁ, সরকারী কাজে সাহায্য করতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর কর্মচারী তৈরীর জন্যও সরকারের এ প্রকার একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। অতপর ১৭৮১ সালের অক্টোবরে কলকাতা শহরের বৈঠকখানা অঞ্চলে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। আর মোল্লা মদন তারই প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।
বস্তুত ঐ মাদ্রাসাই পরে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিত হয়। অবশ্য ঐ পরিবেশে কলকাতার উক্ত মাদ্রাসা থেকে ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারার আশানুরূপ বিকাশ ঘটা কতদূর সম্ভব ছিল তা স্বতন্ত্র কথা। তবে আমরা বর্তমানে যতদূর দেখতে পাই, পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় যে, এককালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলন ও আযাদী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বারা যে দেওবন্দ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার কাজ প্রথম যে মহান ব্যক্তির দায়িত্বে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ফলশ্রতি হিসাবেই উমহাদেশে পাকিস্তানের ন্যায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সৃষ্টি হলোঃ আজ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম-উলামাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া অনেকের মধ্যেই উক্ত বিপ্লবী ভবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না? যুগ সমস্যার, যুগ জিজ্ঞাসা ও আধুনিক নানাবিধ বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার মতো যে ধরনের এবং যে পরিমাণ যোগ্য আলিমের প্রয়োজন ছিল, ঐ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম-উলামাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া অনেকের মধ্যেই উক্ত বিপ্লবী ভবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না? যুগ সমস্যার, যুগ জিজ্ঞাসা ও আধুনিক নানাবিধ বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার মতো যে ধরনের এবং যে পরিমাণ যোগ্য আলিমের প্রয়োজন ছিল, ঐ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তা পরিবেশন করনতে সমর্থ হচ্ছে না, তারই পরিণতিতেই হয়তো যোগ্য ইসলামী নেতৃত্বের অভাব ঘটায় ইসলামের নামে এদেশ অর্জিত হলেও আজও এখানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না বরং দিনের পর দিন পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। সম্ভবত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা-পদ্ধতি ও এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম অথবা দীনী চিন্তার গরমিলের দরুনই এমনটি হতে চলেছে। এ ব্যাপারে উলামা নেতৃবৃন্দের আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ বংশের শাজরা
I
শায়খ শামসুদ্দিন মুফতী
I
শাহ ওয়াজিহদ্দীন
I
শাহ আবদুর রহীম
I
শাহ আবদুল্লাহ শাহ ওয়ালিউল্লাহ
৩. শাহ আবদুল কাদের ৪. শাহ আবদুল গনী
I I
১. শাহ আবদুল আযীয ২.শাহ রফীউদ্দীন
মওলানা মুখসুল্লাহ
মওলানা আবদুল হাই(জামাতা)
I I
শাহ ইসমাইল শহীদ
I
মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব
গ্রন্থাবলী
তাঁর গ্রন্থাবলীকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে কুরআন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত কুরআন মজীদের তরজমা ফতহুর রহমান উল্লেখযোগ্য। এটি কুরআনের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ তরজমা। তাঁর এ পর্যায়ে গ্রন্থের মধ্যে মুকদ্দমা ফী তারজুমাতিল কুরআন আল ফওযুল কবীর এবং আল ফাতহুল কাবীর’ও রয়েছে। এ গুলোতে কুরআনের তরজমা ও ব্যাখ্যার মুলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে।
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হাদীস সংক্রান্ত। এর মধ্যে ইমাম মালিকের বিশ্ববিখ্যাত মুয়াত্তার আরবী শরাহ মুসাওয়া ও মুসাফ্ফা’ প্রসিদ্ধ। হাদীসে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আন্নাওয়াদির মিনাল হাদীস আল দুররিশ-সামীন’ ও ‘শরহে তরজমা-এ-আবওয়াবে বুখারী’ প্রসিদ্ধ।
তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে হচ্ছে ফিকাহ শাস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে (ক) ‘আল ইনসাফ’ (খ) ইকদুলজীদ ফী আহকামিন ইজতিহাদ ওয়াত্তাকলীদ। এসব গ্রন্থের মধ্যে তিনি ফকীহতের ইখতেলাফকে বিরোধিতা নয় বরং মতদ্বৈধতারূপে দেখিয়ে দিয়েছেন।
চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হচ্ছে তাসাউফ সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে (ক) ফায়সালাতু ওয়াহদাতিল ওয়াজুদ ওয়াশ শাহুদ (খ) আল কওলুল জামীল, (গ) তাফহীমাতে-ইলাহিয়া (ঘ) আলতাফুল কুদুস (ঙ) আন-ফানসুল-আরিফী (চ) ফুয়ুযুল-হারামাইন (ছ) আলখায়রুল-কাসীর (জ) সাৎয়াত ও (ঝ) লুময়াত বিখ্যাত।
পঞ্চম শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ ‘আলহুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’। তাঁর এ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটিকে ইসলামের ভাষ্য বলা চলে। মওলানা মানাজির আহসান গিলানীর ভাষায় ‘আমি এ গ্রন্থটির ন্যায় মানব রচিত এমন কোন গ্রন্থ দেখিনি, যাতে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে।‘
এ অমর গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা বাংলার শ্রেষ্ঠতম সুফী চরিত্রের ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী সাহেব আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে উর্দু ভাষায় তাঁর লিখিত ‘নেজামে তালীম’ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেন, “আমার মতে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহর (স) সুন্নাহর পরে এটাই সর্বোৎকৃষ্ঠ কিতাব। কেননা, এতে এমন সব জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয় রয়েছে যা অপর কোন গ্রন্থে নাই, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কানে শোনেনি, এমনকি কেউ অন্তর দিয়েও উপলব্ধি করেনি। মূলত এটা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা অথচ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য-বরং বলা চলে মুহাম্মদী শরীয়তের নির্যাস।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি