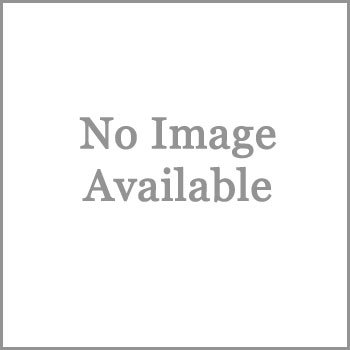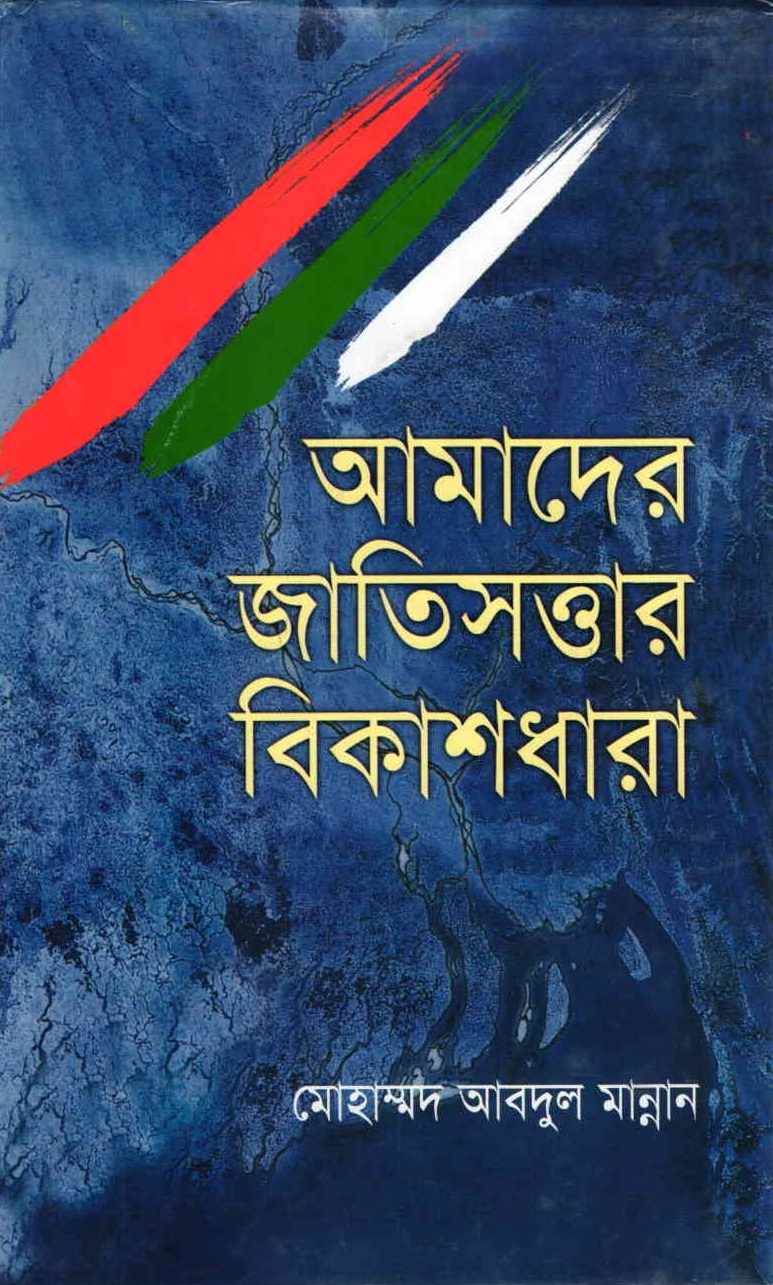১.
সভ্যতার পতাকা হাতে সাহসী মানুষ
আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রীক বিবরণীতে গঙ্গার পুবদিকে গঙ্গারিড়ী বা বঙ্গ-দ্রাবিড়ী নাম এক শক্তিাশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা-বিধৌত এ রাজ্যের বঙ্গ-দ্রাবিড় জাতি ছিল অপরাজেয় শক্তি। টলেমী জানাচ্ছেন, গঙ্গা-মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিড়ীরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গা খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখাকার তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল-রত্ন পশ্চিম দেশে রপ্তানি হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত জাতি ভাতে আর নেই।
আদিতে বঙ্গ ছিল বর্তমান বাংলাদেশেরই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বঙ্গ সেই স্বতন্ত্র ক্ষদ্রতর রূপেই পরিচিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকেও বাংলার শুধু পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলেই বঙ্গ নাম অভিহিত হতো। পাল ও সেন আমলে এবং মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত ছিল রাঢ় নামে। উত্তর বঙ্গকে বলা হতো পুন্ড্রবর্ধন, বরিন্দ্ কিংবা লাখনৌতি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিচু অংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। বাংলার পুব ও দক্ষিণ অঞ্চলকে মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর ১২৪২-৪৪ সালের তাবাকাত- ই- নাসিরীতে বঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকা গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে জিয়াউদ্দীন বারনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্হ তারিক-ই-ফীরুজশাহীতে প্রথম তা উল্লেখ করেন। মিনহাজের ‘বঙ্গ’ আর বারনীর ‘বাঙ্গালাহ’ বাংলার পুব-দক্ষিণবর্তী অভিন্ন অঞ্চল। বৃহত্তর ঢাকা ও সাবেক ত্রিপুরা জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চল সমতট নামেও পরিচিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা দূর-অতীতে কখনো বাংলা বা বাঙ্গালা কিংবা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না।
বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ ঈসায়ী) প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মাপুত্রের নিম্ন অববাহিকার ব্যাপকতর এলাকাকে বাঙ্গালাহ নাম অভিহিত করেন। লখনৌতি (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ও বাঙ্গালাহকে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল তার আমলেই প্রথম বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয় এবং তিনি প্রথমবারের মতো শাহ-ই-বাঙ্গালাহ নাম ধারণ করে নিজেকে বৃহৎ বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এর ফলে এখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের সূচনা হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ
“ যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের- সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান (মুসলিম( আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল”।
(বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব- সূভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ২২)
এরপর বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার আয়তন পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু বৃটিশ ভারতের বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশ নয়, পশ্চিমে বিহারের অংশ, পুবে আসাম এবং কোন কোন সময় উড়িষ্যার অংশবিশেষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এসবের শাখানদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটির পাললিক গঠন ও মৌসুমী আবহাওয়া বাংলাদেশের মাটিকে বিস্ময়করভাবে উর্বর করেছে, চাষাবাদকে করেছে উৎসাহিত। সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের আকর্ষণ আর ভূ-প্রকৃতিগত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে ঘন বসতিপূর্ণ। নদ-নদীর তীর ঘেঁষে এখানে গড়ে উঠেছে মানব-বসতি, পত্তর হয়েছে গ্রাম-বন্দর। এ জনপদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার-বন্দর বিকশিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহকে ঘিরে। নদ-নদীর দুই পার জুড়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে বিরামহীন ভাঙ্গা-গড়া আর পরিবর্তনের ধরা। এদেশের অনেক জনাকীর্ণ শহর-গ্রাম-জনপদের উত্থান আর পতনের সাথে এ ধারা মিশে আছে। বাংলার জন-জীবনে এবং এদেশের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ন্ত্রণেও যুগ-যুগ ধরে নদ-নদীর রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা।
নদ-নদীর প্রবাহ এ দেশের সমতলভূমিকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাজিত করেছে। এসব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা ও ঐক্যবদ্ধ রাখা বরাবরই ছিল কঠিন কাজ। এসব বিচ্ছিন, বিভক্ত এলাকায় স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক সত্তার উত্থান ও বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষ্রদুশাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ এলাকার রাজনীতি চিহ্নিত হয়ে বহুকাল। রাজ্য ও প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহের দ্বারা। বহিঃসীমান্তের নদীপ্রবহা এবং অভ্যন্তর ভাগের অসংখ্য শাখা, প্রবাহ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা ও জলপ্লাবিত সমতলভূমি এদেশকে দুর্গম করেছে। বাইরের হামলার বিরুদ্ধে দিয়েছে প্রতিরক্ষঅর প্রাকৃতিক সুবিধা। এ বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আদি-বঙ্গ বরাবরই বাইরের হামলা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরপদ ছিল। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চল ও উত্তর বঙ্গ প্রাচীনকালে বহুবার উত্তর ভারতীয় শাসকদের কর্তৃত্বাধীন হয়েছে।
নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এ দেশের মানুষের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এ এলাকার মানুষকে কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী করেছে। সংগ্রামশীল এই সাহসী মানুষেরা বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার দুর্জয় প্রেরণা নিয়ে। হাজার বছরের কুসংস্কার আর অধর্মেল বিকৃতি বুকে নিয়ে বৈদিক শাস্ত্র-শাসনের ভারে ন্যূব্জ ও আড়ষ্ট ভারত ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে যে কোন পরিবর্তনের ধারাকে ভয় পায়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুসের প্রাণ-ধর্ম ও হৃদয়-আবেগের দু’ধা স্রোতস্বিনীর মুখে সেসব জঞ্জাল ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অনায়াসে।
সেমিটিক তৌহিদবাদী, ধর্মমতের উত্তর-পূরুষ এবং উন্নততর সংস্কৃতির ধারক বঙ্গ-দ্রাবিড়রা আর্যদের শির্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্হ, তাদের তাপস্যা ও যাগযজ্ঞ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ট হওয়ার ধারণাকে কখনো কবুল করেনি, মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট, নযিরবিহীন জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়েও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ বিশ্বাস, শিক্ষা, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষের চিত্ত জুড়ে গভীর আসন গেড়েছে। জীবাত্মার নির্বাণ লাভের বুদ্ধ-বাণী তাদেরকে উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সবশেষে মানব-মুক্তির মহাসনদ ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে ও জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে।
সিন্দু নদের উপত্যকায় তার সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য-ভারতে ও রাজস্থানের নানা জায়গায় প্রাক-আর্য তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় এমনি সভ্যতা-সম্পন্ন এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। তারা প্রধানত দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা ছিল। এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তারা এসেছে সেমিটিকদের আদি বাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়া দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল। এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। তারাই ইয়েমেন ও ব্যাবিলনকে সভ্যতার আদি বিকাশ ভূমিরূপে নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালা উদ্ভাবন দ্রাবিড় জাতিরই অবদান। সুপ্রাচীন এক গর্বিত সভ্যতার পতাকাবাহী এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে আর্য আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মহোঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। অনুরূপ সভ্যতার পত্তন হয়তো তারা বাংলাদেশেও করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতির কারণে সেগুলোর চিহ্ন এখন নেই। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেনঃ
”তারা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতো সুন্দর নগরী পাক-বাংলায় নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পাথ্যক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোন চিহ্ন নাই। প্রাকৃতির কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলা যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতি, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়ে পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দায করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না”। (আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি, পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা-১৯৬৯)।
২
বাংলায় আর্য আগমন
দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত আর্যদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই যাযাবরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে আরো পুবদিকে অগ্রসর হয়। সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বৈদিক আর্যরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় অর্জনেও সকল শক্তি নিয়োগ করে। প্রায় সম্পর্ণ উত্তর ভারত আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বাধীন মনোভাব ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত বঙ্গবাসীরা আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুকে দাঁড়ায়। ফলে করতোয়ার তীর পর্যন্ত এসে আর্যদের সামরিক অভিযান থমকে দাঁড়ায়।
আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেনঃ
“প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াচিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে ভাগলপুরের সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই”। (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ২১)
সামরিক অভিযান ব্যাহত হওয়ার পর আর্যরা অগ্রসর হয় ঘোর পথে। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান পরিচালনা করে। তাই দেখা যায়, আর্য সামাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এ দেশে প্রথম আসেনি, আগে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। কেননা, ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেলে সামরিক বিজয় সহজেই হয়ে যাবে। এ এলাকার জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তা ছিল মূলত তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা হেফাযত করার লড়াই। তাদের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শত শত বছর স্থায়ী হয়। ‘স্বর্গ রাজ্যে’ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের যে অসংখ্য কাহিনী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি আর্য সাহিত্যে ছড়িযে আছে, সেগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের কাহিনীকে এসব আর্য সাহিত্যে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে কোন মানবগোষ্ঠীকে এমন নোংরা ভাষায় চিহ্নিত করার নযীর পাওয়া যাবে না। উইলিয়াম হান্টার তার ‘এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল’ বইয়ে ও প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ
“সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজনিত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তীতে। ……… যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদেরকে প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে”।
সাংস্কৃতিক সংঘাত
কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর ‘এর সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল’ বইয়ে দেখিয়েছেনঃ তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। বাংলা ও বিহারের জনগণ আর্য-অধিকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাও ছিল ধর্মভিত্তিক তথা সাংস্কৃতিক।
আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম তথা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে জেগে ওঠা এই এলাকার সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের সংক্ষোভের তোড়ে উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলোর আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল।
বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এদেশে আর্য-প্রভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবাংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকেই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। তারপর চার ও পাঁচ খ্রিস্টাব্দের গুপ্ত শাসনামলে আর্য ধম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।
মৌর্য বংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। আশোকের যুগ পর্যন্ত এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ছিল না। কিন্তু তারপর তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটে। হিন্দু দেব-দেবীরা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা লাভ করতে শুরু করে। বৌদ্ধ ধর্মের এই বিকৃতি সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডট ‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ বইয়ে লিখেছেনঃ
“Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of th Buddha into a Divine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu partheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu.”
সতিশচন্দ্র মিত্র তাঁর ‘যশোর খুলনার ইতিহাস’ গ্রন্হে লিখেছেনঃ
“যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে ইহা পুঁতিয়া রাখিতেন। …….. উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাঁহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়”।
অর্থাৎ হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে এভাবে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়েছিল। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিল না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেল নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তারপর বুদ্ধের চরণ দেখা গেল। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসল। এভাবে ধীরে ধীরে এমন সময় আসল, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকল।
গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দোর্দন্ড প্রতাপ শুরু হয়। আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবল আছড়ে পড়ে এখানে। এর মোকাবিলায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা ও বিহারের জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এ সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর জনগণের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ শক্তিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেনঃ
“আর্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপি্থি হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফলাফল”।(বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)
এ আন্দোলনের তোড়ে বাংলা ও বিহারে আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল। আর্য-দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পুব-সীমানার রাজ্যগুলো শুধু মুক্তই হয়নি, শতদ্র নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা অনার্য রাজাদরে অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত জনজাগরণের শক্তিতেই শিশুনাগবাংশীয় মহানন্দের শূদ্র-পুত্র মাহপদ্মনন্দ ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করে সমগ্র আর্যবার্ত অনার্য অধিকারে এনে ‘একরাট’ উপাধি ধারণ করেছিলেন।
বাংলাদেশেই আর্যবিরোধী সংগ্রাম সবচে প্রবল হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে আবদুল মান্নান তালিব লিখিছেনঃ
“সেমিটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর পুরুষ হিসেবে এ এলাকার মানুষের তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভাবত তাদের একটি অংশ আর্য আগমনকালে তৌহীদবাদের সাথে জাড়িত ছিল। এ কারণেই শের্কবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলতে থাকে”। (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪)
জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতমের জীবনধারা এবং তাদের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ অনেক গবেষক মনে করেন যে, তারা হয়তো বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মান্নান তালিব লিখেছেনঃ
“জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্হ বেদকে ঐশী গ্রন্হ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরুপণ করে যে, বেদবিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে”। (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)
মওলানা আবুল কালাম আযাদ দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ কখনো নিজেকে ভগবাদ দাবি করেননি। অশোকের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধ-মূর্তির প্রচলনও কোথাও ছিল না। প্রতিমা পূজাকে সত্যের পথে এক বিরাট বাধা গণ্য করে সেই অজস্র খোদার খপ্পর থেকে বুদ্ধ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করে দিব্যজ্ঞানলাভ ও সত্য-সাধনায় মুক্তি নিহিত বলে ঘোষণা করেছিলেন।
বাংলায় দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে দীর্ঘ দিন আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এরপর খ্রিস্টীয় চার ও পাঁচ শতকে গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক হিন্দু ধর্মের কিছুই প্রসার হয়নি। ষষ্ঠ শতকের আগে বঙ্গ বা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি। উত্তর-পূর্ববাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠে। পঞ্চম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়াগার সংস্কৃতি নাম পাওয়া যায়। তা থেকে ড. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, তখন বাংলার আর্যয়করণ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছিল। অযোধ্যাবাসী ভিণ প্রদেশী বাহ্মণ, শর্মা বা স্বামী, বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঙি নামে ব্রাহ্মণেরা জেঁকে বসেছিলঃ
“বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেই ঋগ্বেদীয়, কেই বাজসনেয়ী, কেউ শাখাব্যয়ী, যাজুর্বেদীয়, কেই বা সামবেদীয়, কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব, বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎসা বা কৌন্ডিন্য। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল”। (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩২)
সাত শতকের একেবারে শুরুতে গুপ্ত রাজাদের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ্য-শৈবধর্মের অনুসারী শশাংক রাঢ়ের রাজা হয়ে পুন্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে তিনি বৌদ্ধ নির্মূলের নিষ্ঠুর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা শশাংক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন। তিনি আদেশ জারি করেনঃ
“সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বুদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে”। (রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, পৃষ্ঠা ১২৪)
সাত শতকের শেষার্ধ থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত গোর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ‘মাৎসান্যায় যুগ’। এ যুগে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের শিথিলতার সুযোগে আর্য-ব্রাহ্মণেরা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মাৎস্যন্যায়ের এ অন্ধকার যুগেই এদেশে সংস্কৃত ভাষাও মাথা তোলে।
পাল আমলঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতির আয়ূ বৃদ্ধি
দীর্ঘ এক শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে আট শতকের মধ্যভাগে গরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে গৌড়-বঙ্গ-বিহারে বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল শাসনের সূচনা হয়। পাল শাসনের চারশ’ বছর ছিল এদেশের মানুষের গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এ আমলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। কয়েকটি ছাড়া সকল মহাবিহার ছিল বাংলাদেশে। দশ শতকের শেষভাগের জেষ্ঠ্যজেতাবীর বাড়ি ছিল উত্তর বঙ্গে। তার ছাত্র বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর শ্রজ্ঞান (৯৮০-১০৩৫) জ্ঞানরাজ্যের এক বিশ্ববিশ্রত নাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্য শীলভদ্রও ছিলেন বাংলাদেমের অধিবাসী। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক। জনগণের মুখের ভাষার মর্যদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ যুগের আরেক গৌরব। এ যুগে ছিল বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল।
বাংলার পাল-রাজত্ব চারশ’ বছর স্থায়ী হয়। গৌড়-বঙ্গে পাল শাসন চলাকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সমসাময়িক আর্য-ব্রহ্মণ্য শক্তিপুঞ্জ সুলতান মাহমুদের হামলায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল। ফলে পাল শাসন তার ভৌগোলিক সীমান্তে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব থাকে। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত পাল শাসনে বাংলায় বৌর্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম এ সময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে। পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ূ আরো চার-পাঁচশ বছর বৃদ্ধি পায়।
পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির মিল-সমন্বয়ের স্লোগান দেয়। বহিঃসীমান্তে তাদের মিত্ররা সামরিকভাবে সুবিধা করতে না পারলেও ব্রাহ্মণদের এই চতুর কৌশল বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় তারই বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেনঃ
“পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল”। (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯)
এ সময় পাল রাজারা অনেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আর তাদের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকর্মে নিজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশেষত দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হলো, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় নয় শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যেকার। এই সমন্বয় ছিল এক তরফা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই গড়ে উঠেছিল সবকিছু। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়ঃ
“এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষগত হয়ে পড়ছিল।…… বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল”। (বাঙালির ইতিহাস, ১৫১)
তথাকথিত এই মিল-সমন্বয়ের আদর্শ বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছিল, তাদের জাতিসত্তাকে করে তুলেছিল অন্তঃসারশূন্য, আার রাষ্ট্রসত্তাকে করে তুলেছিল বিপন্ন। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির সীমানা হেফাযত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকেরা রেখে গেছেন।
সেন শাসনঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য
পাল-রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটদেশীয় চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বর্ণের সেনরা বাংলাদেশ শাসন করে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বারো শতকের শুরুতে রাঢ়-এর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করে সামন্তরূপে জেঁকে বসেন। পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যের গোলযোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নাদশার এই সুযোগে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (মৃঃ ১১৫৮) এখানে প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্ঠা করেন। তার রাজধানী ছিল বিজয়পুর। বঙ্গের বিক্রমপুরে ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী । শিব-এর পূজারী বিজয় সেন ও তার পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধারায় কুলীনপ্রথাভিত্তিক বর্ণশ্রমবাদী সমাজের ভিত রচনা করেন। তখনকার অবস্থা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেনঃ
“সেন শাসনামলে দেখতে দেখতে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল। নদ-নদীর ঘাটে-ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পুণ্য-স্নানার্থীর মন্ত্র-গুঞ্জরণ, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতের অনুষ্ঠান, জনগণের দৈনন্দিন কাজর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানা স্তর-উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা- এক কথায় সমস্ত রকম সমাজ-কর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে সমাজাদর্শ পৌরণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। সে আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে, মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো”। (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)
সেন আমলে বর্ণাশ্রম প্রথা পুরোপুরি চালু হলো। উৎপত্তি হলো ছত্রিশ জাতের। যারা উৎপাদনের সাথে যত বেশি সম্পর্কযুক্ত, তাদের স্থান হলো সমাজে ততো নীচুস্তরে। যারা যতো বেশি উৎপাদন-বিমুখ, অন্যের শ্রমের ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, যত বেশি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী, সমাজে তাদের মার্যাদা হলো তত উপরে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। এভাবে সেন-বর্মন শাসিত বাংলাদেশে একটি সর্বভুক পরগাছাশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম হয়।
জাতিসত্তা বিনাশের অভিযান
পাল আমলে সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণেরা তথাকথিত মিল-সমন্বয়ের কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেন-বর্মন পর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তথাকথিত সমন্বয়ের মুখোশ আর রাখল না। তারা স্বমূর্তিতে আগ্রাসনের দাঁত-নখ ব্যাদান করে রাজপথ আগলে দাঁড়াল। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি যে উদারতা দেখান হয়েছিল, তার বদলা হিসেবে ব্রাহ্মণবাদী সেনরা বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করল নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান। সে নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। ‘ডিসকভারিজ অব লিভিং বুদ্ধইজম ইন বেঙ্গল’ গ্রন্হের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেনঃ
“যে জনপদে (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১৫৫০ ঘর ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্হ ত্রিশ বছরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল, তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিস্কৃত হইতেছে”। (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা ১১-১২)
ভারতে তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেনঃ
“ভারতের মাটি ও আবহাওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা মৌসুমী ফুলের মতই অবলুপ্ত হয়নি। এই পতন ও এই অবলুপ্তি অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা নয়- সম্পর্ণ অস্বাভাবিক। ভারত-ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের অবলুপ্তি এর আয়ুষ্কালের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি নয়, এটা কঠোর হস্তের একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড………..। ……….. আমি শুধ বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার ও বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসস্তূপগুলোর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা উল্লেখ করব যে, ঐ সকল ধ্বংসস্তূপই বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি গঠনের সাধনা ও সিদ্ধি এবং বিরুদ্ শক্তি কিরূপ নির্মম হস্তে সে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সমাহিত করেছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ- জীবন্ত স্বাক্ষর”। (টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃষ্ঠা ২১)
সেন-বর্মন শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধ জাতিসত্তার সাথে এ এলাকার জনগণের মুখের ভাষার অস্তিত্বের সংকটও সৃষ্টি হয়েছিল। সেই চরম দুর্গতির বিবরণ দিয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেনঃ
“পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংগালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যজাত বাংগালা ভাষায় রচিত গ্রন্হগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাংগালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাংগালা গ্রন্হ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য”।
(প্রাচীন বাংগালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯-১০)
সে আমলের বাংলা ভাষার কিছু নমুনা ১৯০৭ সালে ড, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। চর্যাপদ নামে পরিচিত এই চারটি পুঁথি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন শুধু নয়; আমাদের পূর্বপুরুষদের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামের কাহিনী এবং তাদের রুদ্ধ হাহাকার এসব প্রাচীন পুঁথির পাতায় কান পাতলে শোনা যায়।
প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন ধারা
সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে দেশবাসীর জীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুম জনগণের পক্ষের শক্তির হিসেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইসলাম প্রচারক আলেক, সূফী ও মুজাহিদগণ। বাংলাদেশে রাজা শশাংকের সময় থেকেই ইসলাম প্রচারকদের আগমনের সূচনা হয়। এরপর মাৎস্যন্যায় যুগের ঘন অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল দেশের নানা জায়গায়। ইসলাম প্রচারকগণ নিপীড়িত জনগণকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়ান বিক্রমপুরে, পুন্ড্রবর্ধনে, রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে।
দশ ও এগারো শতক থেকে অসহায় দলিত মানুষের কানে ইসলামের মুক্তিবাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল দ্রোহাত্মক উচ্চারণ।
দ্বাদশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাঙ্গেয় উত্যকার অভ্যন্তরে এক নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলে। আর্যদের বৈদিক ও পৌরণিক ধর্মের বিরুদ্ধে বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল, ইসলামের দ্রোহাত্মক বানী তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল।
একেকজন ইসলাম প্রচারক জনগণের কাছে আবির্ভূত হন তাদের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে। প্রচারকদের গড়ে তোলা মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাগুলো নির্যাতিতের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের লঙ্গরখানা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় ও চাহিদা পূরণের কেন্দ্র এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্গ হিসেবে পরিচিত হয়।
৩
মুসলিম শাসনঃ বাংলার ইতিহাসের গঠনমূলক যুগ
ইসলাম প্রচারক আলেম, দরবেশ ও মুজাহিদগণ জনগণকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তার মধ্যে দিয়ে ইসলামের প্রতি জনগণের সমর্থন গড়ে ওঠে। জনসমর্থনের সে দৃঢ় ভিত্তির ওপর ১২০৩ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন হয় ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ঐতিহাসিক বিজয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু লামা তারানাথ তাঁর ষোল শতকের বিবরণীতে জানান, বৌদ্ধরা মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দিত করেছিল এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীকে বিজয়ে সাহায্য করেছিল। শ্রীচারু বন্দোপাধ্যায় ও প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধরা মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে কিছুটা শান্তি লাভ করেছিল।
লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুর্নিয়া শহর, দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পুব ও দক্ষিণ-পুবে তিস্তা ও কারতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী একশ’ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে।
বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়, এখানে তা উদ্দেশ্যও নয়। তবে এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলার মুসলিম বিজয় ছিল জনগণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামেরই সাফল্য, যা তাদরে সামনে বহুল প্রত্যাশিত এক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ভারতে মুসলিম বিজয় সম্পর্কে গোপাল হালদার মন্তব্য করেনঃ
“ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির………. এ পরাজয় রাষ্ট্র-শক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদার নীতি ও আত্ম-সচেতনতার কাছে। ………. কারণ ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে তুলে নেয়”।
(সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃষ্ঠা ১৯৬)
ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির ব্যর্থতা ও ইসলামী সংস্কৃতির বিজয়ের কারণ চিহ্নিত করে কমরেড এম. এন. রায় ‘ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান’ নামক গ্রন্হে লিখেছেনঃ
“ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি বরং তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে। সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ-শক্তি তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তার ফল হলো এই য, বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচার-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ডুবে গেল। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এজন্য নিপীড়ত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভীড় করে দাঁড়াল……….। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করল। তার কারণ তার পিছনে জীবনের প্রতি সে দৃষ্টিবঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শন সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃঙ্খলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণেকে মুক্তির পথ দেখায়”।(পৃষ্ঠা ৬১-৬২)
মুসলিম শাসন আমল বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ হিসেবে ঐতিহাসিকদের বিবেচনা লাভ করেছে। এ জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ যুগেই একটি উন্নত ও সংহত রূপ লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে এ যুগেই বাংলার জনগণ একটি আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ হয়। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তিও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. এম এ রহীমের মন্তব্যঃ
“যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ প্রদেশে আর কয়েক শতকের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন অব্যাহত থাকত, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত এবং অথীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো”। (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা)
গণেশের রাজনৈতিক ‘অভ্যুত্থান’
১২০৬ সালে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ইনতিকালের পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত ১৩২ বছরে অন্তত ২৩ জন মুসলিম শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন। দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের প্রতি এই শাসকদের আনুগত্য ছিল নামমাত্র। ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেই নামমাত্র সুলতানী শাসনামল হিসেবে চিহ্নিত। শের শাহের সময় (১৫৪০-৪৫) কয়েক বছর বাংলাদেশ দিল্লীর সাথে যুক্ত ছিল। ১৫৭৬ সালে বাজমহলের যুদ্ধে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত দাউদ খান কররানী স্বাধীন সুলতানরুপেই বাংলাদেশ শাসন করেন। স্বাধীন সুলতানী শাসনামলের মধ্যভাগে দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার ইতিহিাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ শাহাদাতবরণ করেন। এরপর ১৪১০ থেকে ১৪১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ইলিয়াশাহী বংশের সাইফউদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহ একের পর এক বাংলার শাসনমঞ্চে আবির্ভূত হন। গণেশের চক্রান্তে তারা সকলেই নিহত হন। শিহাবউদ্দীনকে হত্যা করার পর গণেশ তাঁর বালকপুত্র আলাউদ্দীন ফিরূপ শাহকে রাজা হিসেবে খাড়া করে এ সময় নিজেই কার্যত রাজা হয়ে বসেন। এরপর যখন বুঝতে পারেন, কাউকে আর শিখণ্ডী না রাখলেও চলবে, তখন ফিরুজকে হত্যা করে গণেশ ১৪১৫ সালে সিংহাসন দখল করেন।
রাজা গণেশের সিংহাসন দখলের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের অবসানকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের দু’শতাধিক বছরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ উচ্ছাসিত হয়ে ওঠে। গণেশ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করেন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাড়ায় তার প্রধান লক্ষ্য। রমেশচন্দ্র মজুমদার গণেশের স্বল্পকাল-স্থায়ী শাসনামলকে ‘হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্ঠা’ বলে উল্লেখ করেন। সে সময়ের বহু ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশকে গণেশ পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে তিনি পরিণত করেন কাচারি বাড়িতে।
রাজা গণেশের নেতৃত্বে বর্ণহিন্দুদের এই রাজনৈতিক অভ্যূত্থানের মোকাবিলায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেন। বাংলার এই ভয়াবহ দুর্দিনে শায়খ আলাইল হকের পুত্র সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিম নূর কুতুব-উল-আলম মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর আহ্বানে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কী এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিপদ বুঝে গণেশ বিনা যুদ্দে আত্মসমর্পন করেন। গণেশের পুত্র যদু নূর কুতুব- এর কাছে ইসলাম কবুল করেন এবং জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার শাসক হন।
শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলন
গণেশের রাজনৈতিক অভ্যূত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা সাংস্কৃতিত পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু করে। সুলতানী আমলের শেষদিককার বিদ্যাৎসাহী মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্হাদি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্হ মুসলিম শাসকদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত থেকে ভাষান্তর ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়।
সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে’ সমৃদ্ধ ভাষা আরবীতে তখন তাফসীর, হাদীস. উসুল, তর্কবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থণীতি, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্হরাজি মজুত ছিল। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের উপযোগী এই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার জনগণের সামলে তুলে ধরার কোন ব্যবস্থাই এ সময় করা হয়নি। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষা বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। কিন্তু তাদের তৈরি বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করল, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ছিল না।
সুলতানদরে পৃস্ঠপোষকতায় সৃষ্ট মঙ্গল-কাব্যের প্লাবনে সাধারণ মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাষ্ট্রকে নির্মাণ করার পাশাপাশি জাতি গঠনের কাজে শাসকদের সম্যক সচেতনতার অভাবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষভাগে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়।
শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এমনি পটভূমিতে পরিচালিত হয়েছিল। চৈতন্য সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গ্রন্হ ‘বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ’-এর লিখেছেনঃ
“তিন শত বছরের মধ্যে বাঙালি ধর্ম রক্ষার্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই- মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল”। (পৃষ্ঠা ২৬১)
চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সময় যুগান্তাকারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। বহু হিন্দু লেখক চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে প্লাবিত করে।
এই হিন্দু পনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় কোন কর্মপন্হা সে সময় মুসলিম সমাজে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। এ শূণ্যতার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধেরও জন্ম হয়। এ কারণে বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের বিরাট মিছিলে এক শ্রেণীর মুসলমান কবিও গা ভাসিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভাষায় এরা ছিলেন “বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি”।
প্রেম ও ভক্তির ধর্ম প্রচারের নামে চৈতন্যের নেতৃত্বে ‘পাষাণ্ডি’ বা মুসলমান সংহারের আওয়াজ তোলা হয়। এ ছাড়া চৈতন্যের ধর্মাদর্শের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল আদিরস। স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমকেই চৈতন্য বেশি ঝাঁঝালো মনে করতেন। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি এবং রজকিনী প্রেমের আদিরস সঞ্চার করে চৈতন্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটি বড় অংশকে ইসলামের প্রভাব-সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হন। এ সাফল্য প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেনঃ
“শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে জাতিভেদের জন্যই কিছু উঁচু-বর্ণের হিন্দু ব্যতীত সকলেই মুসলমান হয়ে যেত”।
হিন্দু সাংস্কৃতিক পনরুজ্জীবন আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমানদের বিরুদ্দে চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার। শ্রী চৈতন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসার বাণী প্রচার করেন। তা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার জন্ম দেয়। বাংলায় সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির এটি ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। শ্রীচৈতন্যের বড় হাতিয়ার ছিল হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি, আর পরকীয়ার রজকিনী প্রেমের আদিরস সঞ্চার। চৈতন্যের হিংসানীতির শিকার হয়েছিলেন নবদ্বীপের কাজী। কাজীর বাড়িতে হামলা চালানোর মিছিলে চৈতন্য নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এ হামলা হলো ‘উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রথম ঘটনা’।
চৈতন্য তার শিষ্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামক দুই ভাইয়ের সাহায্যে সুলতাতন হোসেন শাহের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করেন। এ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হোসেন শাহও চৈতন্যের আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।
চৈতন্যপন্হিদের সাংস্কতিক আন্দোলনের প্রকৃতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে চৈতন্যের ব্যর্থতার ওপর আলোকপাত করে মওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেনঃ
“ছোলতান হোসেনের প্রাথমিক দোষ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া, গৌড় রাজ্যের সাধু-সন্যাসীরূপী বৈষ্ণব জনতা বাংলাদেশ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোছলেম শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য যে গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ছোলতান ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথাসময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।……….. চৈতন্যের দেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়াই বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে এমন আশ্চার্যরূপে উধাও হইয়া গিয়াছেন যে, ভক্তরাও তাহার শেষ জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সংবাদই দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেছেন অন্তর্ধান, কেহ বলিতেছেন সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ ইত্যাদি”। (মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস , পৃষ্ঠা ১১০)
সাঁইত্রিশ বছরের আফগান শাসন ও স্বাধীন বারো ভূঁইয়া
স্বাধীন সুলতানী আমলের পর ১৫৩৯ সালে শেরশাহ সূর বাংলায় আফগান শাসন কায়েম করেন। ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত আফগানের ৩৭ বছরের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই আমলে মুসলিম জনজীবনকে ইসলামী আদর্শের আলোকে সংস্কারের ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শের শাহ বাংলার তিনটি ইকলিম বা প্রদেশ ‘ইকলিম সোনারগাঁও’ ইকলিম লাখনৌতি’ ও ইকলিম সাতগাঁও-কে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯টি সরকার ও ৬৮২ টি পরগনায় ভাগ করেন।
১৫৭৬ সালে বাংলায় আফগান শাসনের অবসানের পরও প্রায় তিন যুগ পর্যন্ত পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৬০৮ সালের আগে পর্যন্ত বাংলায় মোগলদের কর্তৃত্ব ছিল একেবারেই সীমিত এলাকায়, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি সেনা-ছাউনিকে ঘিরে। বাকি এলাকায় মসনদে আ’লা ঈসা খাঁ, ওসমান খাঁ লোহানী, মাসুম খান কাবুলী প্রমুখ পাঠান মুসলিম নায়কগণ নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। আকবরের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ এবং তার দ্বীন-ই-ইলাহী নামক নতুন ধর্মমত প্রচারের বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাজী সাহেবের ফতওয়া বাংলার বার ভূঁইয়াদের মোগলবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই ফতওয়া তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে জনসমর্থনের ভিত্তি রচনায়ও সহায়ক হয়। আকবরের জীবদ্দশায় এই এলাকায় মোগলদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।
মোগল কর্তৃত্ব: ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ
সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর অন্যতম অনুসারী সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতি (১৬০৮-১৬১৩) বাংরায় মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১০ সালে তিনি আকবর নগর (রাজমহল) থেকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) রাজধানী স্থানান্তর করেন।
ঢাকার বিখ্যাত নবাবদের মধ্যে শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৮০-৮৮) এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম-উস-শানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে শায়েস্তা খান ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন।
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবাদার মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলাদেশে শাসন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর থেকে রাজধানী মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন। এ কারণে পরবর্তী স্বাধীন শাসকগণ মর্শিদাবাদের নবাব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।
মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে শের শাহের আমলের ১৯টি সরকার ৬৮২ টি পরগণকে ১৩ টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় পুনর্বিন্যাস করেন। মুর্শিদ কুলী খানের পর সুজাউদ্দীন (১৭২৭-৩৯), সরফরাজ খান (১৭৩ ৯-৪০), আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬), সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭) নামমাত্র মোগল কর্তৃত্বের অধীনে কার্যত স্বাধীন নবাবরূপে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন পরিচালনা করেন।
৪
মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমি
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা আকস্মিকভাবে ঘটেনি। এখানে মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমিও তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। পনের শতকের প্রথমার্ধে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে রাজা গণেশের রাজনৈতিক উত্থান-প্রচেষ্টা এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা দীর্ঘদিন থেকেই বাংলায় মুসলিম শাসন উৎখাতের স্বপ্ন দেখেছিল। সামনের সারিতে এসে নেতৃত্ব গ্রহণের হিম্মত তাদের ছিল না। তারা সব সময়ই ষড়যন্ত্রের পেছন দরজা ব্যবহারের অপেক্ষায় ছিল।
এই পটভূমিতে ১৪৯৮ সালের ২০ মে পর্তুগীজ নাবিক ডা গামা ভারতের মালাবার উপকূলে এসে পৌছেন। মুসলিম বণিকগণ তাকে সেখানে বাধা দেন। কিন্তু কালিকটের হিন্দু রাজা জামুরন তাকে অভ্যর্থনা জানান ও নিজ প্রসাদে আশ্রয় দেন। ছয়মাস পর ভাস্কো ডা গামার মাধ্যমে পর্তুগালের রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে জামুরিন এই ঐশ্বর্যশালী দেশে বানির্জ করার জন্য পর্তুগীজ নাবিকদের আমন্ত্রণ জানান। এভাবে ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনধারার সূচনা হয়।
১৫০২ সালে ভাস্কো ডা গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসে কোচিন ও কান্নানোরের রাজার সহযোগিতায় জামুরিনের রাজ্যে হামলা করেন। ১৫০৫ সালে পনের শ’ নাবিকসহ ফ্রান্সিককো দ্যা আলমেডিয়া এদেশে আসেন। মালাবার উপকূলে বণিক ও হজ্জযাত্রীদের জাহাজগুলি এই পর্তুগীজ দস্যুদের হামলাল লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। ১৫০৯ সালে আল ফানসো দ্যা আল বুকার্ক মালাবার উপকূলে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫১০ থেকে ১৫১৫ সালের মধ্যে কোচিন, দমন, দিউ পর্তুগীজ অধিকারে চলে যায়।
এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে তরবারি
ইউরোপে ক্রসেডের পটভূমিতে পর্তুগীজরা ছিল চরম মুসলিমবিদ্বেষী। সেই পটভূমিতে পর্তুগীজরা মুসলিম ভারতে এসেছিল এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে।
ইউলিয়াম হান্টারের ভাষায়ঃ
They were not traders, but knighterrant and Crusaders…….. Their national temper had been formed in their contest with the Moors (Muslims) at home, (A Brief History of the Indian People, 1868, P-167)
ইংরেজ বণিকরা এদেশে প্রথম আসে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬০২ সালে ডাচ, ১৬০৪ সালে ফরাসী, ১৬১২ সালে দিনেমার, ১৬৩৩ সালে স্পেনীয়, ১৭২৩ সালে আস্ট্রিয়, ১৭১৩১ সালে সুইডিশ এবং ১৭৫০ সালে ক্রশীয় বণিকরা বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে এদেশে আসে।
১৬২০ সাল থেকে ইংরেজ বণিকরা সুরাট, আজমীর ও পাটনায় সীমিত আকারে ব্যবসা করছিল। ১৬২৪ সালে তারা উড়িষ্যার বালাশেরে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৫১ সালে ইংরেজরা হুগলীকে কুঠি স্থাপন করে। তখন থেকেই তারা বর্ণহিন্দু ব্যবসায়িক মিত্রদের সহযোগীতা নিয়ে এদেশের রাজনীতির দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে।
১৬৮২ সালে উইলিয়াম হেজেজ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির এজন্ট নিযুক্ত হন। এরপর বাণিজ্যিক শর্ত লঙ্ঘন, সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ, হুগলীতে দুর্গ নির্মাণ, কর প্রদানে কারচুপি, দেশীয় ব্যবসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ এবং বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কর্মচারীদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৮৬ সালে ইংল্যান্ড থেকে সৈন্য বোঝাই জাহাজ এসে পৌছে বাংলার সুবাদার ও ভারত সম্রাটের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য।
এর আগে ১৬৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বার্ষিক কুড়ি পাউন্ড বেতনের রাইটার-এর চাকরি নিয়ে ভাগ্যন্বেষী জোব চার্নক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজার কুঠিতে যোগ দেন। দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৬৮৫ সালে তিনি হুগলী কুঠি’র চীফ এজেন্ট নিযুক্ত হন। হুগলী কুঠির বকেয়া শুল্ক বাবদ তেতাল্লিশ হাজার টাকা আদায়ের জন্য ঢাকার সুবাদার জোব চার্নকের বিরুদ্দে ডিক্রী জারি করেন এবং তাকে ঢাকায় তলব করেন। চার্নক কাসিমবাজারে পালিয়ে যান। সুবাদারের লোকেরা তাকে সেখানে ধাওয় করলে রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে তিনি হুগলীর কুড়ি মাইল দক্ষিণে জঙ্গলাকীর্ণ সুতানুটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। ১৬৮৭ সালে জোব চার্নক সুতানুটি থেকে পালিয়ে যান মাদ্রাজে।
ইংরেজদের নানা কুকর্মে রুষ্ট হয়ে শায়েস্তা খান বাংলায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খানের স্থলে ইবারহীম খাঁ সুবাদার হন। ইংরেজ বণিকরা অতীত অপকর্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে বহু আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধা পুনরায় ফিরে পায়।
১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নক তৃতীয় বারের মতো সুতানুটির ঘাটে অবতরণ করেন। কৌশলগত যাবতীয় সুবিধার দিক বিবেচনা করে তিনি সেখানেই কেন্দ্র স্থাপন করেন।
গঙ্গাতীরের ধান ক্ষেত, কলাবাগান, জলাভূমি ও কয়েকটি কুঁড়েঘর নিয়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলকাতা নামক তিনটি স্যাঁতস্যাতে জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামকে কেন্দ্র করে তখন থেকেই ভারতের মুসলিম সাম্রজ্যের অভ্যন্তরে ইংরেজ ‘নাবিক, বণিক ও লোফার’ এবং তাদের এদেশেীয় বর্ণহিন্দু কোলাবোরেটদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে বেড়ে উঠতে থাকে শহর কলকাতা। এ. কে. রায়ের ভাষায়:
“The fair dealings of the English traders with Hindu marchatns and the latter’s faithfulness to the Company became the talk of the day.” ( A Short History of Calcutta)
এ ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিতে চারদিক থেকে যারা ভিড় করতে লাগলো তাদের পরিচয় হলো-
“They were mainly Hindus because it was easier to manage the submissibe Hindus than the refractory Muslims.” (History of the Freedom Movement of India)
আঠার শতকের শুরু থেকে ইংরেজ বণিক ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্র ধরে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীকে তাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। তারা সকলেই ছিল হিন্দু। ১৭৩৯ সালে কাসিমবাজারে কোম্পানির সকল এদেশীয় কর্মচারীর পরিচয়ও ছিল অভিন্ন। এভাবেই ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রী গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসনেরে অবসান ছিল এ মৈত্রীজোটের অভিন্ন লক্ষ্য। এস.সি হিল তাঁর গ্রন্হ ‘বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭’- এ প্রমাণপঞ্জীসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
আলীবর্দী খান ১৭৪০ সালে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এর পর থেকেই তাঁকে একদিকে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় মারাঠা বর্গী ও রোহিলাদের সাথে লড়াই চালাতে হয়। এই দ্বৈত সংকটের সুযোগে ১৭৫৪ সালে ইংরেজরা কলকাতায় উইলিয়ান দুর্গ নির্মাণ করে।
ইংরেজ কর্মচারীদের তখনকার চিঠিপত্র দেখা যায় যে, মুসলিম শাসন ধ্বংসের ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্র তখন পরিণত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চরম সুযোগ উপস্থিত হয়। তারা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে প্রথমে ইয়ার লতীফকে পরে বিশেষ বিচেনায় মীর জাফরকে শিখণ্ডী হিসেবে বেছে নেয়।
১৭৫৭ সালের ১মে কলকাতায় ইংরেজ কমিটি তাদের বর্ণহিন্দু দালালদের সহায়তায় মীর জাফরের সাথে এগার দফা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। সেই ষড়যন্ত্রমূলক এগার দফা চুক্তির ভিত্তিতেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম বাগানে যুদ্ধ প্রহসনের মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন হয়। সেই সাথে লুপ্ত হয় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা এবং কালক্রমে ভারতর্ষ- আসমুদ্র হিমাচল।
পলাশীর এই যুদ্ধকে কোন কোন হিন্দু লেখক ‘দেবাসুর সংগ্রাম’ নামে অভিহিত করেছেন। এখানে ‘দেবতা’ হলেন ক্লাইভ আর ‘অসুর’ রূপে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে জীবন দানকারী তরুন নবাব সিরাজকেই চিহ্নিত করা হয়। পলাশীর শোকাবহ বিপর্যয়কে কলকাতায় ‘পলাশীর বিজয়োৎসব’- রূপে পালন করা হয় এবং দুর্গাদেবীর অকাল-বোধনের মাধ্যমে বসন্তকালীন দুর্গোৎবকে শরাদীয় দুর্গোৎসবরূপে পালন করে ক্লাইভকে দেবতুল্য সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করা হয়।
মীর কাসিমের শেষ প্রতিরোধ
১৭৫৭ সালের ২৯ জুন পরাধীন দেশের পুতুল নবাবরূপে মসনদে বমেন মীর জাফর। ৩ জুলাই রাজকীয় শান-শওকতের সাথে দুইশ’ নৌকা বোঝাই সোনা-চাঁদি মুর্শিদাবাদ থেকে কলতাকা পাঠনো হয় ইংরেজদের ‘যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ’ হিসেবে। এভাবেই ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের সম্পদ লণ্ঠনের মাধ্যমে নগর কলকাতার উত্থান ঘটে।
ইংরেজদের পৌনঃপুনিক টাকার দাবি মিটাতে মীর জাফরের রাজকোষ শূন্য হয়। ইংরেজদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মীরজাফর ওলন্দাজদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইংরেজরা মীর জাফরকে সরিয়ে দিয়ে ১৭৬৫ সালের অক্টোবর মাসে তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসায়।
মীর কাসিম তার অতীত ভূলের কাফফারা আদায় করতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেন। দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তিনি। ফলে ইংরেজদের সাথে শুরু হয় প্রত্যক্ষ লড়াই। ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ হলো গিরিয়ায়, উদয়নালায়, পাটনায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম আশ্রয় নিলেন আযোধ্যায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন তিনি। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী বেণী বাহাদুর ও বেনারসের বলওয়ান সিংহ ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাতের পুরনো খেলায় লিপ্ত হয়। ফলে মীর কাসিম ও সুজাউদ্দৌলার যৌথ বাহিনী ১৭৬৪ সালের এপ্রিলের এক যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়।
এরপর ১৭৬৪ সালে ২২ অক্টোবর দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যায় নবাব ও মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনী বখশারে ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। এই যুদ্ধের সময়ও পুনরাবৃত্তি হলো একই নাটকের। সম্রাটের দেওয়ান সেতাব রায়, অযোধ্যার নবাবের মন্ত্রী বেণী বাহাদুর ও মীর কাসিমের খ্রিষ্ট্রান সেনাপতি মার্কাট ও আরাটোনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়।
বখশারে বাংলার জনগণের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেল। বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব কার্যত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ক্লাইভ এক চুক্তির ভিত্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রশাসনের ফরমান আদায় করে নিলেন।
অন্য দিকে ভগ্ন-হৃদয় মীর কাসিম দীর্গ বারো বছর মধ্য-ভারত সফর করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান। ১৭৭৭ সালের ৬ জুন দিল্লীর আজমিরী দরজার বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফিররূপে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন মীর কাসিম। তার মাথার নিচে রাখা নামাঙ্কিত চাদর দেখেই বাংলার এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত নবাবক সেদিন শনাক্ত করা সম্ভব হয়।
১৭৯৬ সালে ঢাকার নামেমাত্র নবাব শামসউদ্দৌলা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারত, আফগানিস্তান ও পারস্যের মুসলতান শাসকদের সাথে গোপন যোগাযোগের ভিত্তিতে ওমানের মস্কট থেকে আরব জাহাজে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে এবং সৈন্যরা শামসউদ্দৌলার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।
কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই ‘ষড়যন্ত্রের’ আভাস পেয়ে ১৭৯৯ সালে শাসসউদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে। নবাব শামসউদ্দৌলা ১৮৩১ সালে মারা যান।
৫
পলাশী-উত্তর বাংলার চালচিত্র
১৭৫৭ সালে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য-বিপর্যয় এবং ১৭৬৪ সালে বখশারে মীর কাসিমের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে পাঁচশ’ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নাম ক এক বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে। ফলে অতি অল্প সময়ের লুণ্ঠন-শোষণে বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতিসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয়। বিশেষ করে ভারতের পুরাতন শাসক মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথা তুলতে না পারে সেজন্য সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়।
ইংরেজ ও তার এদেশীয় দালালদের লুণ্ঠন
ইংরেজরা দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়েরা আনুষ্ঠানিক ফরমান আদায় করে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট তারিখে। কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকেই তারা শাসন কর্তৃত্ব কক্ষিগত করেছিল। মীর জাফরকে ‘পুতুল নবাব’ সাজিয়ে লর্ড ক্লাইভ শুরু থেকেই ‘প্রকৃত নবাব’ সেজে বসেছিলেন। আর এই পুতুল নবাবীর সূচনাকাল থেকেই ইংরেজনা এদেশে ইতিহাসের নজীরবিহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়েছিল।
খোদ লর্ড ক্লাইভ পলাশীর ‘যুদ্ধ জয়ের’ বখশিশ হিসেবে মীর জাফরের কাছ থেকে ২ লাখ ৩৪ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে রাতারাতি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হন। মীর জাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছয়জন কর্মচারীকে ১,৫০,০০০ পাউন্ড উৎকোচ প্রদান করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ পাউন্ড ঘুষ আদায় করেন। (পি. রবার্টস: হিস্টরী অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮; ড. এম এ রহীম : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৯)
কোম্পানির ও কলকাতার অধিবাসীদের ‘ক্ষতিপূরণ’ হিসেবে এবং সৈন্য ও নৌবহরের ব্যয় বাবদ কোম্পানি আদায় করে মোট ২৫,৩১,০০০ পাউন্ড। তাছাড়া মীর কাফর ইংরেজ কর্মকর্তাদের খুশি করতে ৬,৬০,৩৭৫ পাউন্ড উপঢৌকন দেন। বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারী মীর জাফরের কাছ থেকে চব্বিশ পরগণা জেলার জমি ছাড়াও ৩০ লাখ পাউন্ড ‘ইনাম’ গ্রহণ করেছিল। ১৭৫৯ সালে ক্লাইভকে ৩৪,৫৬৭ পাউন্ড বার্ষিক আয়ের দক্ষিণ কলকাতার জায়গীর প্রদান করা হয়। (ব্রিজেন কে গুপ্ত : সিরাজউদ্দৌলা এন্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃষ্ঠা ৪১)।
ইংরেজদের বিভিন্ন রূপ টাকার দাবি মেটাতে মীর জাফর রাজকোষ শূণ্য করে ফেলেছিলেন। মীর কাসিম এই ঋণ পরিশোধ এবং মসনদের বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীদেরকে ২০০০,০০০ পাউন্ড দিয়েছিলেন। (ড. এম এ রহীম : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬)
মীর জাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলা ১৭৬৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর মসনদ লাভের জন্য কোম্পানির কর্মচারীদেরকে যে ঘুষ দেন তার পরিমাণ ছিল ৮,৭৫,০০০ টাকা। রেজা খান ২,৭৫,০০০ টাকার উৎকোচের বিনিময়ে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবাবের নবাব-নাযিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০)
উৎকোচ নামক দুর্নীতি এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে আমদানী করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত মাত্র দশ বছরে ষাট লাখ পাউন্ড আত্মসাৎ করেছিল। এ কথা ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। (Fourth Parliamentry Report 1773, P-534; সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৯)।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অর্থ বিলাতে নিয়ে যায়। ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলে তিনি নিজ আচরণ সমর্থন করে বলেন:
“পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তা আপনারা ভেবে দেখুন। একজন বড় রাজার ভাগ্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। একটি সমৃদ্ধ নগর আমার দয়ার প্রতিক্ষায় আছে। আমার মুখের সামান্য হাসিতে কৃতার্থ হওয়ার জন্য ধনী মহাজনরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। আমার দুই পাশে স্বর্ণ মণিমুক্তায় পূর্ণ সিন্দুকের সারি এবং এগুলি কেবল আমারই জন্য খোলা হয়েছে। (পার্লামেন্ট কমিটির) সভাপতি মহোদয়, এ মূহূর্তে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, তখন আমি কিভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলাম”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)
বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনে ইংরেজরা একা ছিল না। তাদের পাশে ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের সহচর এদেশী দালাল, গোমস্তা ও বেনিয়ানগোষ্ঠী। তাদের শোষণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ব্যারিংটন মেকলে স্বয়ং মন্তব্য করেছেনঃ
“কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য নয়, নিজেদের জন্য, প্রায় সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তারা দেশী লোকদের উৎপন্ন দ্রব্য অত্যন্ত কম দামে বেচতে এবং অন্যদিকে বিলাতি পণ্য খুবই চড়া দামে কিনতে বাধ্য করত। কোম্পানি তাদের অধীনে একদল দেশী কর্মচারী নিয়োগ করত। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে এলাকায় যেত, সে এলাকা ছারখার করে দিত। সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করত। ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার উচ্চপদস্থ (ইংরেজ) মনিবের শক্তিতে বলীয়ান। আর এই মনিবদের প্রত্যেকের শক্তির উৎস ছিল খোদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। (তাদের ব্যাপক লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে) শীঘ্রই কলকাতায় বিপুল ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত হলো। সেই সাতে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালো। বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্হ একথা ঠিক, কিন্তু ও ধরনের (ভয়ঙ্কর) শোষন ও উৎপীড়ন তারাও কোনদিন দেখেনি”। (Macaulay : Essaya on Lord Clive, P-63; সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০)
ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা লাভের আগে দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও তাদের পণ্য-ব্যবসা সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করতে পারেনি। এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কাঠামো অক্ষত রেখে তাদের এই ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল না। আগে যা কখনো সম্ভব হয়নি, পলাশীর পরে এখন তা সম্ভব হলো। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা হাত পাওয়ার সাথে সাথে নজীরবিহীন ক্ষিপ্রতার সাথে বাংলা ও বিহারের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের এই ভিত্তি ও কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে দেয়।
এই সমাজকে ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রক্রিয়া হিসেবে তারা-
ক. ভুমি-রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা চালু করে এবং
খ. ভূমি-রাজস্ব হিসেবে ফসল বা উৎপন্ন দ্রব্য আদায়ের প্রচলিত পদ্ধতির বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।
ইংরেজ প্রবর্তিত এই নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেন :
“এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আঘাতে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইল। বিহার ও বাংলা শ্মশান হইয়া গেল”। (সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১০)
ইংরেজ শাসনের আগে এ দেশের শাসকরা সমগ্র গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। চাষী জমির ফসলের দ্বারা গ্রাম-সমাজের মাধ্যমে এই রাজস্ব আদায় করত। ইংরেজরা গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের এ ব্যবস্থআ লোপ করে কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং ফসলের বদলে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের রেওয়াজ চালু করে। এভাবে এদেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ধ্বংস করে তারা সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থা নতুনভাবে গড়ে তোলার আয়োজন করে। কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশি খাজনা ও কর আদায় করে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এক নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এই জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজরা বাংলা ও বিহারের নিষ্ঠুরতম দস্যু সরদারদেরকে ‘নাযিম’ নিয়োগ করে।
নাযিম নামক এই দস্যুদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোম্পানির দলিলপত্র থেকে জানা যায়। বাংলা ও বিহারের রাজস্ব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ১৭৭২ সালের ৩ নভেম্বর ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন :
“নাযিমরা জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশি পারে কর আদায় করে নিচ্ছে। জমিদাররাও নাযিমদের কাছ থেকে চাষীদের লুণ্ঠন করার অবাধ অধিকার লাভ করেছে। নাযিমরা আবার তাদের সকলের (জমিদার ও কৃষকদের) সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার রাজকীয় বিশেষ অধিকারের বলে দেশের ধন-সম্পদ লুট করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২)
১৭৬৫-৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর সে বছরই তারা প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি ২০ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে আদায়ের পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের রাজস্ব-নীতি ও ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :
“এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের ওপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চাপিয়ে বসে। এই পিরামিডের শীর্ষদেশে রহিল ইংরেজ বণিকরাজ, তার নীচে রহিল বিভিন্ন প্রকার উপস্বত্বভোগীর দলসহ জমিদারগোষ্ঠী। এই বিরাট পিরামিডের চাপে বাংলা ও বিহারের অসহায় কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এদে দাঁড়াল”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২)
ব্যবসায়ের নামে ‘প্রকাশ্য দস্যুতা’
বাংলার জনগণের কাছ থেকে ছিনেয়ে নেওয়া বিপুল ভূমি-রাজস্ব, কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় করা ঘুষ, ব্যবসায়ের নামে ব্যক্তিগত লুণ্ঠন এবং এদেশের টাকা দিয়ে এখানে নামমাত্র মূল্যে পণ্য কিনে ইউরোপে চালান করা হতো। ফলে যে মুনাফা তারা লাভ করত, তার পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য রকম স্ফীত। এ দেশের জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাজস্বের টাকার একাংশ দিয়ে এ দেশেরই কারিগরদের তৈরি পণ্য-সম্ভার নামমাত্র মূল্যে কেড়ে নিয়ে ইউরোপে চালান দিয়ে মুনাফা করা হতো বিপুল অংকের টাকা। সমুদয় গ্রাম করত ‘কোম্পানি-লগ্নি’। এই অদ্ভুত লগ্নির চেহারা ছিলো :
“বাংলাদেশের জনগণের টাকা, বাংলার কারিগরদের তৈরি দ্রব্য, কিন্তু মুনাফা কোম্পানির। কার্লমার্কস, রেজিনাল্ড প্রমুখ লেখক এই ‘ব্যবসায়ের’ নাম দিয়েছেন ‘প্রকাশ্য দস্যুতা”। (পূর্বোক্ত)
ব্যবসায়ের নাম ইংরেজ বণিক কোম্পানির এই দস্যুতার মুখে বহু শিল্প-কারিগর উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য নিজেদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। অনেকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩- এই ছয় বছরে কৃষকদের সাথে কারিগরদের একটি অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয়। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনল্ডস লিখেছেন :
“ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকার বিশ্বখ্যাত মসলিনের এক তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ-পীড়নে অস্থির হয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল”। (রেজিনাল্ড রেনল্ডস : সাহিবস ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৫৪)
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ
ইংরেজদের নয়া রাজস্বনীতির কারণে কৃষকরা খাজনার টাকা যোগাড় করার তাকিদে বছরের খাদ্য-ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা মুনাফা শিকারে সেরা সুযোগরূপে বেছে নেয় চালের মজুতদারীকে। তারা চালের একচেটিয়া ব্যবসা কুক্ষিগত করার জন্য বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ব্যবসা-কেন্দ্র খুলে ফসল ওঠার সাথে সাথে চাউল মজুদ করে রাখত। পরে সুযোগ বুঝে চাষীদের কাছে তাদেরই রক্ত পানি করা শ্রমের ফসল কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করত। তাদের এই একটি ব্যবস্থাই ‘ভারতের শস্য-ভাণ্ডার’ নামে খ্যাত, মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ, যেখানে মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ’ বছর মানুষ কখনো দুর্ভিক্ষের সাথে পরিচিত ছিল না, সেই বাংলা ও বিহারকে দুর্ভিক্ষের স্থায়ী কেন্দ্র পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
১৭৬৯ সালে ফসল ওঠার সাথে সাথে ইংরেজরা বাংলা ও বিহারের সকর ফসল কিনে ফেলে। সারা বছর মজুদ করে রেখে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সাল) সে খাদ্য-শস্য কয়েকগুণ বেশি দামে বেচতে শুরু করে। কয়েক বছরের নিষ্ঠুর শোষণে সর্বস্বান্ত কপর্দকশূণ্য কৃষক ও কারিগরদের পক্ষে এত চড়া দামে সে চাল কিনা সম্ভব ছিল না। ফলে বাংলা ও বিহারে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। তৎকালীর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হোস্টিংস-এর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল এক কোটি পঞ্চাশ লাখ।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত এই মহা দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ লেখক ইয়ং হাসবেন্ড লিখেছেনঃ
“তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হলো চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এই পণ্যের জন্য তারা যে দাম চাইবে, তাই তারা পাবে।……. দেশে যা কিছু খাদ্য ছিল তা (ইংরেজ বণিকদের) একচেটিয়া দখলে চলে গেল। ……… খাধ্যের পরিমাণ যত কমতে লাগল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির-দুঃখময় জীবনের ওপর পতিত হলো এই পুঞ্জিভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটি এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের শুরু মাত্র। ………. দেশিয় জনশক্রদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষেণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা ছিল, তা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনো দেখেনি বা শুনেনি”।
তিনি আরো লিখেছেনঃ
“চরম খাদ্যভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সাথে সাথে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল, সেখানেই দিন-রাত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হলো এত শীঘ্র ও এতই বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূণ্য ইংরেজ ভদ্রলোক এ্হ ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ষাট হাজার পাউন্ড ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন”। [Young Husband : Transactions in India (1786 ; P. 123-24]
‘মৃত্যু-ব্যবসায়ী’ ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দালালদের সৃষ্ট এই ছিয়াত্তরের মহা-মন্বন্তর সম্পর্কে ইয়ং হাসবেন্ড মন্তব্য করেন :
“বাংলার সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ নতুন অধ্যায়ের যোজনা করেছে, যা মানব সমাজের সমস্ত অস্তিত্বকালব্যাপী ব্যবসানীতির এই ক্রর উদ্ভাবনা-শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে; অলঙ্ঘণীয় মানবাধিকারসমূহের ওপর কত ব্যাপক, গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাটার চলতে পারে, এই অধ্যায়টি তারও কালজয়ী নির্দশন হয়ে থাকবে”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩১)
এ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার বিবরণ দিয়ে এল. এস. এস. ও মলী লিখেছেন :
“চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাদের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হলো। কিন্তু কে তাদের কিনবে? কে তাদের খাওয়াবে? বহু এলাকায় জীবিত লোকেরা মরা মানুষের গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্ঠা করেছে। নদী-তীর লাশ আর মমূর্ষুদের দেহে ছেয়ে গিয়েছিল। মরার আগেই মুমূর্ষ লোকদের দেহের গোশত শিয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলত”। (L.S.S.O Molley : Bengal. Bihar and Orissa Under British Rule, P-113.)
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে পরবর্তী যুগের ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :
“১৭৬৯ সনের শীতকালে বাংলার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার জের দুই পুরুষ ধরে চলে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ইতিহাস ছিল চমকপ্রদ সামরিক-সাফল্যে প্রাণবন্ত কোম্পানির প্রশংসাপত্রসহ ধারাবাহিক সংগ্রামগুলোর সমাহার। সুতরাং যুদ্ধ বা সংসদীয় বিতর্কের সাথে সংযোগহীন এই ঘটনা (দুর্ভিক্ষ) সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই বললেই চলে। …… ১৭৭০ সনের সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে গণমড়ক অব্যাহত থাকে। কৃষকরা গবাদিপশু বিক্রি করে দেয়: বিক্রি করে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি; তারা বীজধান খেয়ে ফেলে; নিজেদের ছেলেমেয়েদের তারা বিক্রি করতে থাকে এবং তারপর তারও কোন ক্রেতা পাওয়া যায় না। তারা গাছের পাতা, ক্ষেতের ঘাস খেতে থাকে এবং ১৭৭০ সনের জুন মাসে দরবারের আবাসিক প্রতিনিধি শভ ভক্ষণের সত্যতা সমর্থন করেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, রোগগ্রস্ত হতভাগ্যের দল দিবারাত্রি বড় বড় নগরগুলো পূর্ণ করতে থাকল। বছরের প্রথমে মহামারির প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। …….. অর্ধমৃতদের সাথে শবদেহের অবিন্যস্ত স্তূপে পথ অবরুদ্ধ, নির্বিচারে কবর দিয়েও সমস্যার আশু সরাহা হলো না; এমন কি প্রাচ্যের ঝাড়ুদার হিসেবে খ্যাত শিয়াল-কুকুরের দলও সাফাইয়ের বিতৃষ্ণাকর কাজে ব্যর্থ হলো এবং অবশেষে পচাগলা শবদেহগুলো নাগরিকের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলল।…….. সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী ১৭৭০ সনের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয়। জুন মাসে মৃত্যু-সংখ্যা হিসেবে বলা হয় ‘সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি ষোল জনে ছয় জন মৃত’; এবং হিসাব করে দেখা হয় যে, ‘কৃষকসহ খাজনা প্রদানকারী জনসাধারণের অধিকাংশ ক্ষুধার জ্বালায় ধ্বংস হবে’। বর্ষাকালে (জুলাই হতে অক্টোবর) জনশূণ্যত এত প্রকট হয়ে উঠে যে, আতংকগ্রস্ত সরকার পরিচালক-সভার কাছে ‘দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট কৃষক ও ক্ষুদে উৎপাদকদের (কারিগর) সংখ্যা ‘সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে”। [ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : গ্রাম বাংলার ইতিকথা (এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল গ্রন্হের অসীম চট্টোপাধ্যায় কৃত তরজমা), পৃষ্ঠা ১০-১৭]
এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এই নযীরবিহীন গণমৃত্যু সম্পর্কে ইংরেজরা কতটা নিরুদ্বেগ ও বেপরোয়া ছিল তার বিবরণও হান্টারের লেখায় বিধৃত। ইংরেজরা তাদের লুণ্ঠনের পরিমাণ সম্পর্কেই আগ্রহী ছিল। এদেশের মানুষের ব্যাপারে তাদের জাতীয় মানসিকতা ছিল অদ্ভুত রকমের হৃদয়হীন নির্লিপ্ততার।
হান্টার লিখেছেনঃ
“১৭৭২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণ বাংলাকে একটা বিশাল গুদামখানা হিসাবে দেখত, যেখানে বেশ কছু দুঃসাহসী ইংরেজ মোটা লাভে এক বিশাল ব্যবসা চালাচ্ছে। বিপুল দেশীয় জনসংখ্যা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল ঠিকই, এটা যেন তারা একটা আকস্মিক পরিস্থিতি বলে বিবেচনা করত এবং বর্তমানে আমরা নাটাল বা প্রিয়েরীলিয়নের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে আগ্রহ বোধ করি, তার চেয়েও কম আগ্রহ তারা এ সম্বন্ধে বোধ করত”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭)
এ দেশের জনগণের ব্যাপারে ইংরেজদের মানসিকতার প্রমাণ পাওযা যায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে তাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা থেকে। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায়ঃ
“বিশ হাজার লোক যে জেলায় প্রতি মাসে মারা যাচ্ছে, সে জেলার ত্রাণ-কার্যের জন্য কোম্পানি-সরকার একশত পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করে। চার লাখ উপবাসী মানুষের প্রতিদিনের সাহায্যের জন্য এক প্রাদেশিক পরিষদ ‘গভীর বিবেচনার পর মহানুভবতার সাথে’ দশ শিলিং মূল্যের চাউল অনুমোদন করেন। ‘অর্ধেক কৃষক ও প্রজা উপবাসে মারা যাবে’ এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও কোম্পানি কাউন্সিল তিন কোটি মানুষের ছয় মাসের নির্বাহের জন্য অনুদান ধার্য করেন চার হাজার পাউন্ড”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯)
এই অনুদান প্রকৃত ভুক্তভোগীর হাতে যায় কিনা, সে সম্পর্কেও হান্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেনঃ
“ যে দেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণ কৃষিজীবী, সেখানে গণমৃত্যুর ফলে আনুপাতিক হারে জমি অনাবাদি থাকে। বাংলাদেশের জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশ মারা যায় এবং এক তৃতীয়াংশ আবাদি জমি দ্রুত পতিত জমিতে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর এত বেশি জমি অকর্ষিত থাকে যে, দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রজাদেরকে বাস্তুত্যাগ করে পরিষদশাসিত এলাকায় আনার জন্য (কোম্পানি সরকারের) পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। দুর্ভিক্ষ –পরবর্তী প্রথম পনের বছরে জনশূন্যতা অবিচলিতভাবে বাড়তে থাকে। ঘাটতির সময়ে সবচে বড় বিপর্যয়ের শিকার হয় শিশুরা এবং ১৭৮৫ সন পর্যন্ত বৃদ্ধরা মারা যায়। কিন্তু তাদের শূন্যস্থান পুরণের জন্য নতুন কোন প্রজন্ম ছিল না। জমি পতিত পড়েই রইল এবং তিন বৎসরের সতর্ক তদন্তের পর ১৭৮৯ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার কোম্পানির এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলের বন্যজন্তু-আকীর্ণ জঙ্গল বলে ঘোষণা করেন”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩১)
সারা দেশে যখন মৃত্যুর এই বিভীষিকা চলছে, তখন ১৭৭২ সালে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তৎকালীন বাংলা ও বিহারের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেনঃ
“প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তার ফলে চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্বের চেয়ে বেশি হয়েছে। যে কোন লোকের পক্ষে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, এরূপ একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব তুলনামূলকভাবে কম আদায় হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে”। (পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট)
এ প্রসঙ্গে হান্টার লিখেছেনঃ
“১৭৭২ সালে, পুরোনো চাষীরা মরীয়া হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিলে তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং বকেয়া খাজনার দায়ে কলকতার ‘ঋণগ্রস্তদের কারাগারে’ তাদেরকে কয়েদ করা হয়। রাজস্ব নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে একই ঘটনা ঘটে। দুর্ভিক্ষের প্রায় ২০ বছর পর ব্রিটিশরা জেলার দায়িত্ব গ্রহণকালে জেলাগুলো বকেয়া খাজনাজনিত বন্দীতে পূর্ণ ছিল এবং কোনো বন্দীরই পুনঃমুক্তির কোনো আশা ছিল না্। দেশ যখন প্রতিটি বছরের সাথে আরো অধঃপতিত হচ্ছে তখন ইংরেজ সরকার ক্রমাগত বর্ধিত খাজনা দাবি করতে থাকে। ১৭৭১ সনে আবাদি জমির এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি সরকারি হিসেবে পরিত্যক্ত বলে দেখানো হয়। ১৭৭৬ সনে এই হিসেবে সমগ্র আবাদি জমির অর্ধাংশেরও বেশি দাঁড়ায়, প্রতি সাত একর আবাদি জমির সাথে চার একর পতিত থাকে। অন্যদিকে কোম্পানির দাবি ১৭৭২ সনে ১০,০০,০০০ পাউন্ডের কম হতে বেড়ে ১৭৭৬ সনে প্রায় ১১,২০,০০০ পাউন্ডে দাঁড়ায়”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)
বাংলায় ইংরেজ বণিক শ্রেণী, আর তাদের লুণ্ঠন-সহচর বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাপা, জগতশেঠ-আলম চাঁদ প্রমুখ কোটিপতি লগ্নি-পুজির মালিক, তাদের আত্মীয়-স্বজন, নব্য বিত্তশালী এজেন্ট, বেনিয়া, নিলামে জমিদারী খরিদকারী নতুন বর্ণহিন্দু শহুরে জমিদার শ্রেণী, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা তাদের দালাল, নায়েব, গামস্তা প্রভৃতি অর্থলগ্নীর দল তাদের গোলা, মড়াই, আড়ত, কাচারীতে সারা বাংলার খাদ্যশস্য মজুত রেখে যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। স্বল্পকালের লুণ্টন-শোষণের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। জগত শেঠ, আলম চাঁদ প্রমুখ কোটিপতিগোষ্ঠী এ সময় সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। কেউ প্রত্যক্ষ মজুতকারবারী, কেউ বেনামী অংশীদার, আর কেউ অর্থের লগ্নিকারী। ইংরেজ বণিকশ্রেণীর শাসনকালের ইতিহাসে এই সময়কাল নিষ্ঠুরতার বিচারে তুলনাহীন। ইংরেজ বণিকশ্রেণীর এই অদ্ভুত শাসনকে ইংল্যান্ডের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এডমন্ড বার্ক মানব সভ্যতার ইতিহাসে ‘মৃত্যুর শাসন’ আর ওরাঙ ওটাঙ বা ‘নেকড়ের শাসন’ নামে অভিহিত করেছেন। (Speeches of Edmaund Bark)
কোম্পানি শাসনের এই ভয়াবহ রূপ দেখেই বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যডাম স্মিথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেনঃ
“কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির একচেটিয়া শাসনই যেকোন দেশের বিভিন্ন প্রকার শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসন”। (Adam Smith : Essays on Political Economy, P-131)
সমসাময়িক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্হ সিয়ারুল মুতাআখখেরীন-প্রণেতা এই দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হয়ে লিখেছেনঃ
“ইয়া আল্লাহ। তোমার দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বান্দাহদের সাহায্যের জন্য একবার তুমি নেমে আস। এই অসহনীয় উৎপীড়ন থেকে তুমি তাদের উদ্ধার কর”। (গোলাম হুসাইন তাবাতাবাই : সিয়ারুল মুতাখাখেরীন- গোলাম হুসাইন খান অনূদিত)
ভূমি-ব্যবস্থার ধ্বংস ও কৃষক শোষণের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’
ইংরেজ ও এদেশীয় জনশক্রদের সৃষ্ট ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর বাংলা ও বিহারের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের শেষ চিহ্ন মুছে দিয়েছিল। ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞের এই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়েই ইংরেজ বণিক-শাসকরা তাদের কৃষক-শোষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের দ্বারা মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত ইজারা, জমিদারী, একে একে খসিয়ে ফেলে নতুন হিন্দু জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীর আমদানি করা হয়। যেসব হিন্দু কর আদায়কারী ঐ সময় পর্যন্ত নিম্ন পদের চাকরিতে নিযুক্ ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয় (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান; এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত পৃষ্ঠা ১৪১)। ফলে অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো একেবারে উৎখাত হয়।
হেস্টিংস-এর চুক্তি (১৭৭২-৯৩) ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে এদেশের বুনিয়াদি ও পুরনো জমিদারদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তন। নিলামের ডাকে যারা প্রচুর অর্থ দিতে পারতো, তাদেরকেই জমিদারী দেওয়া হতো। পুরনো জমিদারদের পক্ষে ইংরেজদের চাহিদা মাফিক অর্থ দেওয়া সম্ভব ছিল না।
প্রচুর জমানো টাকা নিয়ে এগিয়ে এল বেনিয়ান, গোমস্তা, মহাজন আর ব্যাংকের মালিকরা। লুণ্ঠন-শোষণের মাধ্যমে অর্জিত নগদ টাকার জোরে রাতারাতি তারা জমিদার হয়ে বসল। তাদের সকলেই ধর্মীয় পরিচয় হিন্দু। তাদের গোত্রীয় পরিচয় দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিক, শীল, তিলি বা সাহা। তাদের অনেকেরই পূর্ব পরিচয় তারা পুরাতন জমিদারদের নায়েব কিংবা গোমস্তা। আর তাদের অভিন্ন পরিচয় তারা বাংলা নব্য-প্রভু শাসকদের দালালরূপী লুটেরা-শোষক।
মুসলমান জমিদারদের জমিদারী দখল এবং মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে ষড়যন্ত্রে মিলিত হয়। পাদ্রীদের পরার্শে কোম্পানি সরকার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আয়মা লাখেরাজ ও তৌজী লাখেরাজের দলিল-দস্তাবেজ ও সনদ-পাঞ্জা কোম্পানি সরকারে দাখিল করার জন্য এক আকস্মিক নির্দেশ জারি করে। মুসলমানদের অনেকেই এসব দলিল-পত্র মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করতে পারল না। তাদের সমুদয় লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করা হয়। এছাড়া মুসলমানদের অধিকাংশ জমিদারী পাদ্রীদের সুপারিশে কোম্পানি সরকার খাস করে নেয় এবং পরে তা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের বন্দোবস্ত দেয়। (আবদুল গফুর সিদ্দিকী : শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা ৪৫)
সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে যে ভূমি-ব্যবস্থা ছিল, তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অনুস্বত্বের অধিকারী নতুন জমিদাররা জমির পূর্ণস্বত্ব মালিকানা লাভ করল। কৃষকরা হলো তাদের অনুগ্রহ ও মর্জিম ওপর নির্ভরশীল।কৃষকরা শুধু জমি চাষ করার অনুমতি লাভ করল। জমিতে তাদের কোন স্বত্ব রইল না। কৃষকের স্বত্ব এবং ভূমি-ব্যবস্থার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকল না। এ ব্যবস্থার ফলে উপস্বত্বের অধিকারীরা পূর্ণস্বত্ব ভোগের দ্বারা কৃষকদের ওপর যে নির্মম নিষ্পেষণ চালায় তার বিবরণ তুলে ধরে আবদুল মওদুদ উল্লেখ করেছেনঃ
“এই নয়া ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অত্যাচার এতখানি চরমে উঠেছিল যে, দাড়ি রাখার জন্য নতুন ট্যাক্স বসাতে তাদের অনেকের সংকোচ হয়নি”। (আবদুল মওদুদ : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি; ড, হাসান জামান সম্পাদিত ও নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশিত, ‘শতাব্দী পরিক্রমা’, পৃষ্ঠা ৬১)
ইংরেজরা তাদের বর্ধিত রাজস্বের দাবি আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই জমিদারদের সাথে প্রথমে পাঁচসালা, এরপরে দশসালা ব্যবস্থা করে এবং ১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডের ভূমি-ব্যবস্থার অনুকরণে ‘চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত’ প্রবর্তন করে। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নিজস্ব রাজস্ব দিয়ে যথেচ্ছা পরিমাণে খাজনা আদায় ও জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত ও উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। জমির ওপর কৃষদের স্বত্ব অস্বীকার করে তাদেরকে জমিদারী শোষন-লুণ্ঠন ও নির্যাতনের স্থায়ী শিকারে পরিণত করা হয়।
মুসলিম শাসন আমলে বাংলার জমিদারদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হতো। তারা ছিলেন বিভিন্নভাবে জমির অধিকারী এবং রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী সরকারি কর্মচারী মাত্র। নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করা এবং শাসন বিভাগের আংশিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদয় করতে পারতেন না; কিংবা কোনরূপ অত্যাচার করতে পারতেন না। রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখরার ব্যাপারে ফৌজদারগণ দায়িত্ব পালন করতেন। কোন কারণে জমিদাররা সরকারের অবাধ্য হলে বা জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারী হলে তাদের জমিদারী ছিনিয়ে নেওয়া হতো। (মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)
ইংরেজ বণিক শাসনে এই পুরো ব্যবস্থারই খোল-নলচে পাল্টে ফেলা হয়।
প্রথমত, মুসলিম আমলে ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায় করা হতো। এখন জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হলো।
দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের নব-প্রবর্তিত ব্যবস্থায় জমির মালিকানার ওপর কৃষক বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধিকার রহিত হলো।
তৃতীয়ত, কোম্পানি সরকার খাজনা আদায়ের জন্য জমির মালিকানা ইজারা দিল বিভিন্ন ভয়ালরূপী যোগানদের কাছে। নিলামের ডাকে প্রচুর অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়ে পুরনো জমিদাররা পিছিয়ে গেল। সেখানে ইংরেজদের লুণ্ঠনবৃত্তির এদেশীয় সহচর এমন একটি নব্য পুঁজিপতি শ্রেণী অধিষ্ঠিত হলো, যাদের একমাত্র ঐতিহ্য ছিল ইংরেজদের তোষণের জোরে এদে্শের কৃষকদেরকে লুণ্ঠন করা। এই শ্রেণীর জমিদাররা সকলেই হিন্দু আর তাদের রায়তরা শতকরা পচাঁত্তর ভাগেরও বেশি মুসলমান। তারা জমির স্বত্ব হারিয়ে নবোত্থিত বর্ণহিন্দু লুটেরা জমিদারদের স্থায়ী শোষণ ও জুলুম-নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ ইংরেজদের বিভিন্ন পদক্ষেপকে ‘শঠতা’ বলে উল্লেখ করে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেনঃ
“বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লীর বাদশাহর প্রধান রাজস্ব অফিসারের দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে। মোটা অংকের উৎকোচ দেওয়ার পরিবর্তে তলোয়ারের জোরেই এই নিয়োগ আমরা ক্রয় করেছি। কিন্তু আমাদের পদের নাম ছিল বাদশাহের দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব অফিসার। এ কারণে মুসলমানরা মনে করে যে, মুসলমানের প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে আমরা বাধ্য; কারণ ঐ বিধি-ব্যবস্থা প্রশাসনের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে এ সম্পর্কে সংশয়ের খুব কমই অবকাশ আছে যে, চুক্তি রচনার সময় উভয় পক্ষ এটাই বুঝেছি………….। পুরনো ব্যবস্থার ওপর যে প্রচণ্ড আঘাত আমরা হেনেছি সেটা বোধ করি শঠতার পর্যায়েই পড়ে এবং ইংরেজরা বা মুসলমানরা কেউই এর পরিণতি উপলব্ধি করতে পারেননি। এটা হচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং জন শোর প্রবর্তিত এক গাদা সংস্কার কার্যক্রম, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায় বন্দোবস্তের মধ্যে যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে”। (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০)
কোম্পানির সমর্থকরূপে নব্য জমিদার ও মহাজন
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার যে শোষণ-ব্যবস্থা চালূ হয় সে সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেনঃ
“বাংলাদেশের জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে। তখন হইতে জমিদারগোষ্ঠীর আদায় ক্রমশ বাড়িয়েই গিয়াছে। কিন্তু শাসকদের রাজস্ব অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের লুণ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগ দিয়া এদেশে জমিদার নামক একদল স্থায়ী শাসককে তাহাদের রক্তাক্ত শাসন ও শোষণে চিরস্থায়ী সমর্থগোষ্ঠীরূপে সৃষ্টি করে”। (সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৬)
ইংরেজ শাসক ও তাদের সমর্থক জমিদারদের খাজনার দাবি মিটাতে কৃষকরা তাদের জমি ও বাড়িঘর বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের জন্য মহাজনদরে শরণাপন্ন হয়। সুদে-আসলে সে ঋণ পরিশোধ করতে কৃষকরা ব্যর্থ হয়, আর মহাজনরা তাদের ঘরবাড়ি-জমি-জিরাত কেড়ে নেয়। এভাবে মহাজনরা কালক্রমে জমিদার হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের শোষণের যোগ্য অংশীদারে পরিণত হয়। বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহাজন মাত্রই হিন্দু। ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট এসব জমিদার-মহাজনরাই ছিল বাংলাদেশের নিরীহ সরল কৃষকদের প্রধান শক্র।
ঋণদান ছাড়া মহাজনদের অন্য একটি ভূমিকা ছিল। ফসল বিক্রি করতে হলে চাষীকে সেই মহাজনের কাছেই ধর্ণা দিতে হতো। ঋণ ও সুদের দাবি মিটাতে চাষীকে মহাজনের শোষণের স্থায়ী শিকার হয়ে থাকতে হতো। মহাজনের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় ছিল না। কখনো ক্ষেপে গিয়ে চাষীরা যাতে মহাজনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চালাতে না পারে, সে জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সর্বশক্তি দিয়ে মহাজনশ্রেণীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়। এভাবে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের কৃষকদের ওপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক-শক্তি তাদের সমস্ত ভার নিয়ে চেপে বসে। বৃটিশরা আদায় করে তাদের খাজনা ও বিভিন্ন কর। আর মহজনরা কৃষকের বাকি ফসলের প্রায় সবটুকু কেড়ে নেয় তাদের ঋণের সুদ হিসাবে।
এ প্রসঙ্গে আর পি দত্ত উল্লেখ করেছেনঃ
“বৃটিশ-ভারতের একজন কৃষকের বার্ষিক গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮ থেকে ৪২ টাকা। ট্যাক্স-খাজনা এবং মহাজনের ঋণ বা ঋণের সুদ পরিশোধ করার পর কৃষকের হাতে অবশিষ্ট থাকত মাত্র ১৩ থেকে ১৭ টাকা। অর্থাৎ আয়ের এক তৃতীয়াংশ হাতে নিয়ে কৃষকের সারা বছর কিভাবে চলবে সেই সমস্যার কথা ভাবতে হতো” (আর পি দত্ত : ইন্ডিয়া টু-ডে, পৃষ্ঠা ২৫১)
বাংলাদেশের লুটের টাকায় বিলাতে শিল্প-বিপ্লব
কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটল। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো ধ্বংসের বিভীষিকা। মোগল আমলের বাংলার সমৃদ্ধ সমাজ-কাঠামো ধ্বংস হলো এবং কোম্পানির অনুগ্রহপুষ্ট দালাল, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, নব জমিদার ও মহাজন নামক লুণ্ঠনকারীরা সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। ইংরেজ বেনিয়াদের এ সকল ভাগ্যন্বেষী অনুচর, দালাল ও মোসাহেবদের দস্যুব্রত্তির দৌরত্ম্যে দেশ জুড়ে ঘনিয়ে আসে শিল্পের ঘোরতর দুর্দিন।
এই নিব্য লুটেরা শোষক শ্রেণীটি সত্যিকার জমিদার যেমন হতে পারেনি, ব্যবসায়ী হিসেবেও তারা ছিল দালাল-পর্যায়ভুক্ত। কোম্পানির একাধিপত্যের দরুন তারা বহির্বাণিজ্যে যেমন নাক গলাতে পারেনি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় বড় দিকও তেমনি ইংরেজদের একচেটিয়া দখলে চলে গিয়েছিল। ফলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যৈর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল বিদেশীদের হাতে।
বাঙালি নব্য জমিদারগোষ্ঠী কৃষি ধ্বংস করল, কৃষকের সর্বনাশ ঘটালো, ব্যবসা হারাল, শিল্পকে অবহেলা করল, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প কেড়ে বাড়ি-ঘর ও জমি-জমায় টাকা খাটাবার দিকে মন দিল। ফলে সমৃদ্ধ একটি জাতি সব দিক দিয়ে রিক্ত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়ল। তাদের অগ্রগতির সকল দুয়ার রুদ্ধ হলো।
পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলা ও বিহারের সম্পদ লুট করে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ বিলাতে নিয়ে যায় তার ফলে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব আরো আগে শুরু হলেও ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এর গতি ছিল মন্হর। কিন্তু বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ ইংল্যান্ডে পৌঁছতে শুরু করার পর থেকে সেখানে অতি দ্রুত বিভিন্ন কল-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে”। (সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)
মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ ছিল একচেটিয়া রফতানিকারী দেশ। এদেশের পণ্য সম্ভার দিয়েই ইংল্যান্ডে ব্যবসা-বণিজ্য চলতো। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য এনে এদেশ বিক্রি করার কথা কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেনি। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার মতো উন্ন ত বস্ত্রশিল্প তখনো ইউরোপের কোন দেশে গড়ে ওঠেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয় ছিল, তার বিবরণ দিয়ে ব্রুকস এডামস লিখেছেন:
“ব্যংক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হওয়ার ৫০ বছর পরও ব্যাংকের প্রচলিত নোটের মধ্যে সবচে বড় নোট ছিল ২০ পাউন্ডের নোট। ১৭৫০……. সমগ্র প্রদেশে বারোটার বেশি বাংক ছিল না। অথচ ১৭৯০ সাল নাগাদ শহরের প্রতিটি বাজারে ব্যাংক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ থেকে রূপা আসার সাথে সাথে শুধুমাত্র অর্থের প্রচলন বেড়ে যায়নি, আন্দোলনও জোরদার হয়েছে”। (Brooks Adams : The Law of Civilization and decay; P. 203-4)
ব্রুকস এডামস শিল্প-বিপ্লবের পটভূমি তুরে ধরে লিখেছেন:
“পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের লুণ্ঠিত ধন-রত্ন ইংল্যান্ডে আসতে লাগল। তখনই অবিলম্বে এর ফল বুঝা গেল। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। তারপর থেকেই (ইংল্যান্ডে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তার তুলনা বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ১৭৬০ সালের সাগে ল্যাংকাশায়ারে বস্ত্র-শিল্পের যন্তপাতি এদেশের মতোই সহজ সাধারণ ছিল এবং ১৭৯০ সালে ইংল্যান্ডে লৌহ-শিল্পের অবস্থা ছিল আ রো শোচনীয়।………. ইংল্যান্ডে ভারতের ধন-সম্পদ পৌঁছার এবং ঋণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক শক্তি বা মূলধন ইংল্যান্ডের ছিল না”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০)
ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের দরুন দেশীয় কারিগর ও শিল্পের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। বিলাতের শিল্প-বিপ্লব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দরুন কোম্পানি-রাজের বদৌলতে বিলাতি বস্ত্র ও শিল্প-সম্ভারে দেশ ছেয়ে যায়। বেনিয়ারা কারিগর শ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ফলে যারা ছিল শ্রমিক, তারাও জীবিকার একমাত্র পথ হিসেবে ভূমিচাষে এগিয়ে আসে।
ব্যবসাক্ষেত্রে বেনিয়া কুঠিগুলোকে কেন্দ্র করে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সি ও দেওয়ান নামে এক নতুন দালালশ্রেণূ গড়ে ওঠে। এই শ্রেণীটিও দেশীয় শিল্প ও কারিগরকে গলাটিপে মারা পথ প্রশস্ত করে।
নতুন আর্থিক বিন্যাসের ফলে যে ভূস্বাসী ও দালাল-শ্রেণীর উদ্ভব হলো তারা একজনও মুসলমান নয়, মুসলমানদের সে সমাজে প্রবেশাধিকার ছিল না। (আবদুল মওদুদ : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২)
এ শ্রেণীটিই পরবর্তীকালে গণবিক্ষোভ ও জাতীয় জাগরণের প্রধান শত্র হিসেবে নিজ স্বার্থে সর্বদাই বৃটিশ শাসন টিকিয়ে রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এ দালাল-শ্রেণীটির ভূমিকার কথা উইলিয়ান বেন্টিঙ্কও স্বীকার করেছেন। (A. B. Keiths : Speeches and Documents on Indian Policy Vol-1, p-2)
শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের কল-কারখানার জন্য কাঁচামালের চাহিদা দেখা দেয়। সে ব্যাপারেও ইংরেজদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রতি। অন্যদিকে তাদের কল-কারখানায় তৈরি পণ্য-সামগ্রী এদেশের বাজার ছেয়ে ফেলে। এভাবে বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ মূলধনী শ্রেণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিরাট বাজার ও কাঁচামালের অফুরান ভাণ্ডারে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাচীন শিল্পব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে ভাতের বস্ত্র-শিল্পের ওপর তাদের আঘাত সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর হয়েছিল। বাংলাদেশ তথা ভারতের বস্ত্র উৎপাদনকারী কারিগররা কোম্পানির বণিকদের দ্বারা পূর্বেই প্রায় ক্রীতাদাসে পরিণত হয়েছিল। বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকরা তাদের কাছ থেকে বাজারদরের অর্ধেক দামে ‘মসলিন’ ও ‘কেলিকো; কিনতো। পূর্বের সকল অত্যাচার ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গ্রাস থেকে তাঁতীদের যে একটি অংশ কোন প্রকারে বেঁচেছিল, বিলাতি পণ্যের বাজারে পরিণত হওয়ার ফলে সে উৎপাদক শ্রেণীটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিল, ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে সে শিল্প এই পর্যায়ে বিলুপ্ত হলো। ইংরেজ বণিক-শাসকদের হাতে এদেশের শিল্প ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছেন:
“অনধিকার প্রবেশকারী ইংরেজরাই ভারতের তথা বাংলাদেশের তাঁত ও তকলী ভেঙ্গে চুরমার করে। ইংল্যান্ড ভারতের তুলাজাত দ্রব্য ইউরোপের বাজার থেকে বিতাড়িত করতে থাকে, তারপর হিন্দুস্থানকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। যে দেশ তুলার জন্মস্থান বলে চির পরিচিত, সে দেশটাকেই তারা শেস পর্যন্ত তুলা দিয়ে (অর্থাৎ তুলাজাত দ্রব্য দিয়ে) ছেয়ে ফেলে”। (Karl Marx : British Rule in India)
শিক্ষাক্ষেত্র মুসলমানদের বিপর্যয় ও হিন্দু-উত্থান
ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষাক্ষেত্র মুসলমানরা সম্পূর্ণ পিছিয়ে পড়েছিল। সাড়ে পাঁচশ’ বছরের মুসলিম শাসনে এদেশে শিক্ষার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধুলিসাৎ হয়েছিল। ইংরেজরা শাসনভার গ্রহণ করার পর মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলো হল:
ক. ইংরেজ ও তার এদেশীয় সহচরদের সম্মিলিত লুণ্ঠন-শোষণের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থা;
খ. ওয়াকফ বা লাখেরাজ সম্পত্তি বায়েজাফত করার ফলে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়া;
গ. ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-প্রথার প্রবর্তন;
ঘ. নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অভাব;
ঙ. খ্রিস্টান মিশনারীদের পরামর্শ ও নির্দেশনায় ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণের ফলে ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা;
চ. মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা;
ছ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম হিন্দুয়ানী ভাবধারায় ঢেলে সাজানো;
জ. মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি সাহায্য ও প্রতিষ্ঠানিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়া; এবং
ঝ. পলাশীর বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানদের আহত আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তাদের ঐতিহ্যবিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বৈরী পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে না পারা।
মুসলিম শাসনামল থেকেই মুসলমানরা বাদশাহ, সুলতান, নওয়াব ও তাদের বড় কর্মচারীদের প্রদত্ত জায়গীর, আয়মা, আল তমগা, মদদ মাশ প্রভৃতি লাখোরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। এসব সম্পত্তির আয় দ্বারা শুধু তাদের ভরণ-পোষণই চলত না, অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ইমামবাড়া, মুসাফির-খানাসহ নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো।
ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সময় বাংলার এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তি ছিল নিষ্কর। ইংরেজরা ১৮২৮ সালে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াফত আইন পাস করে এসব নিষ্কর সম্পত্তি কেড়ে নেয়। শুধু বাংলাদেশেই ১৮২৮ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত কয়েক বছরে অন্তত কুড়ি হাজার নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াফত হয়। ফলে বহু প্রাচীন মুসলিম বংশ উৎখাত হয় এবং মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহসহ অসংখ্য মুসলিম শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয়।
ম্যাক্সমুলার উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজদের ক্ষমতা দখলকালে বাংলায় আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। প্রতি চারশ’ লোকের জন্য তখন একটি মাদরাসা ছিল। বখতিয়ার খিলজী থেকে আলীবর্দী খান পর্যন্ত বিদ্যোৎসাহী মুসলিম শাসকদের আমলে এদেশ অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দরসবাড়ী, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাঁও, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বহু বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। উপমহাদেশের বাইরে থেকেও উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু ছাত্র বাংলার এসব শিক্ষাকেন্দ্রে জমায়েত হতেন।
ইংরেজদের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপেরে ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়। ইসলামী শিক্ষার মহতী কেন্দ্ররূপে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার অবসান ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত কেন্দ্রগুলোর সন্ধান লাভও এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।
ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্দ হওয়ার পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারীদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ-সাহায্যে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। (R. C. Majumder : Bengal in the Nineteenth Century, P-32)।
লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলের পরামর্শে সৃষ্ট ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত আইনবলে কেবলমাত্র ইংরেজি স্কুল ছাড়া অন্য কোন শি ক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য লাভের অনুপযুক্ত ঘোষিত হয়। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহ্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্হী ছিল। এ সম্পর্কে মেকলের উক্তি থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন:
“বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হতে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে; কিন্তু রুচি, মতামত ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ”। (Woodrow : Macaulay’s Minutes on Education in India [1862])
এই মেকলের মেজাজ ও মানসিকতা সম্পর্কে তার আর একটি দম্ভোক্তি থেকে জানা যায়। তিনি একবার বলেছিলেন:
“ইউরোপীয় যে কোনও ভালো লাইব্রেরির একখানি মাত্র আলমারী ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের চেয়েও বেশি মূল্যবান”।
১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করা হয়। ফলে মুসলমানদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, ইংরেজিতে ডিগ্রীপ্রাপ্তরাই সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। ইংরেজদের এই সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তগুলো মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর একের পর এক আঘাত হানে।
১৮১৪ সালে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষাখাতে তারা বার্ষিক এক লাখ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে। অথচ অন্যদিকে ১৮১৬ সালে তারা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ওয়াকফ তহবিলের সাড়ে বাইশ লাখ টাকা হস্তগত করে।
মুসলমানরা ৫৫,০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের সাড়ে বাইশ লাখ টাকার তাদের এই নিজস্ব তহবিল থেকে নিজেরাই যদি ব্যয় করতে পারত, তবে সরকারি সাহায্যের কপর্দকমাত্র ছাড়াই তারা সারা দেশে নিজেদের শিক্ষঅর অনেকাংশের ব্যয়-সংকুলান করতে পারত। কিন্তু ইংরেজ সরকার ধর্মীয় ও ওয়াকফ সম্পত্তির এই বিপুল অর্থ ১৮১৬ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর বশি সময় ধরে অমুসলমানদের জন্য ব্যয় করে। (নওয়ার আদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহসিন ফান্ডের টাকা নির্ধারিত মুসলিম শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয় হবে।)
মুহসিন ফান্ডের সে বিরাট আয় থেকে ১৮৩৬ সালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজ খোলা হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেঝে কোন মুসলমান ছাত্র ভর্তির সুযোগ ছিল না। অথচ হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) দানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেঝে হিন্দুদের পড়ার সুযোগ থাকে অবারিত। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৩০০ ছাত্রের মধ্যে বছরের পর বছর সেখানে এক ভাগও মুসলমান ছিল না।
চট্টগ্রামে মীর ইয়াহিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যে বিপুল সম্পত্তি রেখে যান, কোম্পানি সরকার সে দানের টাকায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। সে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু।
নতুন গজিয়ে ওঠা হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণী শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার নযীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইংরেজদের লুণ্ঠন-সহচর এই জমিদার ও ধনিক গোষ্ঠী শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়েছি নিজেদের মুসলিম-প্রধান জমিদারী এলাকায়। কিন্তু মুসলিম রায়ত-প্রজাদের কাছ খেকে লুটে নেওয়া ধন-সম্পদ থেকে স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য ব্যয় করেছে হিন্দু-প্রধান অন্য এলাকায়। নোয়াখালীর জমিদার প্রতাপচন্দ্র কিংবা জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবার, সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অভিন্ন ছিল। প্রতাপচন্দ্র মুসলিম প্রধান নিজ জমিদারী এলাকার শিক্ষার জন্য কোন কিছু না করে স্কুল কায়েম করেছেন বীরভূমে হিন্দু প্রধান এলাকায়। ঠাকুর পরিবারের জমদিারী ছিল পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকায়; কিন্তু তারা থেকেছেন কলকাতায় এবং জমিদারীর আয় থেকে খরচ যা কিছু করেছেন সেখানেই।
খ্রিস্টান মিশনারী ও নব্য-পুঁজিপতি দালাল হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষা শিক্ষার স্কুল বাংলা পাঠশালাগুলোতে ‘বাংলা ভাষ্য’র নামে যা শিখানো হতো তা আসলে সংস্কৃতেরই নামান্তর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা যবানকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পাঠ্য-পুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল হিন্দু দেব-দেবীর পৌরণিক কাহিনী নিয়ে। ছাত্রদের জন্য ক্লাসে সরস্বতী-বন্দনা ছিল বাধ্যতামূলক।
১৮৪১ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৪৬ সালে ঢাকার স্কুল-কলেজে ২৬৩ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১৮ জন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মাত্র চার দশকের মধ্যে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পচিঁশ গুণ। এই ছাত্রদের প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। ১৮৮১ সালে ১৭১২ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ১৪৮০ জনই ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু। বাকিরা বিহারি, অসমীয় বা উড়িয়া। বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। একই বছর গোটা উপমহাদেশে ৪২৩ জন এম এ ডিগ্রী লাভ করে। তার মধ্যে ৩৪০ জন ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু। ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের ছাত্রদের সম্মিলিত সংখ্যা মাত্র ৮৩ জন। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের এই উত্থান যে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ মদদের ফল, তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।
ইংরেজদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেনঃ
“আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যব্স্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্হি, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। ……… আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি”। (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৬০)
মুসলমানদের সর্বনাশের এ নাটকে ইংরেজ নায়কের পাশে ভিলেনরূপী বর্ণহিন্দুদের উত্থান ও জাগরণ সম্পর্কে সুরজিত দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ
“ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো, অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিতশ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়”। (সুরজিত দাশ গুপ্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম; পৃষ্ঠা ১৬৯)
সুরজিত দাশগুপ্ত লিখেছেনঃ
“ব্রিটিশদের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকার দেশীয় মানুষ সামর্থ্য ও সাহায্য যুগিয়েছে : পাইক সম্প্রদায় – এরা ব্রিটিশদের বাহুবল যুগিয়েছেদ; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়…… এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র বা দালাল হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে, ধর্মের বিচারে ব্রিটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী”।
এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেনঃ প্রথম যুগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষঅর সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছে, যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের চাকরিও পেয়েছে। মুসলমানরা সে রকম সুযোগ-উৎসাহ পাননি।
সরকারি চাকরিঃ ‘মুসলমানদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই’
মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রিয় চাকরির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। রাজস্ব আদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সকল উল্লেখযোগ্য উচ্চপদে মুসলমানরাই নিযুক্ত ছিল। দেওয়ান পদে সব সময়ই মুসলমান কর্মচারি ছিল এবং প্রাদেশিক দেওয়ান অফিসে বহুসংখ্যক মুসলমান কর্মচারী কাজ করত। বাংলাদেশের ১৬৬০ টি পরগনায় আমিন, আলিম, কারকুন, খাজাঞ্চি, কানুনগো প্রভৃতি পদে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী কাজ করত। ছোটখাট পদে ছিল হিন্দুরা। বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাযী, মুফতী, মীর-ই-আদল প্রভৃতি পদে মুসলমানরাই অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।
এভাবে বিভিন্ন সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদে যেসব মুসলমান কর্মরত ছিলেন, ইংরেজ আমলে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়। পলাশীর পতনের পরপরই কোম্পানির নির্দেশে মীল জাফর আশি হাজার দেশীয় সৈন্যকে বরখাস্ত করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় বাকি সৈন্যদেরও চাকরিচ্যুত করা হয়। সামারিক ও বেসামরিক সকল কর্মস্থল থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়। মুসলমানদের চাকরিচ্যুত করে বিভিন্ন সরকারি পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হয়।
ইংরেজদের নিয়োগ-নীতির বদৌলতে সৃষ্ট অবস্থা সম্পর্কে হান্টার লিখেছেনঃ
“একশত বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয় চাকরির সমস্ত পদ মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। বর্তমান তাদের আনুপাতিক হার মোট সংখ্যার তেইশ ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। এটাও আবার শুধু মাত্র গেজেটেড চাকরির বেলায় প্রযোজ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেছে। ক’দিন আগে দেখা যায় যে, কোন একটা বিভাগে এমন একজনও কর্মচারী নেই, যে মুসলমানের ভাসা পড়তে জানে; এবং বস্তুত কলিকাতায় এখন কদাচিত এমন একটা সরাকির অফিস চোখে পড়বে, যেখানে চাপরাশি ও পিয়ন পদের উপরিস্তরে একজনও মুসলমান কর্মচারী বহাল আছে। এ রকম হওয়ার কারণ কি এই যে, মুসলমানদের চাইতে হিন্দুরা অধিকতর যোগ্য এবং তারাই সুবিচার পাওয়ার দাবি রাখে? অথবা ব্যাপারটা কি এই যে, বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের এত বেশি সুযোগ রয়েছে যে, সরকারি চাকরি গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক এবং তাই চাকরির জায়গাটা তারা হিন্দুদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, কিন্তু সরকারি কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্য যে রকমের সর্বজনীন ও অনন্য মেধা থাকা দরকার, বর্তমানে তা তাদের নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও এ কথার পরিপন্হী। বাস্তব সত্য হলো এই যে, এদেশের শাসন-কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয় এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য এখন সরকারি চাকরি এবং বেসরকারি কর্মক্ষেত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গছে”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮)
১৮৬৯ সালের আইন-আদালতের চিত্র তুলে ধরে হান্টার লিখেছেনঃ
“মহামান্য রাণীর নিযুক্ত মোট ছয়জন আইন অফিসারের মধ্যে চারজন ইংরেজ ও দুই জন হিন্দু ছিল, মুসলমান একজনও ছিল না। হাইকোর্টের উচ্চতর গেজেটেড পদে মোট একুশ জন অফিসারের মধ্যে সাতজন ছিল হিন্দু, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। ব্যারিস্টারদের মধ্যে তিনজনি ছিল হিন্দু, মুসলমান একজন ও ছিল না। কিন্তু হাইকোর্টের উকিলের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকাটা সর্বাধিক করুণ ইতিহাসের পরিচায়ক। বর্তমানে যারা জীবিত, তাদের সকলেরই মনে আছে যে, আইনের এই পেশাটা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদেরই করায়ত্ত ছিল।………. ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে উকিল হিসেবে সনদ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের সবাই মুসলমান। এমনকি, ১৮৫১ সালেও যারা সনদ পেয়ে তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান। এরপর থেকেই এ পেশায় নতুন ধরনের লোকদের সমাগম ঘটতে থাকে। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ্যতার যাচাই শুরু হয়ে যায় এবং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৫৮ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল সাতাশ, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। শিক্ষানবীশ হিসেবে কর্মরত উদীয়মান আইনজীবীদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ, কিন্তু মুসলমান শূন্যের কোঠায়”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০)
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে।
১৮৬৯ সাল ও তার পরবর্তী বছরগুলোর অবস্থার পর্যালোনায় দেখা যায়, চাকরি সর্বোচ্চ স্তরে আনুপাতিক হার ছিল মুলমান একজন আর হিন্দু দু’জন। এরপর মুসলমান একজন, হিন্দু তিনজন।
দ্বিতীয় স্তরে আগে ছিল মুসলমান দুই আর হিন্দু নয় জন, পরে মুসলমান এক আর হিন্দু দশজন।
তৃতীয় স্তরের চাকরিতে পূর্বে মুসলমান চারজন আর হিন্দু ও ইংরেজ মিলে সাতাশ জন, পরে মুসলমান তিন এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে চব্বিশ জন।
নিম্ব স্তরে ১৮৬৯ সালে মুসলমান ছিল চার জন ও অন্যান্য ত্রিশ জন। পরে মুসলমান চারজন আর অন্যান্য ঊনচল্লিশ জন।
শিক্ষানবীশ স্তরে ১৮৬৯ সালে আটাশ জনের মধ্যে দু’জন মুসলমান আর পরবর্তীকালে সেখানে একজন ও মুসলমান নাই”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬)
কলকাতা থেকে ফারসি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ‘দুরবীন’ ১৮৬৯ সালে জুলই সংখ্যায় চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেনঃ
“উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সকল চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদেরহাত থেকে ছিনিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। অথচ এমন সময় এসেছে, যখন মুসলমানদের না্ম আর সরকারি চাকরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না। কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাঙক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিলনার অফিসে কতিপয় চাকরিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিকারটি সরকারি গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, এই শূণ্যপদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে। মোট কথা হল, মুসলমানদের এতাটা নীচে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হাসিল করা সত্ত্বেও সরকারি বিজ্ঞপ্তি মারফত এটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে য, তাদের জন্য কোন চাকরি খালি নেই। তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি কারো দৃষ্টি নেই এবং এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও রাজি নয়”। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩)
চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের ওপর সবচে বড় আঘাতটি করা হয়েছিল অফিস-আদালতের ভাষারূপে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালূ করার মাধ্যমে। এই কাজে ইংরেজদের উদ্বদ্ধ করতে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ সরকারের সমর্থক ইংরেজি শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের উচ্ছেদ করে একচেটিয়া অধিকার লাভের স্বার্থ-চিন্তাকে সামনে রেখে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিস আদালতের ভাষারূপে চালূ করার জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং আরো বিভিন্নভাবে দাবি জানাতে থাকে।
দিল্লী সম্রাটের কাছ থেকে রাজা উপাধি নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে রাম মোহন রায় ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালূর পক্ষে ওকালতি করে আসেন। ইংরেজরা এই দাবি নিজেদের জন্যও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থানুকূল বিবেচনা করে ১৮৩৭ সালে এক আকস্মিক আদেশ জারির মাধ্যমে ইংরেজিকে অফিস-আদালতের ভাষারূপে ঘোষণা দেয়। এর ফলে সরকারি চাকরির প্রতিটি দুয়ার মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।
দীর্ঘদিন ফারসি সরকারি ভাষারূপে চালূ থাকার কারণে এবং ইংরেজদের শিক্ষানীতি সকল দিক দিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ, সামর্থ্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আঘাতরূপে বিবেচনা করার কারণেই মুসলমানরা এতকাল ইংরেজি শিক্ষা করেননি এবং তা করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও অনুভব করেনি। জেমস লঙ মুসলমানদের ইংরেজি না শিকার একটি কারণ হিসেবে বলেছেনঃ
“খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবী ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দু’টি ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল”। (বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ১৫৬)
মুসলমানদের ইংরেজি না শেখার পটভূমি তুলে ধরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ ১৮৮০ সালে ‘দি ফিউচার অব দ মোহমেডানস অব বেঙ্গল’ নামক পুস্তিকায় ‘সাঈদ’ ছদ্মনামে লিখেছেনঃ
“The Aversion to English education is tracesble to race not felt by the Hindus, to their possession of a rich literature of their own, to their greater religious bigotry and partly to their povrty.” (The Calcutta, Review, Vol LXXIL. NO; CX LIV, 1881. P-V; ডক্টর ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতরার ধারা, পৃষ্ঠা ৫৯)
মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ না করার একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ইংরেজ ও তাদের সহযোগী দালাল হিন্দু জমিদারদের শাসন-শোষণে মুসলিম অভিজাতশ্রেণী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানের পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। শহরের ব্যয়বহুল শিক্ষার জন্য সন্তানদের প্রেরণা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে সিসিল বিডন ১৮৫২ সালের ২৫ এপ্রিলের এক ‘মন্তব্যপত্রে’ লিখেছেনঃ
“মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, তারা তাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থ দৈন্য ছিল না”। (ডক্টর ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃষ্ঠা ৫৯)
সার্বিক এ বরৈী পরিস্থিতিতে চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে অবস্থা দাঁড়ায়, সে সম্পর্কে হান্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার ১৮৭১ সালে প্রদত্ত একটি তালিকা থেকে জানা যায়, সে সময়কার ২১১১ টি গেজেটেড পদে মুসলমান ছিল মাত্র ৯২ জন। আর ১৫টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ আটটিতে একজনও মুসলমান ছিল ন। (হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭)
চাকরিক্ষেত্রে মুসলমানদের অপসারিত করে হিন্দুদেরকে অধিষ্ঠিত করার পিছনে ইংরেজদের যে মানসিকতা কাজ করেছে, ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে স্যার জন ম্যালকম-এর বক্তৃতা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ
“ভারতের হিন্দুদের সহযোগিতাই আমাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়”।
লর্ড এডিনবরো একইভাবে সে মানসিকতা তুলে ধরেছেন। তিনি ১৮৪৩ সালে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে এক পত্রে লিখেছেনঃ
“মুসলমানরা বরাবরই আমাদের শক্র। ভারতে আমাদের নীতি হতে হিন্দুদের প্রতি আমাদের হস্ত প্রসারিত রাখা”। (A. R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal. P-64)
ভাষা ও সাহিত্য : মুসলিম সৃষ্টিধারায় বিপর্যয়
ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলিম শাসক, প্রচারক ও লেখকদের অবদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে বাংলাকে যেমনি মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তেমনি তাদের হাতেই মৃত ও অবহেলিত বাংলা ভাষা নবজীবন পেয়েছে। এমনকি বাংলা গদ্যের যে নমুনা, তাও মুসলিম শাসনামল থেকেই পাওয়া যায়। ষোল শতাব্দীর আগেই চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজনে গদ্যের খানিকটা প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনকালে সাহিত্যের প্রয়োজন ছাড়াও সরকারি দফতরখানা, খাজাঞ্চিখানা, কাজীর বিচারালয় ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। সেই গদ্যের পরিচয় জানিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেনঃ
“ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলা গদ্যে লেখা চিঠির নমুনা পাওয়া যাইতেছে। দলিল পাইতেছিল সপ্তাদশ শতাব্দী হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা চিঠি ও দলিল অনেকগুলিই মিলিয়াছে। এই সময়ে লেখা দলিল এবং কাজ-কর্মের চিঠিতে আরবী-ফারসি শব্দের বড়ই আতিশয্য। এমনকি ভাষা ঠিক বাংলা বলতে বাধে”। (ডক্টর সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে গদ্য; মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : মুসলিম সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪)
সুকুমার সেন বা পরবর্তীকালের বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে বাংলা ভাষার আদি গদ্য-রূপটি ‘বাংলা বলতে বাধলে’ও এটাই ছিল বাংলা ভাষার আদি অবস্থা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য-নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত, দৌলত কাজী, ভারতচন্দ্র, সৈয়দ আলাউল, শ্রীকর নন্দী, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছটি খাঁ, আবদুল গফুর, ফয়জুল্লাহ, মুন্সী মুহাম্মদ আবেদ আলী, মুন্সী আইজুদ্দীন, মুন্সী আসমত- প্রমুখের লেখায়ও আরবী-ফারসিবহুল বাংলা ভাষাই লক্ষ্য করা যায়।
বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন সম্পর্কে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেনঃ
“বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনে আরবী-ফারসি শব্দের অকুণ্ঠিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির পত্রে এবং পরবর্তিকালে পাদ্রী জেকব বিশ্বাসের গদ্য রচনায় এইরূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষার সহিত পুঁথিত ভাষার পার্থক্য খুব বেশি নহে। অতএব, আরবী-ফারসিবহুল বাংলা যে কেবল অশিক্ষিত মুসলমান শায়েরদের রচনায়ই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে-তাহা আরও অধিক বিস্তৃত ও তাহার মুল আরও গভীরে প্রোথিত ছিল”। (আবদুল গফুর সিদ্দিকী : মাহে নও, কার্তিক, ১৩৬৩)
পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের ব্যাপারে ইংরেজরা যে নীতি গ্রহণ করে, তার ফলে মুসলিম অভিজাতশ্রেণী বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষমতা হারায়। ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যে নতুন ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে তাতে বাংলা ভাষার চেহারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ লক্ষ করা যায়। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেক গ্রন্হমালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং ইংরেজ-প্রসাপুষ্ট ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার রূপ ও সাহিত্যের গতি পাল্টাতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের এবং ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের এমন এক প্রেরণা যুক্ত হয়েছিল, যার সাথে বিপর্যস্ত মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুর। হিন্দু সাহিত্য, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুর সমাজাদর্শই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সবটুকু জায়গা জুড়ে ঠাঁই করে নিল। ভাষার সংস্কারে এবং বাংলা গদ্য-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টানরা এ সময় ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছিল। তার পিছনে কাজ করেছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুবিধা সৃষ্টির প্রেরণ। বর্ণ হিন্দুরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার কারণেই ছাপাখানার ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা ভাষার আদল পরিবর্তনের এ কাজটি এত ব্যাপক হলো, যার ফলে বাংলা হরফ ঠিক থাকল বটে, কিন্তু রক্তে-মাংসে সে ভাষা হয়ে উঠল অনেকাংশেই সংস্কৃত; যা ছিল আসলে বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখারই নামান্তর। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের হিংসা ও আক্রোশ এড়িয়ে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে বাংলা ভাষা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রেখেছিল। অথচ ইতিহাসের এই পর্যায়ে ইঙ্গ-হিন্দু মিলিত ষড়যন্ত্রের মুখে বাংলা ভাষা আখ্যায়িত হলো বৈরী সংস্কৃত ভাষারই দুহিতা নামে।
এ প্রসঙ্গে কাজী আমিনুল ইসলাম লিখেছেনঃ
“ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটে। ফলে বাংলা সহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার লোক মুসলমানদের মধ্যে থাকল না। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মঙ্গল-কাব্যরূপ সাহিত্য এগিয়ে গেল। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্য হতেই আধুনিক সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নাম জড়িয়ে যে সাহিত্য, তারই মধ্যে তারা বিচরণ করে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলাকে আনলেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঘুরে গেল। একচেটিয়াভাবে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যকে লালন করাতেই সাহিত্যের যে মুসলিম ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহারের গন্ধ ছিল, তা সরে গেল। ভারতচন্দ্র হতে আরম্ভ করে নন্দনকুমার, জগতধীর রায় প্রভৃতির যে বাংলা ভাষার আরবী ফারসি শব্দের প্রাধান্য ছিল তা মুছে গেল। সেই থেকে ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিল”। (কাজী আমিনুল ইসলাম বাংলার রূপরেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৭-৭০)
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ মাড় পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াল, বাংলা ভাষা মুসলমানদের মাতৃভাষা কি-না, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে কি-না, সে সম্পর্কেও নানা দ্বিধা-সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বাংলার মুসলমান বাঙালি, যখন হতে বাঙালির জন্ম (পাল-যুগ), তখন হতে তাদেরও জন্ম। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭)
এই ঐতিহাসিক সত্যও অনেকেই বিস্মৃত হয়ে বসে। এ প্রসঙ্গেই মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ লিখেছেনঃ
“পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পরিবর্তন এবং বাংলা গদ্যের চর্চায় বাঙালি মুসলমানের আত্মনিয়োগ ও সাধনার ব্যাপারটি বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের উত্তরাধিকার রয়েছে কি না এসব প্রশ্নও অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের মনে নানা দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সংশয় ও আলোড়ন বিলোড়নের জন্ম দেয় এবং এ নিয়ে কম বাক-বিতণ্ডাও হয়নি”। (মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫)
বাংলা ভাষার এ অবস্থার জন্য পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ই যে কারণ ছিল, সে সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেনঃ
“যদি পলাশীতে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলা হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত”। (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্হে সংকলিত পৃষ্ঠা ৪২১)
ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়
মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে ইসলামী শরীয়তের আলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের শিক্ষার ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে মুফতী, কাজী, মুহতাসিব ও নায়েব নিযুক্ত করা হতো। তারা মুসলমানদেরকে শরীআতের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন, তাদের ধর্মীয় সমস্যাগুলো সমাধান করতেন এবং ঈমান-আকীদার হেফাযতের ব্যাপারে দায়িত্ব পাণ করতেন, বিয়ে-শাদী পড়াতেন, জানাযা ও জুমআর নামায প্রভৃতিতে ইমামতি করতেন। এভাবে মুসলমানদের ইসলামী জীবনের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। এই স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে পীর-ফকীর-খন্দকার প্রভৃতি নামে একশ্রেণীর ‘ধর্মীয় নেতা’র আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্রভাব নিজ নিজ মুরীদদের মধ্যেই সীমিত ছিল। সাধারণ মুসলিম জনগণের তত্ত্বাবধান তারা করতেন না।
মুসলিম সমাজে এ সময় বিভিন্ন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে। একদল স্বল্পশিক্ষিত পীর-ফকীর-খন্দকার এসব সমস্যার মোকাবিলা না করে বরং সেগুলোকে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় দেখা দেয়। তাদের বিপথগামী হওয়র পথ অবারিত হয়। প্রতিবেশি হিন্দুদের প্রভাবে ও অনুকরণে বুহু কুসংস্কার ও শরীআত পরিপন্হী রীতি-রেওয়াজ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু ধর্মীয় বহু অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচার-আচরণ এ সময় ঢুকে পড়ে তাদের ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়। অনেকে সেগুলোকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে জাতে তোলার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম সমাজে মা বরকত, ওলা বিবি ও শীতলা দেবীর পূজা, কালোজিরা পড়া, কাঞ্জিপাড়া, তাবীজ-কবজ ইত্যাদি বহু নতুন উপসর্গ বেশ শক্তিশালী হয়ে আসন গেড়ে বসে। হিন্দুদের মনসা পূজার অনুকরণে খোয়াজ খিজিরের পূজা, দূর্গাপূজা-দশোহরার অনুকরণে মুহররমের দশ তারিখে হাসান-হুসাইনের তাজিয়া বিসর্জন, হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের অনুকরণে মুসলিম সমাজে নানা পার্বণ চালূ হয়।
পলাশীর পরাজয় মুসলিম সমাজ-জীবনে যে সর্বমুখী বিপর্যয় ও অভিশাপ বয়ে আনে সে সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত মুখপাত্র ইউলিয়াম হান্টার ১৮৭২ সালে লিখেছেনঃ
“তারা (মুসলমানরা) অভিযোগ করেছে যে, তাদের ধর্ম প্রচারকদের সম্মানজনক জীবন-যাপনের একটি রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। ………….. আমরা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্তার প্রবর্তন করেছি, যার ফলে তাদের গোটা সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং তারা ভিক্ষাবৃত্তি ও অবমাননাকর জীবন যাপনের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। …….. তাদের যে সমস্ত আইন অফিসার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্মীয় অনুমোদন দান করতেন এবং যারা স্মরণাতীতকাল থেকে ইসলামী পারিবারিক আইনের ব্যাখ্যা দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালন করে এসেছেন, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে আমরা হাজার হাজার পরিবারকে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি।…… মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের আত্মার ওপর পীড়ন চালাচ্ছি। অসদুদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করেছি এবং তাদের শিক্ষা তহবিলের বিরাট অংক আমরা আত্মসাৎ করেছি। তারা প্রচার করে থাকে যে, আমরা যারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভৃত্য হিসেবে বাংলার মাটিতে পা রাখবার জায়গা পেয়েছিলাম, তারাই বিজয়ের সময় কোনরূপ পরদুঃখ-কাতরতা দেখাইনি এবং গর্বোদ্ধত রূঢতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের সাবেক প্রভূদেরকে কর্দমে প্রোথিত করেছি। এক কথায়, ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীন, অনুদান ও নিকৃষ্ট তহবিল তসরূফকারী এবং দীর্ঘ এক শতাব্দিব্যাপী অন্যায়কারী হিসেবে অভিযুক্ত করে থাকে”। (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা ১২৭, ১২৮)
পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলার মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন :
“বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াফত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি- পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব-রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে”। (ড. ওয়ালি আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)
ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে শঠতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্রে ও বিভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ভাগিদার হিন্দু শেঠ বেনিয়ারাও কখনো সে প্রতারণার শিকার হয়ে জব্দ হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা এই হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক বিবেচনা করে করে যেটুকু করুণা বর্ষণ করেছে, তার দ্বারা তাদের ঋণ শতকরা শত ভাগের বেশিই শোধ হয়েছে। বাংলার মুসলমানদের জন্য যা ছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম বিপদ-বিপর্যয়, এই বর্ণহিন্দু শ্রেণীর জন্য তা ছিল প্রভূ পরিবর্তন এবং নব্য-প্রভুর কিঞ্চিত আশীর্বাদের জীবনের সকল দিক কানায় কানায় পূর্ণ ও পুষ্ট করার সুযোগ। সে কারণেই মুসলমানদের লাঞ্ছনার পটভূমিতে বঙ্কিম-গুরু ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হলো ইংরেজ-প্রভুর বিজয়-বন্দরা :
“ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়”।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি